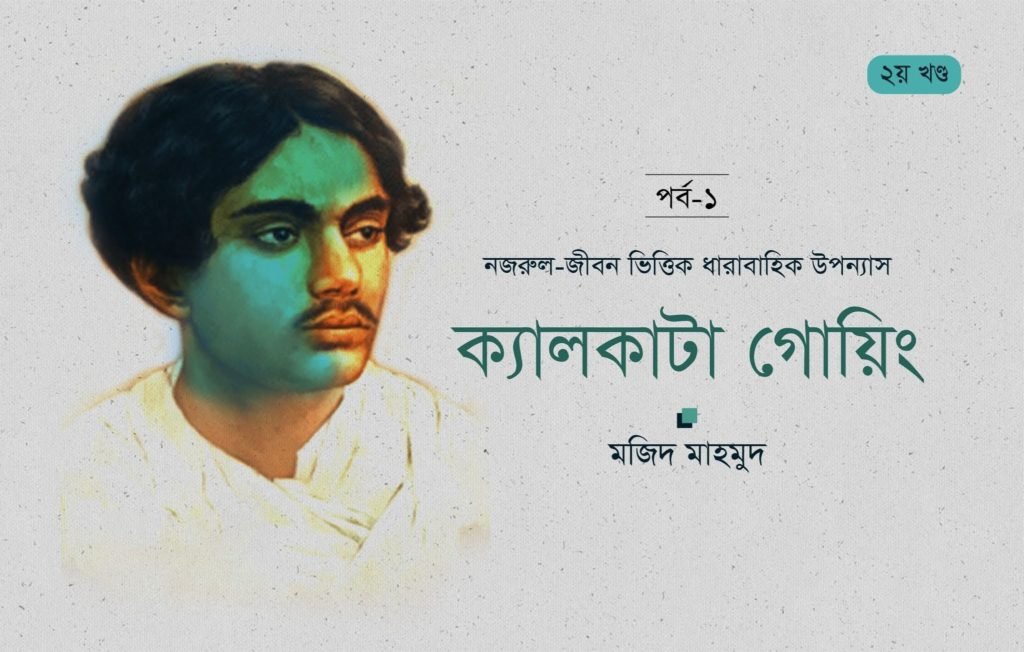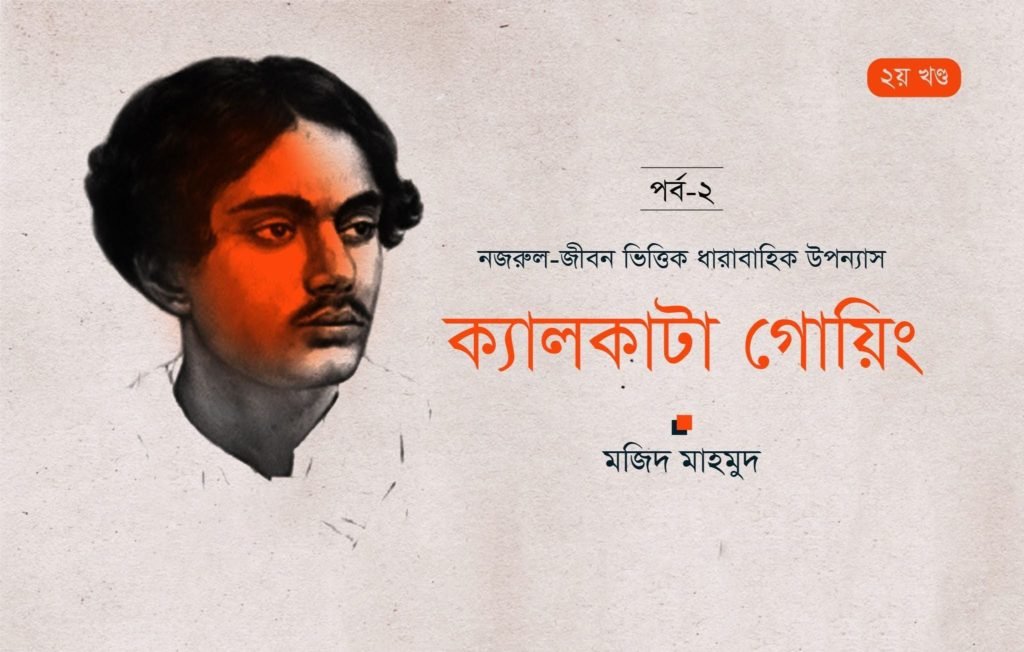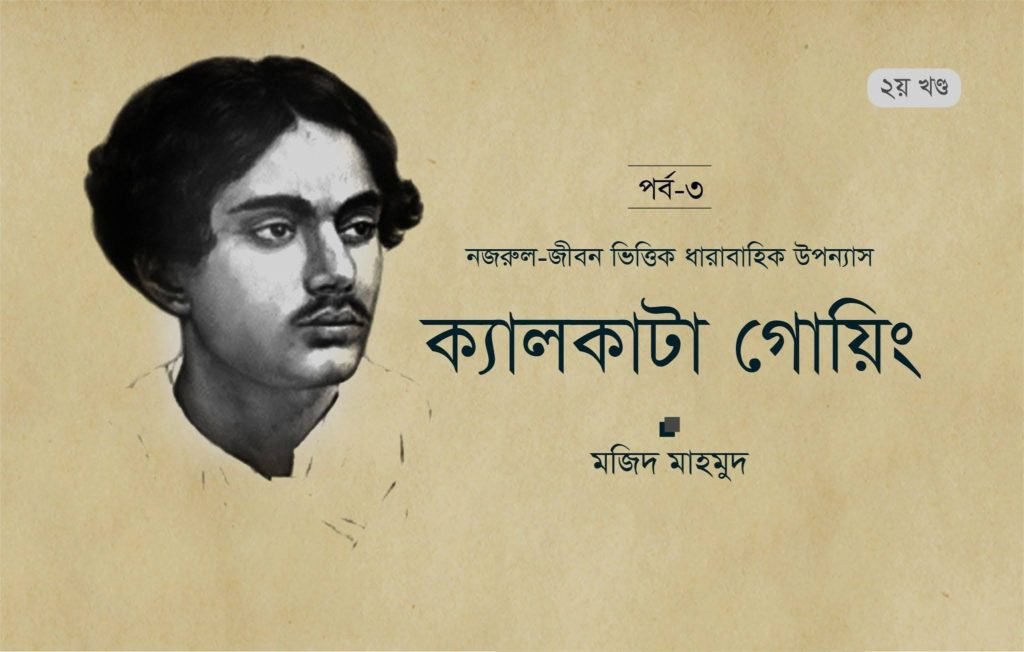পর্ব-১
আমার জন্মের রাতে খুব ঝড় হয়েছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠিক এমন ঝড় হয় না, ঈশান কোণ থেকে দিকচক্রবাল অন্ধকার করে উঠে এসেছিল মেঘ, কালবোশেখি ঝড়ের সঙ্গে ছিল তার মিল, ঘরের চালা উড়ে গিয়েছিল, জল-বাতাসের তেরচা ঝাপটায় মাটির দেওয়ালে ফাটল ধরেছিল—হয়তো সে-কারণে আমার জীবনীকারদের অনেকে বিশ্বাস করতে চায় নি ‘আমার জন্ম এগারই জ্যৈষ্ঠ।’ জ্যোতিষী বি. আর. ব্যানার্জীর কুষ্ঠিতে লিখেছিল—১১ই বৈশাখ, সুফি জুলফিকার হায়দারও তার এই মত সমর্থন করেছিল। মানব-জন্মে যদি গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব থাকে, বছর গণনার রাশিফল যদি ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করে, মানুষের চরিত্র গঠনে যদি জলবায়ু ও পরিবেশে ভূমিকা থাকে—তাহলে আমার জন্ম ১১ই বৈশাখই অধিক যুক্তিযুক্ত।
যারা বলেন ১১ই জ্যৈষ্ঠ ধরে আমার জীবদ্দশায় বেশ কবার জন্মদিন পালিত হয়েছে, আমার নির্বাক জীবনের আগেই—এ দিন ধরেই আব্দুল কাদির দৈনিক ‘কৃষক’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিল—যদি দিনটি সঠিক না হবে তাহলে আমি কিভাবে সমর্থন করলাম। তাদের এই অকাট্য যুক্তির দ্বারা আমার জন্মদিন প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মীমাংসা অনিষ্পন্ন থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেও জানতাম না—আমার জন্মদিন কবে, পরিবারের কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, যেখানে দিন-গুজরান কুণ্ঠাগত—সেখানে জন্মদিন লিখে রাখা বিলাসিতা। আমিও শুনেছিলাম মায়ের কাছে—আমার জন্মেদিন প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল, আম-কুড়ানো ও আম-পাকার গল্প এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল—পরিবারের এই গল্প থেকে আমিও ভেবেছিলাম—আমার জন্ম বাংলা সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কোনো একদিন হবে। হয়তো প্রথম দিকের জীবনীকাররা এই গল্প থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিল—১১ই বৈশাখের চেয়ে ১১ই জ্যৈষ্ঠ আমার জন্ম তারিখ হলে আখেরে ভালো হবে। কারণ আমার জন্ম হয়েছিল—বাংলা সাহিত্যাকাশের রবিচ্ছটার নিচে—শশীর একাদশীতে, ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিল—২৫ শে বৈশাখের আগে এই পথভোলার জন্মদিনের প্রস্তুতির মধ্যে কিছুটা অস্বস্তির কারণ ঘটতে পারে, হয়তো একদিন জন্মদিনও পালিত হবে—রবীন্দ্র-নজরুল দ্বৈরথে, আমিও থাকতে চেয়েছিলাম তাঁর ছায়ায়—এ ধরায় এলাম যখন তাঁর এতটা পরে—জন্মদিনে আগে থেকে কী লাভ! আমার মৌনতার জয় হলো, আর আমি বেঁচে গেলাম অজ্ঞতার পাপ থেকে।
এক ফকির আশ্বাস দিয়েছিলেন—এ ছেলে কেবল বাঁচবেই না, জগদ্বিখ্যাত হবে।
কিন্তু এই ইঙ্গিত কেউ বুঝতে চাইল না—আমি আসলে প্রকারন্তরে বলে দিয়েছিলাম—আমার জন্ম ঠিক ভরা বৈশাখে। তারা আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’র ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতেন—আমি আসলে কী বলতে চেয়েছিলাম। ‘বিদ্রোহী’র মতো কবিতাকে দ্বিতীয় রেখে আমি আমার আগমন বার্তা ঘোষণা করার জন্য শুধু লিখেছিলাম—
ঐ নতুনের কেতন উড়ে কাল-বোশেখির ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
এটা তো আমারই আগমনের বার্তা ছিল। কেবল জন্মদিন নয়, জন্ম সালটাও আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, যদি আমার অন্য দুই সহোদরের জন্ম তারিখ ও সাল জানা থাকত—তাহলে দাবি করা যেত, তাদের জন্ম সাল অজ্ঞাত হলে এই মধ্যম সহোদরের জন্ম তারিখ ঠিকঠাক থাকে কি করে, আমি তো তখন তাদের মতোই অজ্ঞাত ছিলাম; আমার পিতার জন্ম তারিখ, আমার মাতার জন্ম তারিখও আমাদের জানা ছিল না। এক-আধ বছর কমবেশি করে জন্ম সাল লেখা ইংরেজের শিক্ষা-রীতির ফাঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ভবিষ্যতে চাকরি বাকরির সুবিধা পাওয়ার জন্য—স্কুল সার্টিফিকেটে এমনটি প্রায়ই করা হয়ে থাকে। এমনকি আমার দুই পুত্র সানি ও নিনির জন্ম সালও এক বছর কমিয়ে দেয়া হয়েছিল সজ্ঞানে। ফলে আমার জন্ম তারিখ ও মাস জ্যৈষ্ঠ না হয়ে বৈশাখ হলে ১৮৯৯ না হয়ে ১৯৯৮ হলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না।
আমার জন্ম নিয়ে অনেক গল্প শুনেছিলাম বড়দের কাছে, আবার এমন অনেক গল্প আমি বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের কাছে না শুনলেও লোকজন বলাবলি করত। এসব কথার প্রতিবাদের কোনো দরকার ছিল না যে, তারা এমন এক নজরুলকে দেখতে চেয়েছিল, যার জন্মের সঙ্গে কিছুটা অলৌকিকতা জুড়ে না থাকলে তার অসাধরণত্ব প্রমাণ হয় না। জন্মের পরে আমি তিন দিন কোনো শব্দ করি নি; যে ছেলে জন্মের সময় কাঁদে না—তার পরমায়ু নিয়ে সন্দেহ থাকে, আমার বেলা আরো বেশি ছিল, কারণ আগে আরো চার ভাই মারা গিয়েছিল—আমার বাঁচাটা ছিল দৈবাৎ, বাঁচলেও বোবা হয়ে বাঁচতে হবে। এক ফকির আশ্বাস দিয়েছিলেন—এ ছেলে কেবল বাঁচবেই না, জগদ্বিখ্যাত হবে। সংসারিরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলে আমার নাম দুখু মিয়া হতো না, একাদিক্রমে বাবা-মার চার সন্তানের মৃত্যুর পরে আমার মা ঝুঁকি নিতে চান নি, তাই নাম রেখেছিলেন—দুখু মিয়া, এমন নামের দুঃখের কুণ্ডলীকে নিশ্চয় জমে ছুঁবে না। শেষ পর্যন্ত জমের সত্যিই অরুচি হয়েছিল—সারা জীবন আমায় দুষ্টগ্রহ তাড়া করে ফিরলেও সব সময় মরতে মরতে বেঁচে গেছি, এমনকি মারাত্মক আঘাতে নির্বাক হয়েও চৌত্রিশ বছর বেঁচে গেলাম। আমার জন্মের আগে আমার মা হাজি পালোয়ানের দরগায় সিন্নি দিয়েছিলেন—তারাপীঠে মানত করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—পীর ও দেবতার টানাটানিতে আমার দফারফা হলেও কেউ তার দাবি ছাড়ে নি। চুরুলিয়ায় মুসলমান পাড়ায় আমার জন্ম, পরিবারে হিন্দু ঐতিহ্য বিশ্বাস একেবারে উপেক্ষিত ছিল না। আমি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে চলতে চেষ্টা করেছি—মুসলিম পীর-ফকির ও হিন্দু-সন্ন্যাসী আমার জীবনে জড়াজড়ি করে থেকেছে।
কিন্তু ‘চিরিদনি কাহারও সমান নাহি যায়/ আজিকে যে রাজাধরিাজ কা’ল সে ভিক্ষা চায়।’ আমারও যায় নি, কেবল নিজের জীবন নয়—পরিবারের জীবনেও ছিল নানা উত্থান-পতন। আমার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বিহারের সাঁওতাল পরগনার হাজিপুর থেকে। এ কথা শুনলেই অনেকের মনে উদয় হতে পারে—বিহার বুঝি অন্য কোনো দূরের দেশ; প্রকৃতপক্ষে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তখন একই সুবার অধীনে, মোগল ভারতে এক সুবেদার, এমনকি স্বাধীন নবাবের অধীনে একটি প্রশাসনিক এলাকা। হাজিপুর থেকে আমার পূর্ব-পুরুষ বর্ধমানের আসানসোল মহাকুমার জামুরিয়া থানার যে চুরুলিয়া গ্রামে এসে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন তার দূরত্ব খুব একটা বেশি ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, খুব সামান্যের জন্য আমি ‘বিহারি’ হয়ে যাই নি—কারণ চুরুলিয়া গ্রামটি বাংলার শেষপ্রান্ত হলেও বিহার সীমান্তের সন্নিকটে—এ অঞ্চলের অর্ধেক মানুষের মুখের ভাষা ছিল বিহারি।
বাবা ও নিকট আত্মীয়দের কাছে শুনেছি, আমার চাচা বজলে করিমও বলতেন—‘আমাদের অবস্থা একদিন এমন ছিল না। বলতে পারিস, নবাবের সঙ্গে ছিল আমাদের সম্পর্ক। আমরা ছিলাম একদিন এ অঞ্চলের মানুষের দণ্ড মুণ্ডের অধিকর্তা।’
‘না, নবাব কিংবা সেনাপতি না থাকলেও মর্যাদায় কম ছিল না—চিরকালই বিচারকদের অবস্থান ছিল সবার উপরে।’
‘বিচারকের সামনে সিংহাসন থেকে নেমে এসে বাদশাহকেও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। আমাদের পরিবার ছিল সেই ‘কাজী’—যদিও আজ—কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই।’
চাচা বজলে করিম ছিলেন আমার দাদা কাজী আমিনউল্লাহ’র এক ভাইয়ের সন্তান।
আমার পূর্ব পুরুষের যে ইতিহাস ছোটবেলায় শোনানো হয়েছে, তাতে মনে হয়—এ দেশের অধিকাংশ উচ্চবর্গের মুসলমানের মতো আমার পূর্ব-পুরুষ এসেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ থেকে—ভাগ্যের অন্বেষণে। মোগল বাদশার সেনাবাহিনি কিংবা প্রশাসনের উচ্চ পদে চাকরির জন্য বংশ মর্যাদার দরকার হতো, এ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কখনো তা অবাধ ছিল না।
চুরুলিয়া মূলত আমার মাতুলালয়, বাবা দুইবার বিয়ে করেছিলেন এই গ্রামে।
তাছাড়া একটি বংশ লতিকাও আমার মুখস্থ ছিল যেমন—‘হযরত গোলাম নকশবন্দের পুত্র কাজী কেফাতুল্লাহ, তার পুত্র কাজী খেবরোতুল্লাহ, তার পুত্র কাজী গোলাম হোসেন, তার পুত্র কাজী আমিনউল্লাহ, তার পুত্র কাজী ফকির আহমদ, তার পুত্র কাজী নজরুল ইসলাম।’ হযরত গোলাম নকশবন্দের সপ্তম অধস্তন পুরুষ অধম আমি। এই বংশ লতিকা সত্য হলে, এটা দাবি করা ঠিক হবে না—সাত পুরুষ আগে কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ব পুরুষ বাঙালি ছিলেন। আর তখন বাঙালি হওয়া সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমানের জন্য গর্বেরও ছিল না। বিশ শতকের শুরুর দিকে শরৎচন্দ্র তাঁর ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে লিখেছিলেন—‘ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ‘ফুটবল ম্যাচ’—তাঁর এই অপরাধ বর্তমানে বাঙালি মুসলমান ক্ষমা করতে না পারলেও তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় মিথ্যা নয়।
আমাকে বলা হয়েছে, ‘আমার ঊর্ধ্বতন প্রপিতামহ কাজী কেফাতুল্লাহ ছিলেন ‘কাজী-উল কুজ্জাৎ’—আপীল বিভাগের প্রধান বিচারপতি ‘সদরস সদুর’ না হলেও স্থানীয় বিচার বিভাগের প্রধান। মোগল আমলেও বিচার বিভাগ প্রশাসনের অনেকটা প্রভাবমুক্ত ছিল, দিল্লির সম্রাট স্বয়ং নিয়োগ দিতেন তাদের। ফলে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে তাদের খুঁনসুটি লেগে থাকত। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে মোগল সাম্রাজ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়, এক. অযোগ্য শাসন ব্যবস্থা দুই. ইংরেজ কোম্পানির কাছে নবাবের পরাজয়; পাশাপশি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় আমার পূর্ব-পুরুষ কাজীরা হাজীপুর থেকে চুরুলিয়ায় চলে আসে—সম্রাট শাহ আলমের সময়ে। হাজীপুর বর্তমানে বৈশালি জেলার মধ্যে পড়েছে, বলা হয়ে থাকে এখানে পৃথিবীর প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—গ্রিসেরও আগে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত হলেও আগে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। মহাবীর ও আজ পালির জন্মও এই জেলায়। এই সমৃদ্ধ একটি এলাকা থেকে কেন আমার পূর্বপুরুষ চুরুলিয়ায় এসেছিলেন, এই প্রশ্নের জবাবে আমাকে জানানো হয়েছিল—‘পাটনার শাসনকর্তা সৈয়দ হুসেন আলীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব এড়াতে তারা চুরুলিয়া চলে আসে।’ আসলে আঠার ও উনিশ শতক বাংলা তথা ভারতের জন্য এক অস্থির সময় ছিল- একদিকে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও দেশীয় নানা রাজন্যবর্গের উত্থান, অপরদিকে বহির্শক্তি ইংরেজের আগমনে পুরনো কাঠামো পর্যুদস্ত হওয়া। এ সময় ধনী গরিব হয়ে গিয়েছিল, শিক্ষক ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছি, পেশায় পরিবর্তন আসছিল, পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে নতুন ব্যবস্থার উদ্ভব হচ্ছিল। আমিও আমার পরিবার এই অস্থির সময়ের শিকার।
সেদিনের চুরুলিয়া আজকের মতো এত অনুন্নত গ্রাম ছিল না—এক সময়ে অস্ত্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল এলাকাটি, আমার শৈশবেও দেখেছি নরোত্তম সিংহের পরিত্যক্ত গড়, একদা এটি এই দেশীয় রাজার রাজধানি ছিল, এ অঞ্চলের অনেক বাড়ি বানানো হয়েছে এই গড়ের ইট ও পাথর দিয়ে। এছাড়া এখানে একটি বিচারালয় ছিল, মসজিদ ও মক্তব ছিল- আর এই সব দেখভালের এনাম স্বরূপ যথেষ্ট আয়মা সম্পত্তি ছিল। কাজীরা সেই আয়মা সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, স্থানীয় আদালত, মক্তব মসজিদের খাদেমের দায়িত্বও তাদের উপর বর্তেছিল। কিন্তু আমার বাবার জন্মে সে-সব তেমন ছিল না, কিছু গল্প কিছু পুরনো খান্দানির ভগ্নাবশেষে অসীম দরিদ্রতায় আমার জন্ম। আয়মাদার হিসাবে পিতা যে সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তা দিয়ে আমাদের সংসার কষ্টে-সৃষ্টে চলে যেতো, মসজিদ ও মাজারের খাদেমগিরি থেকেও কিছুটা উপার্জন হতো।
আমার বাবার হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর, মুক্তার দানার মতো আলাদা করে চেনা যেতে—অক্ষরগুলো এক সঙ্গে জুড়ে দেয়ার পরে—অর্থপূর্ণ বাক্যের সপ্রাণ মাল্যের মতো দৃষ্টির সামনে ঝুলে থাকত। ছাপাখানা যুগ সর্বত্র চালু হওয়ার আগে হাতের লেখার শৈলী বিশেষভাবে মূল্যায়িত হতো, এর জন্য অনেক অফিসে জল-খাবার দেয়া হতো। এই লেখা থেকেও আমার বাবা কিছুটা আয় করতেন, এলাকার জমিজমার দলিল লেখার কাজও তিনি করতেন, সব মিলে অস্বচ্ছল বলা যাবে না। গ্রাম-গঞ্জে তখন একটি প্রবাদ ছিল—‘কাজীর বাড়ির বেড়ালও এক ছিফারা পড়তে পারে।’ অর্থাৎ আমার সময়ে বিত্ত কম থাকলেও চিত্ত বেশ সমৃদ্ধ ছিল, তৎকালীন আরবি ফারসি জ্ঞান—সেই নিয়মে পড়াশোনা অভাব ছিল না। সেদিক থেকে বাড়িতে হাফিজ রুমি শাদি খৈয়ামের চর্চা ছিল, কিছু বই পুস্তুকও ছিল।
চুরুলিয়া মূলত আমার মাতুলালয়, বাবা দুইবার বিয়ে করেছিলেন এই গ্রামে। বাবা ফকির আহমদের চেহারা ছিল কথিত রাজপুত্রের মতো, আমরা তার ছিটেফোঁটা পেয়েছি; চেহারার সৌন্দর্য ও রাজকীয় মনোভাব তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল—সততা সাহস ও ধর্মপরায়ণতাও আপসহীন। অলসতা ক্রীড়াপ্রিয়তা তার চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ধর্ম পালন ও দার্শনিকতা তাকে কর্মবিমুখ করে তুলেছিল। মায়ের মুখে শুনেছি শেষ বয়সে তার পাশা খেলার নেশায় পেয়ে বসে। স্থানীয় জুয়াড়ি মহানন্দ আশের খপ্পরে পরে প্রায় সর্বশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মতো তিনিও ছিলেন নিস্পৃহ, জীবনের সকল কিছুকে হেলায় হারিয়ে দেয়ার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন- তার চারি-পার্শ্বের ব্যথা-বেদনা তাকে খুব কমই স্পর্শ করেছে। আপাত মনে হতে পারে শকুনির কুচক্রান্তে ধর্মপুত্র একে একে সব হারিয়ে ফেলছেন, কিন্তু সর্বহৃত পাণ্ডবরা একদিন কামক্রোধ জয় করে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে সব কিছু পুনরুদ্ধার করেছিলেন, সেদিন না হারালে তাদের অর্ধেকটা রাজ্য, কিংবা অনুগৃহীত একটি গ্রাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতো, কিন্তু সেদিন অর্ধেক হারিয়ে পূর্ণটা ফিরে পেয়েছিলেন। আমিও হয়তো পিতার চরিত্র পেয়েছিলাম, অথবা পিতাকে মহাভারতের জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হিসাবে দেখলে আমি ছিলাম তাদের ভাগ্য বিড়ম্বিত ভ্রাতা। পিতা সব কিছু হারিয়েছিলেন বলেই আমি সকল কিছু ফিরে পেয়েছিলাম। পিতার চল্লিশ বিঘা জমি পাশা খেলে একদিন খুইয়ে ছিলেন বলেই—
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
ভাবি আর কত যে দৃশ্যপট মনের মধ্যে তৈরি হয়। প্রেমের বসতি কি শরীরকে বাদ দিয়ে সম্ভব?
আহা! কবিগুরু যেন আমার জন্যই লিখেছিলেন, পিতার উচ্ছৃষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকার হলে চুরুলিয়াকে ধরে, স্থানীয় মক্তব—বড়জোর সিয়ারসোল রানিগঞ্জ স্কুল পাস করে, হয়তো আমার শিক্ষক কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মতো কবি হয়েই জীবন কাটিয়ে দিতাম। বাংলার এক সীমান্ত থেকে আরেক সীমান্ত পর্যন্ত গ্রামগঞ্জের নিরন্ন দুখী মানুষের সঙ্গে দুখী হয়ে এতটা মিশে থাকার সুযোগ পেতাম না।
আমার পিতার প্রথম স্ত্রী সৈয়দা খাতুন আমার বোন সাজেদা খাতুনের জন্ম দিয়ে অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন। আমাদের ভাই-বোনের জীবনে তার কোনো স্মৃতি নেই। বোন সাজেদা খাতুন আমাদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, আমার দুরন্তপনা মায়ের একার পক্ষে সামল দেয়া সম্ভব হতো না। মা’র কাছে শুনেছি তার আগেও আমাদের এক মা ছিলেন—একদিনের উলা উঠায় মারা যান, খুব অল্প বয়সে কুড়ি বছরের কোটায়—আমার মায়ের রূপ নাকি তার তুল্য নয়। পৃথিবীতে নিজের মায়ের রূপ ও গুণ সেরা হলেও আমার মায়ের মতো নয়, তবু আমার আরেকজন মা ছিলেন, তিনি আরো সুন্দরী ছিলেন, আরো গুণবতী ছিলেন—এসব শুনে শুনে আমার মনে তার অক্ষয় রূপ অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। আমি মনে মনে ভাবতাম, এমন তো হতে পারে, আসলে সেই মহিলাই ছিল আমার আসল মা, বর্তমান মায়ের কাছে রেখে গেছে, সে আমায় লালন-পালন করছে মাত্র। দূর থেকে তিনি সর্বদা আমায় দেখছেন। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে আদি কালের মুসলিম সতী নারীদের মাতৃরূপ ও পত্নীরূপের গল্প পবিত্রতার সঙ্গে পাঠ করা হতো। আমরা দিব্যচোক্ষে সে-সব দেখতে পারতাম—পুণ্যবতী হাজেরা—যিনি তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য উত্তপ্ত মরুভূমিতে সাফা-মারোয়ার মাঝখানে এক ফোঁটা পানির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন, হযরত আছিয়া কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত স্বামীর জন্য ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—খারাপ লোকের কুচক্রান্ত উপেক্ষা করে অসুস্থ স্বামী সেবা করেও তাঁর মন পাচ্ছে না, পুণ্যবতী খাদিজা কিভাবে তার ধ্যানস্থ স্বামীর জন্য খাড়া পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ গুহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে যশোদা, কুন্তি, গান্ধারী, সীতা, পার্বতী, জগজ্জননী সারদা মা, শচী মাতার মতো বহু মায়ের করুণ কাহিনি শৈশবে আমাদের শোনানো হয়েছে। এসব গল্পে নারীদের মহত্ত্ব বর্ণনা শুনে শুনে একদিকে তাদের ত্যাগ ও কষ্টময় সহিষ্ণু জীবনের প্রতি অকৃষ্ট হয়েছিলাম, অপরদিকে তাদের বঞ্চনা ও পুরুষ জাতির উপেক্ষাও আমায় কষ্ট দিয়েছিল।
আমার পিতার প্রথম স্ত্রীর মতো আমার মা জাহেদা খাতুনের জন্মস্থানও ছিল চুরুলিয়া গ্রাম, নানা মুনশি তোফায়েল আলী এখানকার মুসলমান পাড়ায় সম্ভ্রান্ত ভূ-স্বামী। ভালোই হয়েছিল—দুই বোন ও তিন ভাইয়ের জন্য দুই বুনিয়াদি মাতুলালয় এবং পিতার দিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু কাজী পরিবার মিলে চুরুলিয়ায় আমাদের আনন্দময় শৈশব কেটেছিল। কিন্তু সেই সময়টি পরিবারের বয়স্ক কারো মধ্যে কোনো আনন্দ ছিল না, এক অজানা বিষণ্নতা সর্বদা বড়দের গ্রাস করেছিল। সবার চোখে মুখে এক অজানা হতাশা ঝরে পড়তে দেখা যেত। আমি যতটুকু স্মরণ করতে পেরেছি—তার অন্যতম ছিল অতীতে একদিন মুসলমানদের সব ছিল। তারা ছিল রাজার জাত। ইংরেজ তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। যদিও আমার জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর আগে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের পরাজয়ে মধ্য দিয়ে এ দেশে চূড়ান্তভাবে মুসলমান শাসনের অবসান হয়েছে। তবু তারা তখনো এক অলৌকিক পুনরুদ্ধারের দিবাস্বপ্ন দেখে চলেছেন। পরবর্তীকালে এর অনেকটা আমি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি ‘আনোয়ার’ কবিতার মাধ্যমে :
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার—
তলোয়ার শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!
যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিকদার!’
তবে বড়দের মধ্যে যতই হতাশা থাক—তা আমার শৈশবকে তেমন স্পর্শ করতে পারে নি। যদিও রাঢ় বাংলায় আমার জন্ম হয়েছিল, শুষ্ক ও রুক্ষ মাটি, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া হওয়া সত্ত্বেও গ্রামটি ছিল অদ্ভুত সুন্দর। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার গেলে অজয় নদী। নদীর ওপার গেলেই বিহারের ঝাড়খণ্ড, নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে বীরভূম জেলা। গ্রামের পূর্ব দিকে প্রায় একশ কিলোমিটারের মধ্যে লোকালয় নেই বললেই চলে, পশ্চিম দিকেও প্রায় তিরিশ কিলোমিটার বর্ধমান জেলার অংশ হলেও জনপদের চিহ্ন ছিল কম। ফলে চুরুলিয়া গ্রামটি ছিল যেন মরুভূমির মধ্যে একটি মনোরম মরূদ্যান।
আমার জন্ম বর্ধমানে হলেও মাত্র তিন মাইল দূরে অজয় নদীর পাড়ে বীরভূমে বাংলা সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছিল। মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতী এই নদীতীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। জানি না কিসের ইঙ্গিতে আমার জন্ম-সালের কাছাকাছি সময় থেকে আধুনিকালের সেরা কবি আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অজয় নদীর অববাহিকায় বোলপুর আশ্রম গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। হয়তো আমাকে দিয়ে প্রভু চতুষ্কোণ পূর্ণ করবেন বলেই এই কিংবদন্তি নদী তীরে আমায় উৎপন্ন করেছিলেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাস আর এই নদীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা মিথ ও লোক পুরাণ। অজয় নদীর তীরে বীরভূম কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সারা বছর ধরে চলত উন্মাদনা।
পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিনব্যাপী মহা-সমারোহে শুরু হতো এই মেলা। হাজারো পসরা, অজয় নদের ধার, সর্ষের খেত, শীত মাটির গন্ধ, জনসমাগম, সবমিলিয়ে মহাধুমধাম চলত কেন্দুলিতে। অতিরিক্ত পাওনা ছিল আখড়ায় আখড়ায় বাউল গান, বাউলদের পীঠস্থান এই কেন্দুলি। দূর দূরান্ত থেকে যেমন মানুষ হাজির হতো এখানে, তেমনই সব জায়গা থেকে বাউলরাও হাজির হতো এখানে। ছোটবেলায় বড়দের সঙ্গে প্রতি বছর আমরা দল বেঁধে গেছি এই মেলায়।
কামনায় শরীর যতই বিকারগ্রস্ত হোক, যত ক্ষমতাবানই হোক, গায়ের জোরে প্রেম আদায় করা যায় না।
পৌষের কুয়াশা ভরা ভোর, বেলা বাড়লে ছড়িয়ে পড়ে মিঠে রোদ, চেনা গন্ধ নাকে এসে লাগে। এটাই শীতের বর্ধমান বীরভূম অজয় চুরুলিয়া—একাকার। গঙ্গাসাগর যেমন পৌষ সংক্রান্তির একটি গন্তব্য, তেমনি রাজ্যের দ্বিতীয় গন্তব্যটি অবশ্যই জয়দেব কেন্দুলির মেলা। যেখানে মানুষের সঙ্গে বাউলের মহামিলন হয়। বাউলদের তীর্থস্থান হিসাবেও কেন্দুলি পরিচিত ছিল তখন। বাউলদের মনকাড়া সুর এক আজানা রহস্যময় মহাদিগন্তের দিকে টানতে থাকে—ভাবময় চিন্তাশীল কোনো কিশোর ‘অতিথি’ গল্পের তারাপদের মতো আর ঘরে থাকতে পারে না।
কথিত আছে, কবি জয়দেবের মা যখন মৃত্যুশয্যায়, ছেলের কাছে গঙ্গাজল মুখে দেওয়ার শেষ ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু এখানে গঙ্গাজল কোথায় পাবেন! মায়ের তখন শেষ অবস্থা, তাঁকে গঙ্গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। আর তাঁর পক্ষেও অতদূর গিয়ে গঙ্গা জল আনতে আনতে মা ভবলীলা সাঙ্গ করবেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই ইচ্ছার কথা সর্বান্তকরণে জানালেন কবি জয়দেব। ঈশ্বরের কৃপায় সেই ইচ্ছাপূরণও হলো তার—পৌষ সংক্রান্তির দিন ক্ষণিক সময়ের জন্য অজয় নদের জল উল্টোদিকে বইতে শুরু করে। ঢুকে গঙ্গার ঘোলা জল! সেই জলই মায়ের মুখে তুলে দেন জয়দেব। সেই থেকেই পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রায় শুকনো অজয় নদের জলে স্নান করা মহাপুণ্য বলে বিশ্বাস করেন মানুষজন।
জয়দেবের অলৌকিতা নিয়ে আরো অনেক গল্প চালু ছিল, যেমন লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেবের আগমন নিয়ে—একদিন লক্ষ্মণসেনের সভায় এক বিখ্যাত সংগীতনিপুণ কবি-গায়ক এসে নিজেকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রকাশ করলেন। রাজাও মুগ্ধ হয়ে তার দাবি স্বীকার করে নিলেন, আয়োজন করলেন তাকে সর্বোচ্চ সম্মান জয়পত্র দেয়ার। খবর পেয়ে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী রাজসভায় এসে অনুরোধ করলেন, তার স্বামীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে যেন আগত কবিকে জয়পত্র দেয়া না হয়। রাজা সভায় জয়দেবকে ডেকে আনলেন। তথাকথিত সংগীতনিপুণ কবির গানে গাছের সব পাতা ঝরে গেল, সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। জয়দেব বললেন এ আর এমন কী! গাছে পাতা তো বসন্তকালে এমনিতেও ঝরে যেতে পারে, গাছে আবার পাতা গজিয়ে দেখাও দেখি। সেই কবি অপারগতা প্রকাশ করলেন, তখন জয়দেব গান ধরলেন, আর সাথে সাথে গাছের পাতা গজিয়ে উঠতে থাকল। সকলে জয়দেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন। এমনকি তার কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অনেক অলৌকিক বিচার করা হয়ে থাকে।
জয়দেব তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘গীতগোবিন্দ’ রচনাকালে কিছুতেই উপসংহারে আসতে পারছিলেন না, কবি দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন, ভাবছিলেন—তিনি কিভাবে ‘মানভঞ্জন’ পালায় রাধার মান ভাঙাবেন? তিনি এই সব ভাবতে ভাবতে প্রতিদিনের মতো প্রাতে গঙ্গাস্নানে গেলেন, বাড়িতে কেবল তার সাধন সঙ্গী স্ত্রী পদ্মাবতী স্বামীর ফেরার অপেক্ষায় আছেন। এমন সময় পদ্মাবতী দেখলেন অন্য দিনের তুলনায় আগেই তার স্বামী স্নান সেরে ফিরে এসেছেন, মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ ত্বরিত পুঁথি নিয়ে বসেছেন। পদ্মাবতীও স্বামীর উচ্ছৃষ্ট প্রসাদ করছেন ভক্ষণ; এমন সময় ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন—তার স্বামী আবার স্নান সেরে ফিরছেন, ভয়ে-বিস্ময়ে পদ্মাবতী এর রহস্য জানতে চাইলেন কবির কাছে। জয়দেব তো অবাক, তিনি এসবের কিছুই জানেন না। অবশেষে অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থের কাছে গিয়ে দেখলেন, কেউ একজন ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের মানভঞ্জন পর্বের পাদপুরাণ পর্বে অপূর্ব এক পঙ্ক্তি লিখে রেখে গেছেন—‘স্মরগরলখ-নং মম শিরসি ম-নং দেহিপদপল্লবমুদারম’। কৃষ্ণ স্বয়ং রাধার চরণ মাথায় ধরে তার পরকীয়া সাধন মানুষের শিরোধার্য করেছেন।
তারাশঙ্কও একবার জয়দেবের কেন্দুলি মেলায় গিয়ে লিখেছিলেন—‘ইতিহাস না কিংবদন্তি না বিশ্বাস সে-বিতর্কে না গিয়েও মনে তো একটা শিহরন হয়ই। মনকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। কী আশ্চর্য সমর্পণ! কামনায় শরীর যতই বিকারগ্রস্ত হোক, যত ক্ষমতাবানই হোক, গায়ের জোরে প্রেম আদায় করা যায় না। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও বিনীত হয়ে রাধাকে বলতে হয়, তোমার পা দুটি আমার মাথার উপর রাখো। আমার বিকার দূর হোক। ভাবি আর কত যে দৃশ্যপট মনের মধ্যে তৈরি হয়। প্রেমের বসতি কি শরীরকে বাদ দিয়ে সম্ভব? বৈষ্ণব সাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা এরকম কত পদ যে কি মাত্রায় আধুনিক আর শিক্ষণীয় তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।’
জয়দেব আদি বাঙালি কবিদের অনুপ্রেরণার উৎস হলেও রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ দরবারে তিনি সংস্কৃতি ভাষায় কাব্য-চর্চা করতেন। কিন্তু বাঙালির প্রথম সার্থক কবি চণ্ডীদাসের জন্মও এখানে, কিছু বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও এটি বলা যায়—তিনি জীবনের একটি বড় সময় এখানে কাটিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের একাধিক চণ্ডীদাস ও তার জন্মস্থান নিয়ে যত বিতর্কই থাক আমার শৈশবে অজয় নদীর তীরে এই কবিকে কল্পনা করতে পেরে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি। বালক কবি নিজেই হয়ে উঠেছে জয়দেব চণ্ডীদাস। পরবর্তীকালে ম্যাডান থিয়েটারের হয়ে জয়দেব নিয়ে কাহিনি লিখেছি, জয়দেব সিনেমায় অভিনয় করেছি, সংগীত রচনা ও সুর সংযোজন করেছি। এসবই আমার শৈশব স্মৃতির অংশ।
জয়দেব ও চণ্ডীদাসের লোকগাঁথা ও মেলা শৈশবে আমায় কবি হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।
জনশ্রুতি আছে, চণ্ডীদাসের বাবা ছিলেন এলাকার একজন ছোটখাটো ব্রাহ্মণ জমিদার, তার পুত্র হয়েও তিনি রজকিনী নামে এক ধোপাকন্যার প্রেমে পড়েন। সুন্দরী রজকিনীকে দেখে চণ্ডীদাস জাতপাত ভুলে যান, প্রেমিক-প্রেমিকার বাড়ির মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নদী। রজকিনী ওপারের ঘাটে কাপড় ধুতে এলে চণ্ডীদাস মাছ ধরার বড়শি নিয়ে এপারে বসে থাকত তাকে দেখার জন্য। এভাবে বার বছর কেটে যায়, একদিন রজকিনী চণ্ডীদাসকে জিজ্ঞেস করেন, ‘বড়শিতে কি মাছ ধরে গো গোসাঁই’—তখন থেকেই শুরু হয় তাদের প্রেমের কথোপকথন পালা। কিন্তু সমাজ তাদের এ প্রেম মেনে নেয় না, অপবাদে জর্জরিত হতে হয়ে একদিন তারা প্রেমের টানে ঘর ছাড়েন।
তাকে নিয়ে অন্য একটা কাহিনিও আছে—বীরভূমের নান্নুরে বাশুলীদেবীর মন্দিরের কাছে চণ্ডীদাসের কীর্তন দলের একটি নাট্যশালা ছিল। চণ্ডীদাসের কণ্ঠে একবার ভক্তিমূলক গান শুনে গৌড়শ্বরের স্ত্রী তার প্রেমে পড়ে যায়। চণ্ডীদাসের প্রতি বেগমের মুগ্ধতা জানাজানি হয়ে গেলে নবাব চণ্ডীদাসকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। কবিকে হাতির পিঠে বেঁধে চাবুক মেরে মেরে সবার সামনে তাকে হত্যা করা হয়। বেগম এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে শোকে মূর্ছিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। আবার অনেকে মনে করেন, শূদ্র কন্যার সঙ্গে প্রেমের অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়। যাই হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যের এই আদি কবি প্রেমের জন্য বলি হয়েছিলেন—তাতে সম্ভবত ভুল ছিলেন না। কবি ও প্রেমিক হিসাবে তিনিই হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি—এমনকি জাত-পাতের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন।
কবির প্রেম কবির নির্যাতন কবির সংগীত-প্রিয়তা ও স্বাধীনচেতা ছিল আমার ভৌগোলিক উত্তরাধিকার। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের লোকগাঁথা ও মেলা শৈশবে আমায় কবি হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সর্বোপরি চণ্ডীদাসের সেই মহান বাণী শিরোধার্য করে শৈশব থেকে সারা জীবন কবিতা ও জীবনের পথে হাঁটার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—
শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।