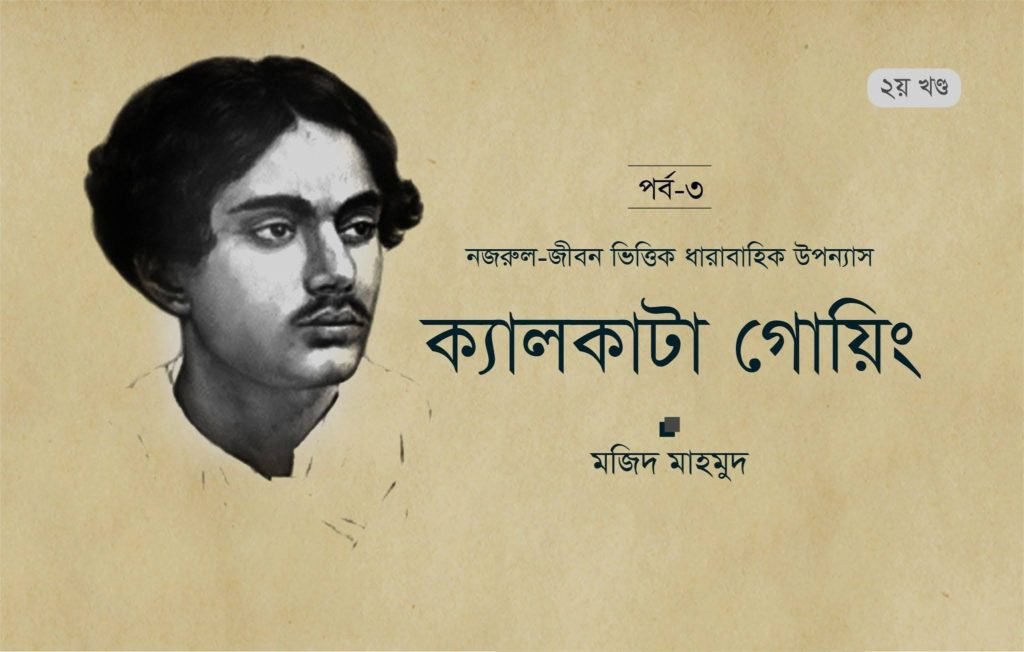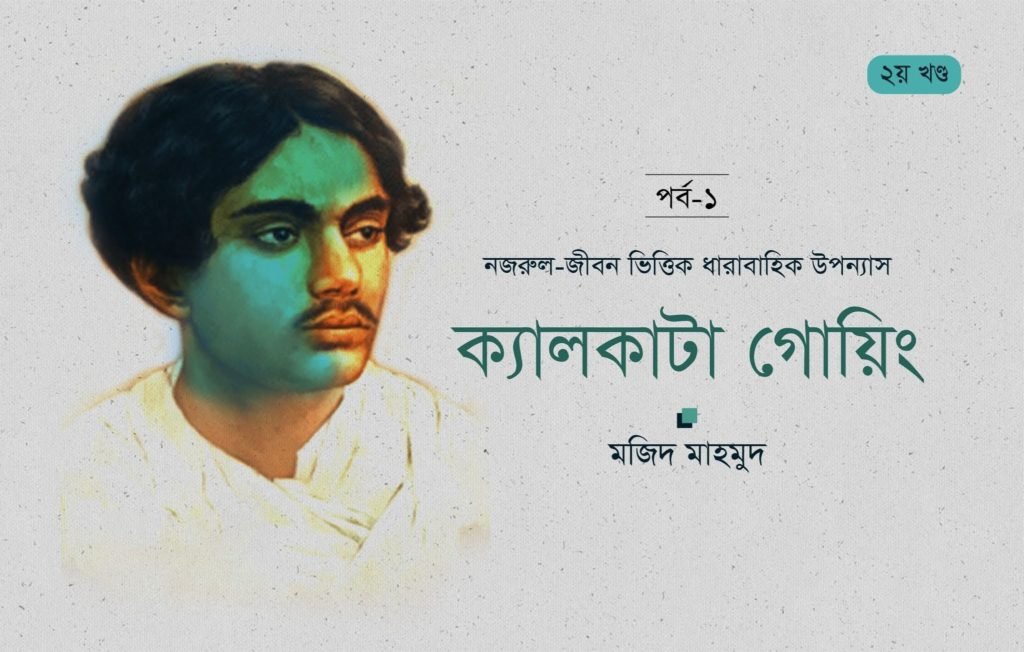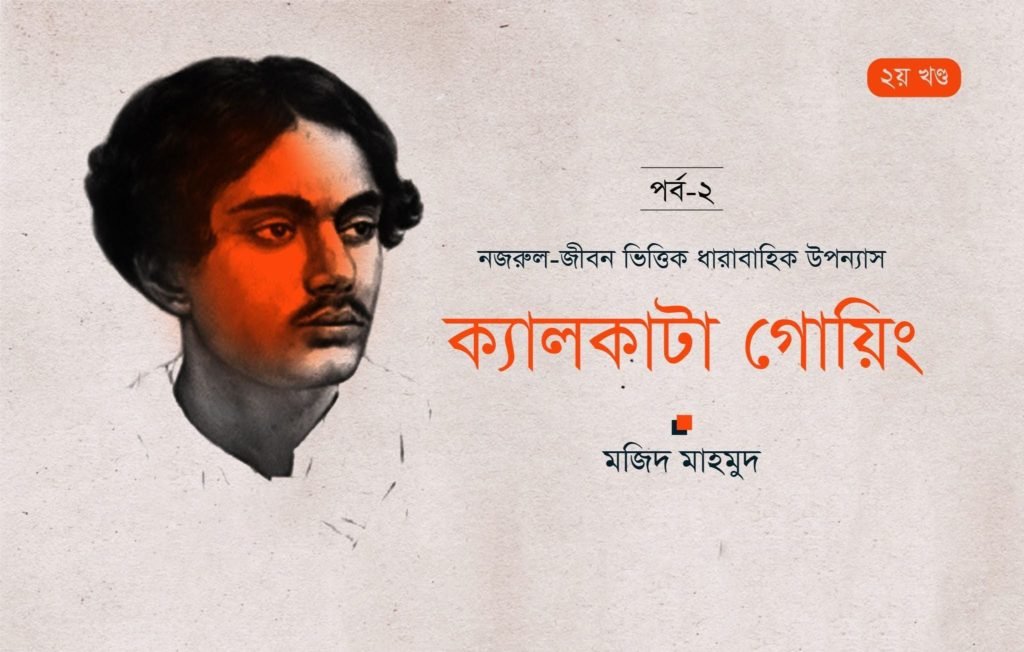পর্ব-৩
খুব অচিরের লক্ষ করলাম আমার ভেতর ব্যাপক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। পিতার মৃত্যুতে কষ্ট থাকলেও হঠাৎ করেই যেন স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। মনে হলো ছোট হলেও আমি আর ছোট নই, আমার সকল কাজের সিদ্ধান্ত এখন আমি নিজেই নিতে পারি। কেউ আর আমার কাজে খুব একটা বাধা দেয় না। এতে আমার দুরন্ত প্রকৃতি আরো দুরন্ত হয়ে উঠল। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দল বাঁধা, খেলাধুলা করা, মক্তবের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি প্রভাব বিস্তার তখনই আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল।
বিনোদ চাটুজ্যের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে এনে আমায় যে মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল, তার অবস্থাও ক্ষীয়মাণ। এই মাদরাসার ছাত্রদের প্রায় সবাই আমাদের মুসলমান পাড়ার, নিম্নবর্গের দুএকজন হিন্দু ছেলেরাও সেখানে পড়তে আসত। বাংলা বর্ণমালা, ইংরেজি ও অঙ্কের সাধারণ জ্ঞান ছাড়া এই মক্তবের অধিকাংশ পাঠ আরবি-ফারসি ও ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হতো। মক্তবে শিক্ষক সংখ্যা ছিল খুব কম, একজন শিক্ষকের কথা মনে আছে—মৌলবি কাজী বজলে আহমদ, তার কাছে শুরু হয়েছিল আরবি-ফারসি শেখার প্রথম তালিম। মক্তবে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তখন থেকে হেড-মৌলবি সাহেব আমায় বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে পাঠাতেন। আমার নিজ ক্লাসেও শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে আমি পাঠ দান করতাম। বাংলা ইংরেজি অঙ্ক—সব বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার মতো আমার সাহস এবং যোগ্যতা তৈরি ছিল বলে শিক্ষকগণ মনে করতেন। ছাত্ররাও শিক্ষক হিসাবে আমার সান্নিধ্য বেশ উপভোগ করত।
বিনোদ চাটুজ্যের পাঠশালাতে আমার ইংরেজি ভাষার ভিত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটাকে বলা চলে যুগের ফসল, ইংরেজ আমল হওয়ার কারণে প্রায়ই প্রত্যেকে দুএক ছত্র ইংরেজি ইশকুলে না গিয়েও শিখে ফেলতে পারত। বাড়িতে আরবি ফারসি চর্চা থাকলেও আমার পিতা ও চাচা বজলে করিমও ইংরেজি বলতে পারতেন। ইংরেজ আমল হওয়ায় ইংরেজ কবি রাজনীতিবিদ দার্শনিক ও সেনাপতিদের জীবনী নিয়েও স্কুলে আলোচনা করা হতো। শৈশবেই আমরা শেক্সপিয়ার, হোমার, গ্যারিবল্ডি, নেপোলিয়ান, আব্রহামা লিঙ্কলন, ভারতের ইংরেজর রানি-রাজার কাহিনি পড়ে ফেলেছি। বিদ্যাসাগরের বোধোদয়সহ অনেক শিশুশিক্ষা বইতে এসব থাকত। ইংরেজ মনীষীদের জীবনী ভালো লাগলেও রাজারানিসহ ইংরেজ শাসককুলের প্রতি আমার ঘৃণা জমা হয়ে উঠতে থাকে তখন থেকেই। আশেপাশের বহুলোক ইংরেজের অনুগত হলেও অধিকাংশ মানুষ এদেশের ইংরেজ শাসন পছন্দ করত না। তারা ভাবত মানুষ হিসাবে এটি তাদের অপমান, দেশমাতার অপমান। দেশমাতা পরাধীন ভেবে তাদের মধ্যে অক্ষম প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠত।
বড়দের কাছে গল্প শুনেছি, ইংরেজ আসার আগে এদেশের মানুষের এতটা কষ্ট ছিল না।
ভালো ছাত্র হিসাবে আমার খ্যাতি থাকলেও শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বন্দি থাকতে ভালো লাগত না। আণ্ডাল থেকে গৌরাণ্ডি পর্যন্ত যে ছোট্ট রেল লাইন চলে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি স্টেশন আমাদের চুরুলিয়া, তার দুধারে বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও দুএকটি খেজুর ও তাল জাতীয় উদ্ভিদ, সাঁইবাবলা—সেখানে আমার মন পড়ে থাকত। ‘উত্তরে অজয় নদের সুবিস্তীর্ণ বালুকাবিস্তার। কাশগুচ্ছসমাচ্ছন্ন সৈকতভূমি। অদূরে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব নির্মিত পাণ্ডবেশ্বর মহাদেবের পাঁচটি মন্দির।’ গ্রামের প্রায় চারদিকে দুর্গের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে কোয়ালিয়ারি কালিমন্দির, জয়নগর দুর্গামন্দির, লাইকাপুর কালিমন্দির—তার কিছুদূর গেলে অজয় ও দামোদর নদের সুপ্রবাহিত ধারা—একে অপরের সাথে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। ঢেউ খেলানো লালমাটির গভীরে জমা আছে মহাকালের কান্নার অঙ্গার। এখানকার জমি রুক্ষ হলেও এক সময়ে গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। এর গভীর থেকে মাটি খুড়ে কয়লা বের করার কারণে বনাঞ্চল প্রায় সাফ হয়ে গেছে।
মক্তবের পরিবেশে কেমন যেন বিষণ্নতা, ছাত্রদের চলাচলের মধ্যে দরিদ্রতার স্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যেত। কিছুদিন আগে বাবা মারা গেছেন, আগেই তার সব জমিজমা খুইয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। হঠাৎ করেই আমাদের পরিবারে নেই নেই শব্দটির আধিক্য দেখা যেতে লাগল। পিতার আমলে এতদিন ছিল জাতীয় বিপর্যয়ের বিষণ্নতা, আর এখন প্রবল দারিদ্র্যের মুখে পুরো পরিবারের দিশাহার হওয়ার পালা। তখন নিয়মিত খাবার সংস্থান হওয়াই আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। আশেপাশের অন্যদের অবস্থাই যে খুব ভালো এমন নয়। মায়ের বাবার বাড়ির অবস্থা ভালো থাকলেও তার ব্যক্তিত্ব তার বাপের বাড়ির আত্মীয়দের কাছে হাত পাততে বাধা দিল। আমার মধ্যে তখন থেকে রোজগার করার প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠল, আমি বুঝতে পেরেছিলাম এখন থেকে রোজগার না করলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা পরিবারের সঙ্গে তিনবেলা আহার করাই কঠিন হয়ে পড়বে।
এ বয়সে রোজগার করা খুব সহজ ছিল না। লালমাটির রুক্ষ জমিগুলোতে বছরের সব মৌসুমে চাষ করা যেত না। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে ধান ছাড়াও তরমুজ, বাঙ্গি, শশা, কুমড়া, মিস্টি আলুসহ অনেক ধরনের ফসল ফলত। জমিতে জলসেচ দেয়া খুব কঠিন ছিল। পীর পুরুরে প্রায় সারা বছরই পানি থাকত, পাতকুয়া বালতি কিংবা হাতে তৈরি সেচযন্ত্র দিয়ে চাষ খুব বেশি করা যেত না। আমার বয়সী ছেলে অথবা বাড়ির মেয়েরা মূলত সেচের মতো কাজ করত। রান্নার কাঠ কুড়াত, অনেকেই অজয় নদীর কাছাকাছি গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনত, অজয় নদীতে মাছ ধরত, বিড়ি বিক্রি করত, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাল বয়ে নিয়ে যেত, মাঠে মহিষ চড়াত। সবচেয়ে বেশি করত রানীগঞ্জ কয়লাখনির আশেপাশে থেকে কয়লা চুরি, কয়লা কুড়িয়ে বিক্রি করত, কেউ কেউ রান্নার কাজেও ব্যবহার করত।
মক্তব ছুটির সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাড়ি ছেড়ে অনেক দূর চলে যেতাম, অনেকদিন অজয় নদের পাড়ে গিয়ে শুয়ে থাকতাম, বিশাল বালিয়াড়ি পেরিয়ে স্বচ্ছ জল বয়ে যেত, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে অনেক সময়ে নদীর পাড় থেকে শুকনো বালি সরিয়ে ভিজা বালুর উপরে শুয়ে থাকতাম, সঙ্গে কোনো বন্ধু থাকত, অধিকাংশ সময়ে আমি একাই যেতাম। সুষাভ বসু ও দীলিপের কাছে শুনেছি তারাও নাকি অনেকদিন বরাকের বালিতে শুয়ে থাকত, হয়তো এদিকে আমি অন্যদিকে ওরা—একই সময়ে যেহেতু আমরা বড় হয়ে উঠেছি, হয়তো তখন এই ছিল চিন্তাশীল তারুণ্যের নির্মল নির্জনবাস। যেখান থেকে আমাদের জন্য মধ্যে জন্ম হয়েছিল—দেশের প্রতি মায়া। আমরা প্রায়ই ভাবতাম—এই যে আমাদের দেশ, এত সুন্দর যার রূপ, দিগন্তজোড়া আকাশ, নদীর কুলকুল ধ্বনি, পাখির স্বাধীন ডানা মেলা—অথচ দেশটি সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে শাদা চামড়ার মানুষ এসে শকুনির মতো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। আমরা কী অসহায় তার সন্তান, মায়ের অপমান, তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অপমান; এসব ভাবতাম, আমার চোখের কোণ দুটি ভিজে উঠত, আর অন্তরে জ্বলে উঠত বিদ্রোহের আগুন।
বড়দের কাছে গল্প শুনেছি, ইংরেজ আসার আগে এদেশের মানুষের এতটা কষ্ট ছিল না। তখনকার প্রতিটি গ্রামই ছিল নাকি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, প্রয়োজনীয় সকল পণ্য উৎপাদিত হতো এখানে। প্রয়োজনীয় কৃষিকর্ম ছাড়াও তৈজসপত্র তৈরি, লোহা ও কাঁসাশিল্প, মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি, সেকরা করত রুপো ও সোনার গয়না, আর তাঁতিদের পোশাক ছিল ইংল্যান্ডের কলের তৈরি পোশাকের চেয়ে ভালো। নৌকা ও ইঞ্জিনবিহীন জাহাজ, মাছধরা, সমুদ্রপাড়ে লবণ তৈরি করা, ঘানিতে তেল বানানো—প্রতিটি গ্রামের ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই চুরুলিয়া গ্রামও একদিন অস্ত্র তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে অধিকাংশ শিল্পের দখল নেয়। তারা ইংল্যান্ড থেকে কাপড় আমদানি করার জন্য এদেশের শিল্প-কারখানাকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত ও ধ্বংস করে, মসলিন শিল্পীদের ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেয়, দেশীয় পণ্যের উপরে অস্বাভাবিক হারে ট্যাক্স আরোপ করে, নিজেদের পণ্য ডাম্প করে খুব অল্পদিনের মধ্যে এ দেশকে একটি আমদানি নির্ভর দেশে পরিণত করে। বাংলার সমৃদ্ধ গ্রাম-গঞ্জ অল্পদিনে শ্মশানে পরিণত হয়।
তবে টিকে থাকার লড়াই অন্য উপায়ও ছিল। অনেক সময় বন্ধুরা মিলে কারো বাড়ির আম, কারো খেতের আলু, শশা, তরমুজ হামেশা টান দিতাম আমরা, তার মধ্যে চুরি বা পাপবোধের ব্যাপার ছিল না। এটাই ছিল এলাকার রীতি। এই অঞ্চলে এ ধরনের চুরিকে তখন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হতো না। কেবল মুসলমানপাড়া নয়, বেনেপাড়া, বাগ্দিপাড়ার ছলেমেয়েরাও এসব চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকত; বিশেষ করে প্রকাশ্যে সরকারি অধিকৃত সম্পত্তি—কয়লা, বন, কারখানার যন্ত্রাংশ এগুলো নেয়া অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হতো। কষ্ট থাকলেও আনন্দের কমতি ছিল না, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে শারীরিক কসরত করে, গান গেয়ে, দৌড় প্রতিযোগিতায় সময় কেটে যেত।
এতকিছুর মাঝেও কেমন যেন এক চিন্তাশীলতা আমার মধ্যে ভর করছিল, বিস্তীর্ণ মাঠ, নদীর বয়ে চলা, দিগন্ত আকাশ এক অজানা গন্তব্যে শৈশব থেকেই আমায় আহ্বান করতে থাকে। বাড়িতে বা মক্তব্যে পড়া কবি-সাহিত্যিকের জীবন আমায় আকৃষ্ট করতে থাকে। কবিদের সম্বন্ধে আমার একটি ধারণা হয়েছিল, তাদের ভাবতাম বিবাগী, বাউন্ডুলে, সন্ন্যাসী, দরবেশ—পথে পথে হেঁটে হেঁটে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে চলে যাওয়া, কখনো রাজদরবারে, কখনো গরিব দুখীর সহায়ক হয়ে, কখনো ঘাটের ধারে স্নানরত সুন্দরীর দেহসৌষ্ঠবের কাছে; তারপর ব্যর্থতা, তারপর প্রতিবাদ এক বিরহ রোমান্টিকতা আমার মধ্যে বাসা বাঁধছিল। গ্রামের দক্ষিণে দামোদর নদী উপত্যকা মাইথন। সেখানকার কল্যাণ্যেশ্বরী মন্দির হলো মায়ের স্থান—মায়ের থান থেকে যার নাম হয়েছে মাইথন। দামোদর নদীর সঙ্গে আমার শৈশবেও বিদ্যাসাগরের নামটি জড়িয়ে গিয়েছিল, বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ গ্রাম আমার জন্মভূমি থেকে খুব দূর নয় । এই গল্প তখনই মুখে মুখে ফিরত—বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির প্রমাণ হিসাবে। বিক্ষুদ্ধ ঝড়বৃষ্টির রাতে তিনি মায়ের ডাকে প্রমত্ত দামোদর পার হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরও ছিলেন দামোদরের মতো একরোখা—এমনকি তাঁর শেষ জীবনও কেটেছিল আমার জন্মস্থানের সন্নিকটে সাঁওতাল পাড়ায়। বিদ্যাসাগরের দামোদরের গল্প সত্য না হলে, ঝড়বৃষ্টির রাতে দামোদর পার না হলে এতদূর গেলেন কী করে! এই নদের নাম দামোদর, কারণ দুরন্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মা যশোদা তার উদরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন, যার উদরে দাম—তার নাম শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ; দাম মানে দড়ি, মাঝে মাঝে দামোদর এতটাই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যেত, বন্যার প্রবল তোড়ে মাঝে মাঝে রাজধানী কোলকাতা থেকে এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, বিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। গ্রামের পুব দিকে বিশাল পলাশডাঙ্গা প্রান্তরের পাশে শাল-তাল-তমাল আর হরিতকী বন। তখন থেকে আমার ললাটে লেখা হয়ে গিয়েছিল কবিতার টীকা। তাই যেখানে গান, যেখানে সুর, কবি যাত্রা লেটো ঝুমুর সেখানেই আমার মন যেতে চায় ছুটে।
যে দেশ পর-দেশিদের দখলে তার সন্তানরা কিভাবে বেঁচে থাকে।
পিতার মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমার জীবনের গভীর কন্দরে আরো একটি নতুন ব্যথার ক্ষত চিরদিনের জন্য অক্ষয় হয়ে গেল। গ্রামের মুরুব্বিরা বলতে লাগত, তরুণ যুবারা বলতে লাগল, অন্দরের নারীরাও বলতে লাগল, কোলকাতা থেকে কথাটি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল, তার প্রবল ঢেউ আমাদের চুরুলিয়ায় গ্রামে এসেও বিষণ্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল—ক্ষুদিরাম নামের এক তরুণের ফাঁসি হচ্ছে। এই নব-তরুণের ফাঁসির হুকুম জাতীয় বেদনা হয়ে সারা দেশে আছড়ে পড়ল, তার প্রবল আঘাত কোলকাতা থেকে বহুদূর চুরুলিয়া নামক গ্রামকেও আছন্ন করে ফেলল। সেই ব্যথা এই গ্রামের অসংখ্য কিশোর তরুণের সাথে নয়/দশ বছরের বালকের প্রাণেও ব্যথা ও বোবা প্রতিবাদের ঝড় উঠল। বিশেষ করে যখন গ্রামের রাস্তা দিয়ে বৈষ্ণব বাউলগণ একতারা হাতে—‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ গান গাইতে গাইতে চলে যেত—তখন এই বালকের হৃদয়খানি ‘দলিয়া-মথিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিত।’ দেশের জন্য এমন করে কেউ প্রাণ দিয়েছে এমন কথা যদিও আমি শৈশব থেকেই আমার পিতা-পিতৃব্যদের মুখে শুনেছি, কিন্তু এমন করে কারো জন্য ব্যথা অনুভব করি নি। কতবার নিজে নিজে ফাঁসির মঞ্চ সাজিয়ে গলায় দড়ি লাগিয়ে দেখতে চেয়েছি—ক্ষুদিরামের কষ্ট অনুভব করতে চেয়েছি। ফাঁসুড়েকে জিজ্ঞাসা করেছি মনে মনে—কাকা বলতে পার নাকি ফাঁসির দড়িতে কেন মোম দেয়া হয়! আমি তো সময় নিয়ে আরো কষ্ট সইয়ে দেশ মায়ের জন্য মরতে চেয়েছি—যে দেশ পর-দেশিদের দখলে তার সন্তানরা কিভাবে বেঁচে থাকে।
শের আলী আফ্রিদির গল্প আমাদের পরিবারে চালু ছিল। তিনি একমাত্র ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড মেয়োকে খুন করেছিলেন। শের আলী যিনি ব্রিটিশের পক্ষের এক গাদ্দারকে হত্যার দায়ে আন্দামানে যাবজ্জীবন নির্বাসন ভোগ করছিলেন, নির্বাসিত বন্দি অবস্থায় তিনি বড়লাটের অসংখ্য দেহরক্ষীর চোখ এড়িয়ে হ্যারিয়েট দ্বীপের সানসেট পয়েন্টে অতর্কিত ছুরিকাঘাতে তাঁকে হত্যা করেন। শের আলী মনে করতেন স্বয়ং স্রষ্টা তাকে এই কাজে নির্দেশ দিয়েছেন—যারা তোমার দেশ দখল করেছে, যারা তোমার দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের ভাগিয়ে দাও। তারা তো তোমাদের হত্যা করেই তোমাদের কাছে থেকে তোমাদের দেশমাতাকে কেড়ে নিয়েছে, তারা তো হত্যার মাধ্যমে তোমাদের উপর শাসন শোষণ জারি রেখেছে; হত্যা ছাড়া আর কোন পথ অবশিষ্ট আছে তোমাদের পুনঃগৌরব ফিরিয়ে আনতে। মহা-বিদ্রোহের পরে মেয়ো হত্যাকাণ্ড এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি একই দিনে দুজন সাহেবকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও অন্যজন বড়লাট। এই হত্যার জন্য শেল আলী সারাদিন অপেক্ষা করে থাকেন, সুযোগ আসে সন্ধ্যের দিকে। এই ঘটনার প্রায় তিন যুগ আগে বিক্ষুদ্ধ দেশমাতার সন্তানকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তবে তার মৃত্যুদণ্ড আমার মধ্যে তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি, তার কারণ হতে পারে তার ঘটনাটি ছিল আমার জন্মের প্রায় তিন দশক আগে, তাছাড়া তিনি বাঙালি নন, পাঠান। কিন্তু ক্ষুদিরামে ব্যর্থ প্রচেষ্টা যেন তাকে আরো আপন করে নিতে সহজ হয়। যখন গানের মধ্যে বলা হতো—‘বড়লাটকে মারতে গিয়ে/ মারলাম আরেক ইংল্যান্ডবাসী।’ ক্ষুদিরামের মৃত্যু আমাকে এতই আলোড়িত করেছিল তার বেশ কয়েক বছর পর এই ঘটনাকে স্মরণ করে আমি একটি নিবদ্ধ লিখেছিলাম—
ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময়ের একটি গানে আছে, ক্ষুদিরাম বলছে—
‘আঠার মাসের পরে
জনম নেব মাসীর ঘরে, মা গো,
চিনতে যদি না পার মা
দেখবে গলায় ফাঁসি’
সেই হারা-ক্রন্দনের আশ্বাস-গান শুনে আজও অতি বড় পাষাণী মেয়েরও চোখে জল আসে, গা শিউরে ওঠে। আমাদের মতো কাপালিকেরও রক্ত-আঁখি আঁখির সলিলে টলমল ক’রে ওঠে। কিন্তু বলতে পার কি দেশের জননীরা, আমাদের সেই হারা-ক্ষুদিরাম তোমাদের কার ঘরে এসেছে? তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন ছেলের কণ্ঠের পানে তাকাও, দেখবে তাদের প্রত্যেকের গলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসির নীল দাগ। ক্ষুদিরাম ছিল মাতৃহারা। সে কোন মাকে ডেকে আবার আসবে ব’লে আশ্বাস দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে, তা যদি বুঝত বাঙলার মা’রা, তা হ’লে তোমাদের প্রত্যেকটি ছেলে আজ ক্ষুদিরাম হ’ত। ক্ষুদিরাম ছেলেবেলায় মা হারিয়ে পেয়েছিল সারা দেশের মায়েদের। মায়ের ক্ষুধা তার মেটে নি, তোমাদের সকলকে মা ব’লে ডেকেও সে তৃপ্ত হয় নি, তাই আবার আসব ব’লে কেঁদে গেছে। এবার অভিমানী ছেলে মায়ের ঘরে আসবে না, মাসির ঘরে আসবে। কিন্তু অভিমানী হ’লে কী হয়, ও ছিল বোকা ছেলে, তাই বুঝতে পারে নি যে, মাসির ঘর ব’লে অভিমান ক’রে যার ঘরে আসতে চেয়েছে, সেও যে মায়েরই ঘর।
মায়ের সাড়া পায় নাই, মা’রা তাকে কোলে নেয় নি, তাই অভিমানে সে আত্মবলিদান দিয়ে আত্মনির্যাতন ক’রে মায়েদের অনাদরের প্রতিশোধ নিয়েছে। যাবার বেলায় দস্যি ছেলে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে গেল না। হায় হতভাগা ছেলে! কার জন্যে সে কাঁদবে? যার জন্যে কাঁদবার কেউ নেই, তার চোখের জল যে লজ্জা, তা’র কাঁদাটাও যে অপমান। দস্যি ছেলে সব চোখের জলকে কণ্ঠের নিচে ঠেলে রাখলে। ফাঁসি প’রে নীলকণ্ঠ হবার আগেই ব্যথায় নীলকণ্ঠ হয়ে গেল। প্রাণের তিক্ত ক্রন্দনের জ্বালা তার কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু কিশোর ঠোঁটের অপূর্ব হাসি। ফাঁসি হ’তে আর দু’চার মিনিট বাকি, তখনও সে তার নিজের ফাঁসির রশির সমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত যে, ফাঁসির রজ্জুতে মোম দেওয়া হয় কেন! তোমরা কি ভাবছ মা যে, কী সাংঘাতিক ছেলে বাপু! কিন্তু ছেলে যতই সাংঘাতিক হোক, সত্যি করে বল দেখি, ওই মাতৃহারা তোমাদেরই মুক্তির জন্য ফাঁসিতে যাওয়ার কথা শোনার পরেও কি তোমরা নিজেদের দুলালদের বুকে ক’রে শুয়ে থাকতে যন্ত্রণা পাও না? ওই মাতৃহারার মরা লাশ কি তোমাদের মা ও ছেলের মধ্যে এসে শুয়ে একটা ব্যবধানের পীড়া দেয় না? নিজের ছেলেকে যখন আদর করে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় যাবতীয় সামগ্রী খাওয়াও, নিবিড় স্নেহে বুকে চেপে ধরে শুয়ে ঘুম পাড়াও, একটু অসুখ করলে তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা খোঁড় তখন কি এই মাতৃহীন ক্ষুদিরামের কথা, তারই মতো আরো সব লক্ষ্মী-ছাড়া মাতৃহারাদের কথা মনে হয়ে তোমাদের বুকে কাঁটার মতো বেঁধে না? তোমাদের এত স্নেহ এত মায়া কি অনুশোচনায়, লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠে না? বল মা, উত্তর দাও! আজ ওই ক্ষুদিরামের মতো শত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে এসে তোমাদেকে তোমাদের মাতৃহৃদয়ের নামে জিজ্ঞাসা করছে, উত্তর দাও! জানি, উত্তর দিতে পারবে না, মুখে কথা ফুটবে না। তুমি বলতে যাবে, কিন্তু অমনি তোমার মনের মা তোমার মুখ টিপে ধরবে!
মানুষের মন আর আত্মা এমনই বালাই যে, পরের দুঃখ দেখে তার নিজের ভোগ বিস্বাদ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মা-দের। মাতৃহারা এক পাশে দাঁড়িয়ে জল-ছলছল চোখে যদি চায়, তা’হলে তোমার হাত উঠবে না তোমার ছেলের মুখে কিছু তুলে দিতে, আপনি শিথিল হয়ে যাবে। এটাও সওয়া যায়। কিন্তু যদি কোনো মাতৃহারা বিদ্রোহ ক’রে কারুর কাছে কিছু না চায়, মাথা উঁচু ক’রে কোনো মায়ের ঘরের পানে না তাকিয়ে তার রুক্ষ কেশ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তির রুদ্রকেতন উড়িয়ে চলে যায়, ডাকলেও ঘরের পানে তাকায় না, মায়ের ডাকে চোখ ছলছল না ক’রে উল্টো আত্মনির্যাতন করে তোমাদের চোখের সামনে, তা’হলে মায়ের মন কেমন ক’রে ওঠে বল দেখি? হে আমার দেশের জননীরা! তোমাদের কাছে এসেছে তেমনি বিদ্রোহী লক্ষ্মীছাড়া মাতৃহারার দল, তাদের হারানো ক্ষুদিরামকে খুঁজে নিতে। ভয় করো না, বিদ্রূপ করো না এদের মা, এরা ভিখারি ছেলে নয়। আমরা তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে আসি নি, আসবও না। আমরা এসেছি আমাদের দাবি নিয়ে, আমাদের হারানো ক্ষুদিরামকে ফিরে নিতে। সে যে আমাদের মাতৃহারার দলের, সে মায়ের দলের নয়। ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে। তোমরা চিনতে পারছ না, তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে, তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের, আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের। ওরা মায়েদের নয়, ওরা ঘরের নয়, ওরা বনের। ওরা হাসির নয়, ফাঁসির। ওই যে কণ্ঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরছ, ওই কণ্ঠে ফাঁসির নীল দাগ লুকানো আছে। ওরা তোমার নয়, আমার নয়, ওরা দেশের, ওরা বলিদানের, ওরা পূজার।
এক ক্ষুদিরামের সঙ্গে অসংখ্য গান্ধীর তুলনা দিতে আমি রাজি ছিলাম না।
কোথায় প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু আঠার বছর যে কেটে গেল ভাই, সাড়া দাও সাড়া দাও আবার, যেমন যুগে যুগে সাড়া দিয়েছ ওই ফাঁসি-মণ্ডপের রক্ত-মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তোমার সাথে আমাদের বারবার দেখাশোনা ওই ফাঁসি-পরা হাসি-মুখে! আর একবার সাড়া দিয়েছিলে তুমি আয়ারল্যান্ডে রবাট অ্যামেট নামে। সেদিনও এমনই তরুণ বয়সে তুমি ফাঁসির কৃষ্ণ-আলিঙ্গন, খড়গের সুনীল চুম্বন পেয়েছিলে। হারা প্রিয়া ‘সারা’র আলিঙ্গনপরশ তোমার জন্য নয়, কমলার প্রসাদ তোমার জন্য নয়, তোমার প্রিয়ার তুমি এমনই বারে বারে পাবে আবার বারে বারে হারাবে, তোমার প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়তম ওই ফাঁসির রশি। কোথায় কোন মাতৃ-বক্ষে কোন “সারা”র কোন কমলার কুঞ্জে আপন ভুলেছ, হে ক্ষুদিরামের জাগ্রত আত্মা। সাড়া দাও! সাড়া দাও! এস আবার ফাঁসিমঞ্চে, আর একবার নতুন ক’রে আমাদের সেই চির-নূতন চির-পুরাতন গান ধরি—
‘আঠার মাসের পরে,
জনম নেব মাসীর ঘরে, মা গো
চিনতে যদি না পার মা,
দেখবে গলা ফাঁসি!’
এই ছিল সেদিন আমার ক্ষুদিরামের চেতনা, এক ক্ষুদিরামের সঙ্গে অসংখ্য গান্ধীর তুলনা দিতে আমি রাজি ছিলাম না, তেমন এক শের আলীর সঙ্গে অসংখ্য জিন্নাহর তুলনা হতে পারে না। আমার বন্ধু সুভাষ ইংরেজ বিদায়ের প্রাক্কালে তাদের মতো শরীর দিয়ে প্রমাণ করল—মায়ের সন্তানদের কাছে মাকে অপমানকারীদের কাছে নতজানু আপসকামিতার কিছু নেই। তারাই ছিলেন আমাদের সময়ের ভারতীয় ক্রাইস্ট—যাদের আত্মত্যাগের মহিমার উপরে আমরা কিছুটা গর্ব নিয়ে বাঁচতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের কষ্ট আরো বেড়ে গিয়েছিল—যখন শুনেছিলাম গান্ধীজী ক্ষুদিরামের পক্ষে না দাঁড়িয়ে তাঁকে সন্ত্রাসী হিসাবে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। স্বদেশি শাসনে হয়তো তাই, বিদেশি শাসনে গান্ধীর অহিংসা কেবল বৃহত্তর হত্যাকারীদের পক্ষে যায়, যারা অগণিত ভূমিপুত্রদের নিহত করে তাদের মা ও পুত্রবধূদের শয্যায় শুয়ে শান্তির কথা বলে। তখন থেকে আমার মনে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও অসংযত বাণী জমাটবদ্ধ ছিল তা-ই পরবর্তী কবিজীবনে গিরিপর্বতের খাদ বেয়ে প্রবল বেগে নিচে নেমে এসেছে। এই স্মৃতির দুঃসহ বেদনা থেকে একদিন আমি লিখেছিলাম—
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি-নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।
ঢাল তরবার, আন মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দেখা।