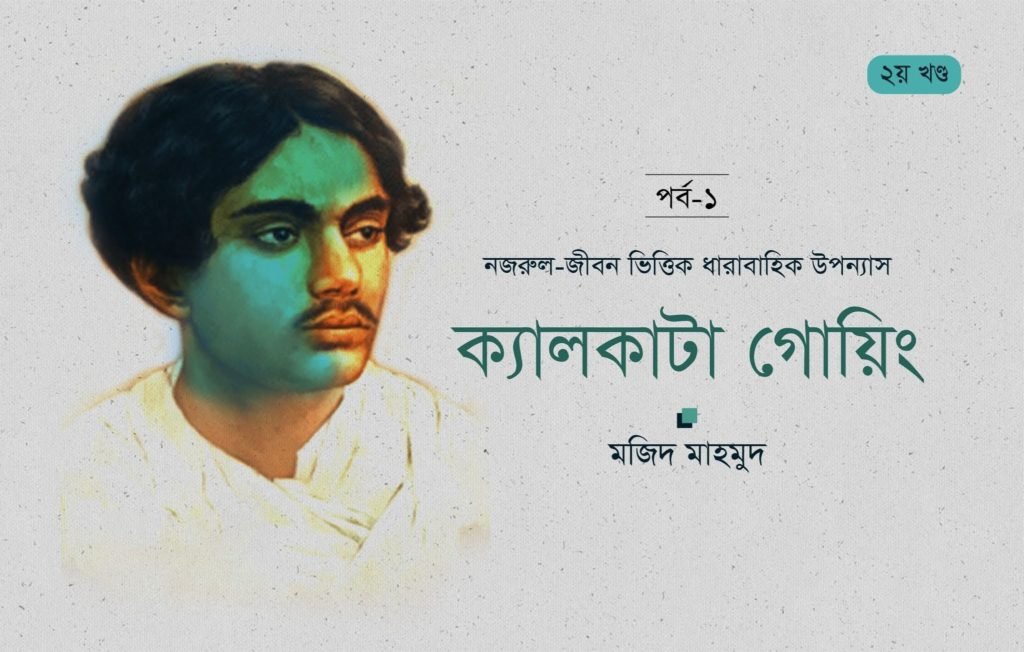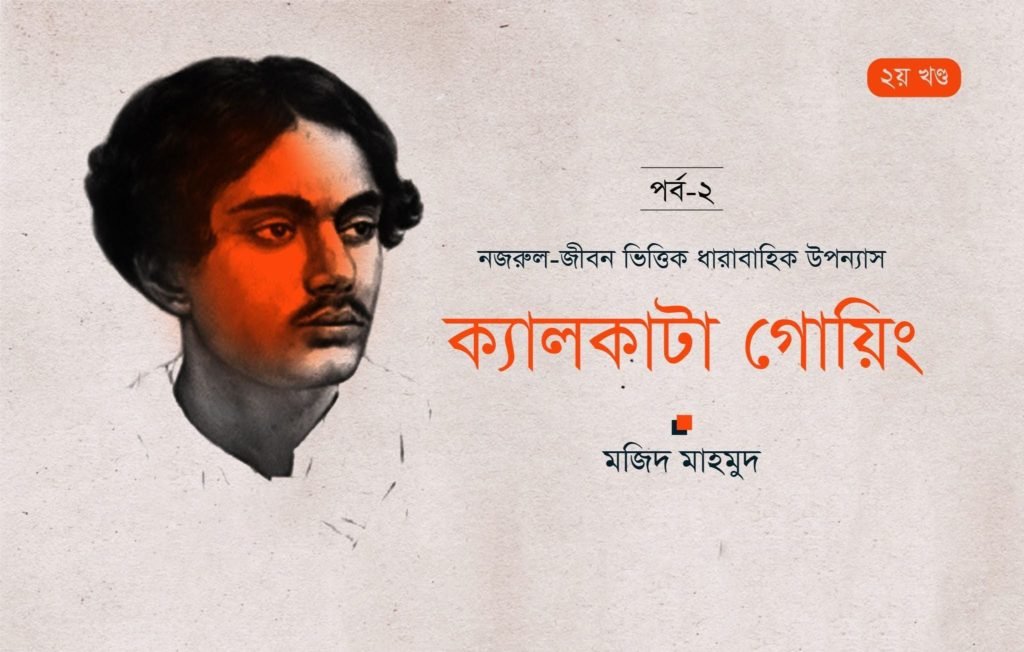পর্ব-৬
১৯৪৬ সাল। আমার শাশুড়ি গিরিবালা দেবী ‘কোলকাতা গ্রেট কিলিং’ বা ‘দীর্ঘ ছুরি সপ্তাহ’র মধ্যে চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বলা চলে—এর মধ্য দিয়ে আমার সংসার জীবনের চূড়ান্ত নাটিকার যবনিকাপাত ঘটল। আমার জীবনীকাররা গিরিবালা দেবীর ভূমিকাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে অঙ্কন করেন নি। সংসারে নারীর যে নিভৃত ত্যাগ—গিরিবালা দেবী আমার সংসারে সেই না-দেখা জায়গাটি অধিকার করেছিল।
সংসার বলতে যদি একটি বাড়ি বোঝায়—যাকে কেন্দ্র করে অন্তত একজন মানুষ আশ্রয় নিয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার তাড়না বোধ করে—তাহলে—সেটি গিরিবালা দেবী। সংসারে বিয়ে নামক বস্তুটি কেবল একটি নারীর সঙ্গে একটি পুরুষের নয়। একটি কনের সঙ্গে একটি বরের নয়। একটি ঘরের সঙ্গে একটি ঘরেরও। সেদিক দিয়ে আমার বিয়ে কেবল প্রমীলা দেবীর সঙ্গে সম্পন্ন হয় নি। তার মা গিরিবালা দেবীকে ছাড়া আমার সংসার-জীবন কল্পনা করা যায় না। প্রমীলা ও গিরিবালা মিলেই মূলত আমার সংসার। গিরিবালা ছাড়া আমার ঘরবাঁধা সহজ ছিল না। সে কথা ভেবেই খাঁ সাহেব আমায় ঘর-জামাই রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল হয়তো। আপাত দৃষ্টিতে খারাপ শোনালেও তখন নার্গিসকে নিয়ে আমার কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না।
দুলির সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয় তখন সে-ও নিতান্ত বালিকা। মাত্র ষোল বছরের কিশোরী—শাশুড়ি নেই, ননদী নেই—জা-ভাজ নেই—পাড়া-পড়শি নেই। একটা পুরুষের সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করা মানেই বিয়ে নয়। সংসারে অন্যের বিছানাও তৈরি করতে হয়। বিহঙ্গ যেমন আকাশের পথে উড়ে এসে বৃক্ষের শাখায় খড়কুটো জমা করতে থাকে—তার উদ্দেশ্য—মানুষের উদ্দেশ্যের মধ্যে তফাত নেই। সংসারে কেউ একজন আসবে, বাতাসে তার ইঙ্গিত এসে পৌঁছালে মানুষ বিয়ে করে। এক আজানা ভেলায় যারা ভাসিয়ে দিয়েছিল—একটি বায়ুযানের ভেতর—তারা এখানে আমাদের খেয়াতরী হিসাবে হয়তো ব্যবহার করেছে। তবু মানুষ ও পাখির মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বর পাখিদের অন্তরীক্ষে ছেড়ে দেয়ার আগে, শূন্যে ভেসে থাকার বায়ুযান দিয়েছেন, শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার জন্য পালকের চাদর দিয়েছেন, সাঁতার কাটার জন্য বৈঠা দিয়েছেন, সব শেষে শিখিয়েছেন—বাসা বানানোর কৌশল। মানুষকে সে-সব দেন নি। বাচ্চাদের পৃথিবীতে আনতে হলে অন্তত একজন সঙ্গী প্রয়োজন। এই দায়িত্ব ঈশ্বর কারো উপর একা ছাড়েন নি। পৃথিবীর পথে ঈশ্বর কাউকে পাঠাতে চাইলে দুজনের কাছে আগে একই বার্তা পাঠিয়ে থাকেন। তাই পৃথিবীতে কেউ কারো একার সন্তান নয়। একজন মানুষও পাওয়া যাবে না—যে তার একক সন্তান দাবি করতে পারে। তাই বলতে হয়—আমাদের সন্তান—নয় আমার সন্তান। পাখি হোক, মাছ হোক, কুমির হোক, বাঘ হোক, ঐরাবত হোক—সবার জন্য একই নিয়ম। সন্তানদের পৃথিবীতে আনা সহজ কাজ নয়। একজনের কাছে থাকে ডিম রাখার থলি, আরেক জনের কাছে থাকে ডিম।
আমাকে মানুষ যতটা অসাম্প্রদায়িক মনে করেছে—আমার এই শাশুড়িমাতাকেও তেমন মনে করা উচিত।
গিরিবালা দেবী—আমার আর দুলির সেই কঠিন কাজ সহজ করে দিয়েছিল। সে মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছিল—আমার কাছে—নাতিপুতির মুখ দেখার জন্য। প্রমীলার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার শাশুড়ির বয়সই বা কত! সেও বিধবা হয়েছিল তার ভরা যৌবনে। হিন্দু বিধবার বিয়ে তখন আইন-সম্মত হলেও বাস্তব-সম্মত ছিল না। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের গিরিবালা দেবী তার বারো বছরের কন্যাকে সেই থেকে পক্ষতলে আগলে রেখেছিলেন। আমার সঙ্গে দুলির বিয়ে দেয়া তার একক প্রচেষ্টা—সম্ভবত তার মধ্যেও একটি পৃথক সংসারের স্বপ্ন ছিল। গিরিবালা দেবী কেবল দুলি ও আমায় সংসার দেয় নি—সে তার নিজের জন্যেও সংসার রচনা করেছিল। ভিন্ন ধর্মে অসম বর্ণে বিয়ে ১৯২৪ সালের ভারতবর্ষের কোলকাতায় কোনো সহজ ঘটনা ছিল না। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে স্বয়ং বিরজাসুন্দরী দেবী—যাকে আমি মা বলে ডেকেছি—তিনি ও তার পরিবার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নেয়। অনেকে মনে করে, ইন্দরকুমার পরিবারের বুঝি গোপন ইচ্ছে ছিল—পিতৃহীন দুলিকে আমার হাতে গছিয়ে দেয়া। এই সুপ্ত ইচ্ছের প্রকাশ—খান বাড়ির বিয়ে ভেঙে যাওয়া।
বিরজাসুন্দরীর পরিবার যে কেবল দুলি ও আমার বিয়েতে বিরোধিতা করেছিল, তা-ই নয়—তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গিরিবাল দেবী ও তার কন্যার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্কও ছিন্ন করেছিল। দুলির সঙ্গে আমার বিয়ে সম্ভব হয়েছিল, একমাত্র গিরিবালা দেবীর কল্যাণে। সেদিক দিয়ে তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অনেক। মাসান্তে অনিয়মিত কিছু অর্থ তার হাতে তুলে দেয়া ছাড়া সংসারে কোন দায়িত্বটি আমি ঠিকমতো পালন করেছি! যখন দেদার আয় করেছি—বইয়ের রয়ালিটি থেকে, গানের রেকর্ড থেকে—তখন ইচ্ছে মতো উড়িয়েছি, যখন আয় কমেছে তখন দায় নিতে হয়েছে গিরিবালা দেবীকে।
প্রায় সকলে এই ভুলটা করে থাকে—আমি কুমিল্লা’র মেয়ে দোলনাকে বিয়ে করেছি। এই ভুলের কারণ হয়তো আলী আকবর খাঁর সঙ্গে কুমিল্লা গমন। নানা নাটক শেষে তখনকার কুমিল্লাবাসী আশালতা ওরফে দুলির পাণি গ্রহণ। সে-বিয়েও আমার কুমিল্লায় সম্পন্ন হয় নি। আমার শ্বশুর বসন্তরঞ্জন সেনগুপ্ত মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রামের বাসিন্দা। আমার শাশুড়িরও জন্ম ওই একই গ্রামে। তেওতা জমিদার বাড়ির পাশে এখনো সেনগুপ্ত পরিবারের বাড়িটির ভগ্নাবশেষ অক্ষত রয়েছে। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি। আমার বিয়ের মাত্র দুবছর আগে কোলকাতা যাওয়ার পথে দুলির খুল্লতাত ভাই বীরেন্দ্রকুমারের সাথে তেওতা গ্রামে গিয়েছিলাম। আমি প্রথমবার কুমিল্লা যাওয়ার মাত্র বছর দুয়েক আগে আমার শাশুড়ি দুলিকে নিয়ে দেবর ইন্দরকুমারের সংসারে বসবাস করতে শুরু করেছিল। তার বছর দুয়েক পরে আমার সঙ্গে। কুমিল্লায় তাদের বসবাস ছিল খুব সাময়িক। ত্রিপুরা এস্টেটে আমার শ্বশুর ও তার ছোট ভাই ইন্দরকুমার আগে থেকেই যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই তাদের কুমিল্লা আসা। দুলির সঙ্গে আমার বিয়ের আগেও গিরিবালা আমায় একইভাবে আশ্রয় দিয়েছেন। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ লেখার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশ যখন আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে তখনো আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম বিহারের সমস্তিপুরে মাতৃরূপী গিরিবালা দেবীর কাছে। তিনি তখন দুলিকে নিয়ে তার ভাইয়ের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমি পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে তাদের নিয়ে কুমিল্লায় ফিরে আসি।
ওই দিনই আনমনে সিলেট রোড ধরে হেঁটে চলেছি। পুলিশ লাইনের কাছাকছি উকিল যোগেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ির সামনে থেকে পুলিশ আমায় গ্রেফতার করে। তারপর কুমিল্লা থেকে আমায় নেয়া হয় কোলকাতয়। সে-সময়ও গিরিবালা দেবী পুত্র-বিচ্ছেদে ব্যথিত হয়েছিলেন।
আমার শ্বশুরের মৃত্যুর আগে তেওতা গ্রামই ছিল দুলির জন্ম ও বেড়ে ওঠা। দুলির শৈশব ও কৈশোরকাল তেওতা গ্রামেই কেটেছিল। সানি ও নিনির মামা বাড়ি বলতে—যমুনার তীরে এককালের বর্ধিষ্ণু তেওতা গ্রামই। ‘ছোট হিটলার’ কবিতায় আমি সে কথা উল্লেখ করেছি—‘মাগো! আমি যুদ্ধে যাবোই নিষেধ কি মা আর মানি/ রাত্রিতে রোজ ঘুমের মাঝে ডাকে পোলান্ড-জার্মানি/ ভয় করি না পোলিশদেরে জার্মানির ঐ ভাঁওতাকে/ কাঁপিয়ে দিতে পারি আমার মামা বাড়ি তেওতাকে।’ সানি ও নিনি মজা করে এটি আবৃত্তি করত। দুলির সঙ্গে বিয়ের পরে শ্বশুর-বাড়ির দাবি নিয়ে কুমিল্লায় যাওয়ার অধিকার আমার ছিল না।
দুলির মতো আমিও তার জন্মস্থান তেওতা গ্রামকে ভালোবেসেছিলাম। যমুনার তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা গ্রামটি পৃথিবীর মধ্যে সেরা সৌন্দর্যে ভরপুর। আমার ক্ষমতা থাকলে শাহজাহান বাদশার মতো এই যমুনাপাড়ে দুলির স্মরণে একটি আশালতামহল বানাতাম। একবার বেড়াতে এসে দুলি ও তার সখীদের নিয়ে একটা গান লিখেছিলাম—‘নীলাম্বরী শাড়ি পরি’ নীল যমুনায় কে যায়?/ যেন জলে চলে থল-কমলিনী ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায়ে পায়।’ যদিও গানটি এখন ভুল সুরে গাওয়া হয়। দুলির কথা মানে গিরিবালা দেবীর কথা। আমার শাশুড়ির সব স্মৃতি তেওতাকে ঘিরে। সুযোগ পেলেই আমি তেওতা এসেছি—গিরিবালা দেবীকে খুশি করতে।
মুসলমান জামাই শাশুড়ির কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও তার আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শি আমায় সুনজরে দেখে নি। ১৯৩৮ সালে ফরিদপুর সম্মেলন এসে সুস্থ অবস্থায় শেষবার তেওতায় গিয়েছিলাম। শাশুড়ি অনেক করে বলে দিয়েছিল, তার অনুরোধে দুই দিন দুলিদের বাড়িতেই ছিলাম। পরে রক্ষণশীল হিন্দুদের সমালোচনার ভয়ে মানিকগঞ্জ শহরে তেজেন মিত্রের ওখানে চলে যাই। কোলকাতা থেকে ফরিদপুর অব্দি এতদূর এসে তেওতা না গিয়ে পারি! নদী পার হলেই আমার দুলির নাড়িপোতা মাটি, শাশুড়ি গিরিবালা দেবীর জন্ম—বিয়ে, সন্তান প্রসব ও বিধবা হওয়ার সকল স্মৃতি এখানে। শাশুড়ির কথা বলতে গেলে তেওতাকে বাইরে রাখা সম্ভব নয়।
গিরিবালা দেবী বিধবা ছিলেন, গিরিবালা দেবীর সংসারের স্বপ্ন ছিল, মেয়ে পাত্রস্থ করার দায় ছিল—কিন্তু বিশ শতকের শুরুর দিকে একজন মুসলমানের হাতে মেয়ে তুলে দিয়ে তার কোনোটাই পূরণ হওয়ার ছিল না। প্রেম করে পরধর্মের অসবর্ণ দুলিকে নিয়ে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম—সেটি একান্ত ভিন্ন কথা। প্রেমের টানে যুগ যুগ ধরে মানুষ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছে ভেতরের শক্তি দিয়ে। প্রেমের আহ্বানে ভেঙে পড়ে মানুষের তৈরি বন্ধন সংস্কার ধর্ম। কিন্তু একজন বিধবার পক্ষে সমাজের বাঁধন কাটা এত সহজ ছিল না। নিজের ধর্ম বাঁচিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে—নিজের ধর্মের মানুষের ঘৃণা, অন্যের ধর্মের মানুষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংসারের সাধ পূরণ করা অসম্ভব। তারপরে সেই সংসার যদি আমার মতো বাউণ্ডুলে ভবঘুরে কবির হয়।
অনেকে আমাদের বাসা ভাড়া দিতে চাইত না। কেবল আমি মুসলমান বলে নয়, গিরিবালা একজন হিন্দু বিধবা মুসলমান জামাইয়ের বাড়িতে জল স্পর্শ করে—সেই অপরাধে। আমার সংসারে গিরিবালার ত্যাগ ছোট করে দেখার উপায় নেই। আমি পুরুষ মানুষ বলে, দেশবরেণ্য কবি বলে জাতপাত সংকটের অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পেরেছি, কিন্তু একজন বিধবা কুলবধূর পক্ষে কাজটি সহজ ছিল না। সমাজ নামক ভূদেবগণ সর্বদা তাকে ভ্রুকুটি করেছে।
আমার শাশুড়ি গিরিবালা দেবী ও শ্বশুর বসন্তকুমার সেনগুপ্তের পরিবার কুল-মর্যাদায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। নিজের স্বামী এবং দেবর উভয় মর্যাদাশীল কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পারিবারিক সাংস্কৃতি পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন। নিজে গান গাইতেন। অল্প বিস্তর কবিতা লিখতেন। সহজ কর্তৃত্বশীলতা ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আমি যেমন আমার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান দুলিও তার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান।
আমার বিয়ের মাত্র তের বছরের মাথায় দুলি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল। সানি ও নিনি—তখনো নিতান্ত শিশু। তাকে নতুন করে ধরতে হলো মাতৃত্বের পদ। তার মাত্র বছর তিনেকের মধ্যে আমিও চিরতরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লাম। একদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কন্যা আশালতা, অপরদিকে একমাত্র উপার্জনক্ষম জামাই মানসিক প্রতিবন্ধী—এহেন অবস্থায় সংসারে যাবতীয় দুঃখভোগকারিণী প্রৌঢ় নারীর পক্ষে কী করার থাকে।
আমাকে মানুষ যতটা অসাম্প্রদায়িক মনে করেছে—আমার এই শাশুড়িমাতাকেও তেমন মনে করা উচিত। আমার অসাম্প্রদায়িকতা যদি কাম্য হয়—তহলে গিরিবালা দেবীকে ভুললে চলবে না, কারণ তিনিও এর ভিত রচনায় ভূমিকা রেখেছিলেন। জানি না বিধির অন্য কোনো ইঙ্গিত ছিল কি না—আমি যদি সেনগুপ্ত পরিবারের জামাই না হয়ে খান-মুন্সিবাড়ির জামাই হতাম—তাহলে কি আমার পক্ষে এত উচ্চকৃত গৌরবময় অসাম্প্রদায়িকতার প্রচারক হওয়া সম্ভব ছিল! এই ভারতে দুইটি সম্প্রদায়ের মিলনের বাণী রচনা করাবেন বলেই গিরিবালা দেবীকে আমি মাতৃরূপে পেয়েছিলাম। আমার পরিবার ও সন্তানদের মিশ্র সংস্কৃতিতে বড় করে তুলতে পেরেছিলাম।
আমি সম্বিতহারা হওয়ার পর জসীমউদ্দীনের কাছে তিনি মনঃকষ্ট প্রকাশ করেছিলেন:
গিরিবালা দেবী জসীমকে বলেছিলেন, ‘লোকে নাকি আমার নামে নিন্দা করে বেড়াচ্ছে জসীম। নুরুর নামে যে সব টাকা-পয়সা আসে সে সব আমি নাকি বাক্সবন্দি করে রাখি। আমার ছেলে নাই, আমি নুরুকেই নিজের ছেলে করে নিয়েছি।’
আমার চিকিৎসা ও পরিবারের জন্য যে সাহায্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেখানেও জসীম বাগড়া দিতে চেষ্টা করেছে বলে অনুসন্ধিৎসুদের ধারণা।
এ কথা বলে আমার শাশুড়ি জসীমের হাত ধরে কেঁদেছিল। তারপর ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়—আমার গৃহবন্দি ছোট্ট প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার ঘরে। আমি তখন মলমূত্রের মধ্যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানমগ্ন ছিলাম।
গিরিবালা দেবী বলেছিলেন, ‘এইসব পরিষ্কার করে স্নান করে আমি বিধবা মেয়েছেলে তবে রান্না করতে বসব। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে। রোজ এভাবে তিন চারবার পরিষ্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তারা এই কাজের ভার নিলে আমার দুচোখ যেদিকে যায় চলে যাব।’
সত্যিই যে এত শীঘ্র তিনি সংসার ছেড়ে চলে যাবেন—সেদিন কেউ অনুমান করতে পারে নি।
তবে এই নিন্দার তির জসীমের দিকেও যায়, কিছুটা হায়দারের দিকেও। হায়দার আমার শেষ জীবনে যথেষ্ট সেবাযত্ন করেছিল। কিন্তু ওর মন ছিল, অস্থির দুর্বল। ও আমাকে কেবল মুসলমানের কবি হিসাবে দেখতে পারলে বেশি খুশি হতো। ওর ধারণা গিরিবালা দেবীর কারণেও আমার কিছুটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। যদিও গিরিবালা দেবী ও হায়দারের মধ্যে সদ্ভাব কম ছিল না।
আমার চিকিৎসা এবং পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সজনীকান্ত দাস ও জুলফিকার হায়দার কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক ছিল। কমিটির অন্যান্য সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও গোপাল হালদার।
কমিটিতে মুসলমান সদস্য হিসাবে হুমায়ূন কবির, সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং স্যার আহমেদ ফজলুর রহমানের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে রেডিও, হিজমাস্টার্স ভয়েস, নিউ থিয়েটারের পক্ষ থেকে কেউ ছিল না। অনেকে মনে করে নাসিরুদ্দিন, মওলানা আজাদ—এরাও থাকতে পারত। সজনীকান্তের মধ্যে প্রবল দ্বৈত সত্তা কাজ করত। মানুষের পেছনে লেগে থেকে সে যেমন মজা পেত, আবার বন্ধুদের সুখ-দুঃখে সে-ই সবার আগে ছুটে এসেছে। অনেকে মনে করে, সজনী শনিবারেরর চিঠিতে তার সামর্থ্যের অপচয় করেছে। আমার মনে হয় ঠিক নয়, সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় ওর কৃতিত্ব থাকলেও হাস্যরসাত্মক প্যারোডি রচনায় ওর পত্রিকা একটা সম্পূরক যুগের সূচনা করেছিল। যেখানে কবিগুরুর তীব্র উপস্থিতি, আমার নিজের সাহিত্যের ঘূর্ণাবর্ত, জীবনানন্দ দাশ ছাড়াও তিরিশ দশকের বুদ্ধদেব, সত্যেন্দ্রনাথ, অমিয়, বিষ্ণু, প্রেমেন সবাই সক্রিয়—সেখানে সে একাই ঘটোৎকচের মতো কিম্ভূত জেগে ছিল। আবার তার সঙ্গে যারা যুক্ত হচ্ছে—মোহিতলাল, হেমন্তকুমার, নিরোদচন্দ্র—প্রত্যেকে কেউ কারো চেয়ে কম যায় না।
‘নজরুল সাহায্য কমিটি’র পক্ষ থেকে আমার পরিবারকে প্রতি মাসে দুশো টাকা সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটি টাকা আদায়ে মূলত শ্যামাপ্রসাদকে ব্যবহার করত। তিনি রাজা-মহারাজাদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনতেন। পাঁচ মাস কমিটি আমার পরিবারকে দুশো টাকা করে দিলেও ষষ্ঠ মাস থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়।
সজনীকান্ত জুলফিকার হায়দারকে বলেছিল, ‘তোমাদেরই (মুসলমানদের) খ্যাতনামা একজন কবি এখানে এসে বলেছে—নজরুলের বাড়িতে আগের মতো এখনো সেই আশ্রিত ও আশ্রিতদের সকাল-বিকাল মিঠাই-মণ্ডা, চা সন্দেশ চলে। অথচ আমরা পরের কাছে হাত পেতে চেয়ে নিয়ে টাকা এনে তাঁকে সাহায্য করছি। সে তোমার সম্পর্কেও কিছু বলতে চাচ্ছিল।’
এই সন্দেহভাজন মুসলিম কবির নাম জসীমউদ্দীন—সেটি সবাই অনুমান করে নেয়। কারণ এর পরেও আমার চিকিৎসা ও পরিবারের জন্য যে সাহায্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেখানেও জসীম বাগড়া দিতে চেষ্টা করেছে বলে অনুসন্ধিৎসুদের ধারণা।
সেটি আজহারউদ্দীন খান স্পষ্ট করেই বলেছে—‘মাসে মাসে দুশো টাকা করে সাহায্য করছিল, সেটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম পল্লিকবি জসীমউদ্দীন মিথ্যা অভিযোগ এনে বন্ধ করে দিয়েছিল।’
আজহাউদ্দীন খান আমার উপরে একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন। ওর বাড়ি মেদনিপুর। আমার অসুস্থকালে মাঝে মাঝে দেখতে আসত।
আমার পরিবারকে এতটা গুরুত্ব দেয়া হোক—তা হয়তো তাদের পছন্দ ছিল না। বাঙালির সহজাত পরশ্রীকাতরতাও হতে পারে। হায়দার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল বলে সজনী ইঙ্গিত দেয়ায় সে-ও জসীমের উপরে ক্ষ্যাপা ছিল। আমার পরিবারে হায়দারের এভাবে লেপ্টে থাকা মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে পছন্দ করত না। হায়দার আমার সেবা করত বলে সে কিছু অধিকার ফলাবার চেষ্টা করত। আবার যাদের পক্ষে রাতদিন আমার কাছে পড়ে থাকার সুযোগ ছিল না, তাদের মধ্যে কিছুটা হীনম্মন্যের ভাবও ছিল।
হায়দার ও জসীমের মধ্যে আমার উপস্থিতিতে আমার বাড়িতে একদিন উত্তপ্ত বাক্যালাপ হয়। জসীম আমায় দেখতে এসে বলল, ‘কবি ভাই কেমন আছেন?’ আমার অসুস্থতার এক বছর পার হয়েছে, তখনো পুরোপুরি বাকরুদ্ধ হই নি। মাঝে মাঝে বন্ধুদের চিনতেও পারি। মর্জি হলে দুএকটা কথাও বলি।
বললাম, ‘তুমি কেমন আছ, তোমার ছেলেরা, তোমার বউ, তোমার পিতা বেঁচে আছেন?’
জসীম আমার একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল। তারপর আমার দিকে একটি কলম ও কাগজ মেলে ধরে বলল, ‘কবি ভাই, আমায় একটা কবিতা লিখে দেন তো।’
আমি লিখলাম, ‘আমি দশ হাজার বছর বাঁচিব। আমার ছেলেরা পাঁচ হাজার বছর বাঁচিবে। জসীম তুমি দশ হাজার বছর বাঁচিবে।’
জসীম যখন আমার হস্ত লেখা কাগজখানি তার পকেটে ঢুকাতে যাচ্ছিল, তখন হায়দার বাধা দিয়ে বলে, ‘এ কাগজটুকু আপনি লইবেন না। ওটা আমাকে দিন।’
হায়দারের এসব মাতবরি দৃষ্টিকটু হলেও সত্য যে দুঃসময়ে সেই তো আমার পাশে ছিল। সে জানত, এসব লেখার একদিন মূল্য হবে। কেউ হঠাৎ করে বেড়াতে এসে কবির এসব মূল্যবান দলিল হস্তগত করে চলে যাবে—তা ওর সইত না।
আমি অসুস্থ হলে ঢাকা থেকে মঈনুদ্দীন আমায় দেখতে এসেছিল শ্যামবাজারের বাসায়। আমার শাশুড়ি গিরিবালা দেবী তখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করছিল। মঈনুদ্দীনকে দেখে বিরক্তির ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল।
মঈনুদ্দীন জানতে চাইল, ‘আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন মাসিমা?’
আমার শাশুড়ি বেশ রাগতস্বরে বলেন, ‘রাগ করব না, কতদিন পরে তুমি এলে বলো তো? এর ভেতর আমাদের উপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেল একটু খোঁজও নিলে না।’
শাশুড়ি রেগে বললেন, ‘এই বুঝি তোমার বুদ্ধি? দিনরাত্রি হৈ হুল্লোড় দাপাদাপি। আমরা আমাদের মধ্যে ছিলাম নাকি, যে তোমার খবর নেব।’
‘সে ঠিকই। তবে আপনাদের বাড়ির সামনে এক বিরাট প্রাচীর তুলে রেখেছেন, তা ডিঙিয়ে আমাদের মতো ক্ষুদ্রলোকের প্রবেশও তো অসাধ্য করে রেখেছেন মাসিমা।’
‘প্রাচীর মানে?’
‘প্রাচীর মানে প্রাচীরই। বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে বাধা এড়িয়ে কী করে আসি বলুন তো?’
‘বাধা? কিসের বাধা, তুমি কি এর আগে এসেছিলে এখানে। কেউ কি তোমায় অপমান করেছে?’
‘না, মাসিমা, আমি আসি নি। আসতে সাহসই হয় নি আমার। জুলফিকার হায়দার নামক জনৈক ভদ্দরলোক আনন্দবাজারে এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এই বলে যে, কবি ভয়ানক অসুস্থ। তাঁর সাথে এখন আর কারো দেখা করা চলবে না। যদি নিতান্ত কারো দেখা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।’
আমার শাশুড়ি মঈনুদ্দীনের কথা শুনে আতকে ওঠেন। বলেন, ‘সে কি! এ বিজ্ঞাপন তাকে কে দিতে বলেছে? নুরুকে নিয়ে দেখছি বেশ ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ হয়েছে।’ ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল—বেশি ভিজিটর অ্যালাউ না করা। তাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিষেধ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি অসুস্থ হলে আমার কাছে তেমন কেউ আসতই না।
সজনী শেষমেষ এতটাই বিরক্তি হয়েছিল যে আমার দ্রুত মরণ হলেই যেন তারা দায়মুক্ত হয়।
আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব তখন আমায় ত্যাগ করেছিল। মুসলমান বন্ধুদের চেয়ে হিন্দু বন্ধুরা বরং বেশি খোঁজ খবর নিয়েছে। বাহার, আব্বাস এদের খুব একটা দেখা যায় নি। অসুস্থ হওয়ার বছর দুই পরে প্রাদেশিক সরকার আমার জন্য মাসিক দুই হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করে। এই প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে বাহারের ভূমিকা ছিল।
একেবারেই যারা উপেক্ষা করেছে তারা হলো আমার রেডিও জীবনের সহকর্মী ও গানের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী। এর একটি কারণ হতে পারে, আমার অসুখের কথা শুনে তারা সংকোচের মধ্যে পড়েছিল। এই সব সেলিব্রেটিদের নিয়ে মানুষের মনে এমনিতেই কৌতূহল থাকে। দুঃসময়ে বন্ধু থাকে না—এটাও সত্য।
হায়দার, জসীম, মঈন, গোলাম মোস্তফা—এদের মধ্যে যা-ই হয়ে থাক না কেন, সাহায্য কমিটি এই তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে আমার পারিবারিক সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে! সকল সত্য মেনে নিলেও পারিবারিক চাহিদা তো আর মিথ্যা নয়। যে কবির বাড়িতে কপর্দক না থাকায় না খেয়ে থাকতে হয়। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নিতে হয়। যার বন্ধু সুভাষ, হক বাংলার চিফ মিনিস্টার—যার গান গেয়ে নাকি তারা যুদ্ধে যায়, গোরস্থান শ্মশানে যায়—তার পরিবারের জন্য সর্বসাকুল্যে মাসে দুশো টাকার সাহায্য পাঁচ মাসের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়—বাংলার অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ যার প্রধান!
এখানেই শেষ নয়। সজনীকান্ত আমার খোঁজ-খবর নিতে প্রায়ই বাসায় আসতেন। যে কোনো কারণেই হোক, সজনীকান্তের সঙ্গে আমার শাশুড়ির একদিনের আচরণ বেশ রূঢ় হয়ে যায়। হয়তো তার মেজাজ ঠিক ছিল না। তাছাড়া আমার শাশুড়ি মনে করত নজরুলকে সাহায্য করা জাতির কর্তব্য। সজনীকান্তও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নি। গিরিবালা দেবী এসব জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে একটা চিঠি লেখেন। মুখার্জী বাবু চিঠিটি সজনীকান্তের কাছে পাঠিয়ে দেন।
সজনী শেষমেষ এতটাই বিরক্তি হয়েছিল যে আমার দ্রুত মরণ হলেই যেন তারা দায়মুক্ত হয়।
সজনী ড. বিধান রায়ের কাছে জানতে চায়—‘নজরুল আর কতদিন বাঁচতে পারেন।’
বিধান রায় বলেন, ‘নজরুলের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো আছে। শিগগির মরার আশঙ্কা দেখছি না।’
তারপর সজনীকান্তের কমিটি আর কাজ করে নি। পাঁচ মাসের পরে আমার পরিবারকে কোনো টাকা পয়সা দেয় নি। এখানেই ‘নজরুল সাহায্য কমিটি’র অবসান হয়।
‘নজরুল সাহায্য কমিটি’ গঠনের কিছুদিন পর মুসলমান ছাত্ররা ‘নজরুল এইড ফান্ড’ গঠন করে। এরা মূলত কোলকাতার টেইলর হোস্টেল, বেইকার হোস্টেল ও কারমাইকেল হোস্টেলের ছাত্র। তবে তাদের সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকও যুক্ত ছিল।
তারাও আগের কমিটির মতো আমার পরিবারকে দুশো টাকা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিন মাস তারা দুশো টাকা করে দিয়েও ছিল। তারপর আমার স্ত্রীর স্বাক্ষর জাল করে ওদের সভ্যদের কেউ দুমাসের টাকা আত্মসাৎ করে।
হায়দার ও জসীমউদ্দীনের মধ্যে এ নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা হয়। হায়দার এ সবের জন্য জসীমউদ্দীনকেই দায়ী করে। মনে হয় হায়দার একটু বাড়াবাড়ি করেছে। আমার প্রতি জসীমের ভালোবাসায় ঘাটতি ছিল না।
‘নজরুল এইড ফান্ড’ যে অর্থ আমার নামে সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল, সেটিও আর আমার পরিবারকে দেয়া হয় নি।
বরং কমিটির সভাপতি সৈয়দুর রহমান ‘নজরুল এইড ফান্ড’-এর অবশিষ্ট টাকা সে তার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়—স্কুল মেরামতের জন্য!
এই কমিটিও ধরে নিয়েছিল, আমার পরিবার বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, আমার দুর্ভাগ্য ওদের কাছে সৌভাগ্য হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছিল।
বিচ্ছিন্নভাবে আমার পরিবারের কাছে কিছু সাহায্য সহযোগিতা এসেছিল সত্য। তবে আমার নামে সাহায্য কমিটি পাঁচ মাসের বেশি অক্ষুণ্ন থাকতে পারে নি। রাজশাহীর কাজী আবদুল ওদুদের উপস্থিতিতে যে কমিটি গঠন হয়েছিল তারা পঞ্চাশ টাকার বেশি পাঠাতে পারে নি।
এ ছাড়া আমায় সাহায্য করার নামে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কমিটি গঠন হয়েছিল। ‘নজরুল রিলিফ ফান্ড’ নামেও তহবিল সংগ্রহ করা হয়। লটারি খেলার মাধ্যমে আমার নামে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আমি কিছুদিন স্বর্ণ ডিম্ব হংসে পরিণত হয়েছিলাম। অনেকে তা জবাই করলেও আমার পরিবারের প্রাণ তাতে রক্ষা হয় নি।
এরমধ্যে কয়েক বছর পার হয়ে গেল। আমিও দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যেতে থাকি। কৃষক প্রজা পার্টির হক সাহেবের কাছে থেকে অবিভক্ত বাংলার চিফ মিনিস্টারের ক্ষমতা ১৯৪৩ সালে চলে যায়—প্রাদেশিক মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে। দু’বছর পর লীগের সোহরাওয়ার্দির কাছে। আমার জন্য প্রাদেশিক সরকার মাসিক দুশো টাকা ভাতা মঞ্জুর করে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে, পরের বছর ১৯৪৫ আগস্টে বন্ধ করে দেয়া হয়, পুনরায় ১৯৪৬ সালের আগস্টে ভাতার টাকা দেয়া হয়। এভাবেই শুরু হয়, উপমহাদেশের আগস্টের খেলা। একচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে কবিগুরু মারা গেলেন, পরের বছর আগস্টের দিকে আমি অসুস্থ হলাম, একই বছর আগস্টে গান্ধী ব্রিটিশ চিরবিদায়ের ডাক দিল। এরপর একের পর এক ঘটতে থাকল ভয়াবহ সব আগস্ট দৈব। তারপর একদিন ঘটে গেল বাঙালি জাতির চূড়ান্ত আগস্ট ট্র্যাজেডি। আগস্ট ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ অব বাঙালি। এবার আমার জীবনে আবারও ভয়াবহ আগস্ট মাস ঘুরে এল—উনিশ শ ছেচল্লিশ সালে। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, পিতা বিচারপতি জাহিদ সোহরাওয়ার্দি, মা বিখ্যাত উর্দু কবি খুজাস্তা আখতার বানু, মামা হাসান সোহরাওয়ার্দি—কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য, ভ্রাতা বিখ্যাত হাসান সাহেদ সোহরাওয়ার্দি। তার এই পারিবারিক পরিচয় না ছিল গুজরাটি গান্ধীর না গুজরাটি জিন্নাহ’র। বাংলার হক, বাংলার সোহরাওয়ার্দি, বাংলার নাজিমউদ্দী পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিশাল যোগ্যতা নিয়েও বাংলার বিশাল ব্যর্থতা ঢেকে দিতে পারল না। শেষ বিচারে ব্যাবসায়িক বুদ্ধিই জয়ী হলো বাঙালির আভিজাত শ্রেণির নেতৃত্বের উপর।
১৬ আগস্ট ভোরে উত্তেজনা শুরু হয়। প্রথমে লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা উত্তর কলকাতায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য করায়—হিন্দুরা এর সমুচিত প্রতিশোধ হিসেবে লীগের শোভাযাত্রাসমূহের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। ওই দিন অক্টারলোনি মনুমেন্টে লীগের সমাবেশ এ যাবৎকালের মধ্যে মুসলমানদের সর্ববৃহৎ জমায়েত। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি ভাষণে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ‘নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে’ বলে ঘোষণা করায় সুযোগসন্ধানীরা ভাবল এটা প্রতিপক্ষের উপরে আক্রমণের মোক্ষম সময়। এই ভয়াবহ দাঙ্গায় যে সব এলাকা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল তা হলো দক্ষিণে বউবাজার স্ট্রিট, পূর্বে আপার সার্কুলার রোড, উত্তরে বিবেকানন্দ রোড ও পশ্চিমে স্ট্রান্ড রোড দ্বারা বেষ্টিত কোলকাতার বহুল জনাকীর্ণ অংশটি। সরকারি হিসাব মতে, এ দাঙ্গায় ৪,০০০ লোক নিহত ও ১,০০,০০০ আহত হয়েছিল। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন হত্যার ঘটনা ছাড়া ২২ তারিখের পর কলকাতার পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।’ যে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো এটিও রহস্যাবৃত্ত থেকে যায়। এই হত্যাকাণ্ড যারাই ঘটাক এতে মূলত হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত চেতনাকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছিল।
ঈশ্বরের নামে হত্যা হলে রক্ষার থাকে না কেউ। ঈশ্বরের জন্য সান্ত্বনা—মানুষও তার, ছুরিও তার।
সেদিনের সেই হত্যাকাণ্ড পার্ক সার্কাসের একদিকে ভগবান দাঁড়িয়ে দেখলেন, ময়দানের অন্যপ্রান্তে খোদাতালা, উভয় নীরবে চোখ মুছলেন, আর নিহতদের দ্রুত উঠিয়ে নিলেন তার বুকের কাছে—যারা জন্মের পর মণ্ডুচ্ছেদন করেছিল তাদেরও, যারা করে নি তাদেরও। প্রতিটি অঙ্গের স্রষ্টা যেহেতু তিনি নিজে। যারা মণ্ডুচ্ছেদনের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চায়, যারা অক্ষত থাকার পুরস্কার চায়। যদিও দিন শেষে ঈশ্বর তাদের মুখ লুকাবার জন্য রেখেছেন একই গর্ত। গর্তের কোনো জাত নেই, কারণ এই গর্ত থেকেই তারা উৎপন্ন এই গর্তে তাদের বিলীন এবং গর্ত থেকে তারা পুনরুত্থিত হবে। যে মানুষ বানাতে লেগেছিল তার কোটি কোটি বছর। পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হয়েছিল শুকনো মাটি। সহস্র কোটি বছর ধরে বৃষ্টিপাত ও রৌদ্র শেষে অগণিত ফেরেশতা ও দেবতার সময়হীন অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি মানুষের আকার দিতে পেরেছিলেন। তাই হিন্দু ভক্তরা এখনো তার মূর্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণে করে যাচ্ছে চেষ্টা, তার মুসলমার ভক্তরা অবিরত গাইছে আকারহীন অপার ক্ষমতার মহিমা। আজ এখানে যারা নিজেরা নিজেদের হত্যা করছে, তাদের পেছনেও রয়েছে ঈশ্বরের অগণিত সময়ের ইতিহাস, আজকের এই নিহত মানুষ তৈরি করতেও তার আগের মানুষদের তৈরি করতে হয়েছিল। তারপর তাদের সঙ্গেই তাদের শিশুদের বড় করে তুলেছিলেন তিনি। তাদের রেখেছিলেন দুইজন মানুষের মধ্যে। কারণ ঈশ্বর জানতেন, নাহলে তারা নিজেরাই হবে তাদের সন্তানের হন্তারক। ঈশ্বর কি পারতেন না নারী বা পুরুষকে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরির ক্ষমতা দিতে, রেতপাতের পরিপূর্ণ সুখ দিতে। বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন, তার এই মহামূলব্যান আবিষ্কার—মানুষ। অন্তত একজন সংহার করলেও অন্যজন করবেন রক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরের নামে হত্যা হলে রক্ষার থাকে না কেউ। ঈশ্বরের জন্য সান্ত্বনা—মানুষও তার, ছুরিও তার।
ঈশ্বর এই মহারণ কুরুক্ষেত্র ঘটাবেন বলেই হয়তো শান্তির বাণী প্রচারকদের এই মেদিনী থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন আগেই। তবু কবিগুরু সদর স্ট্রিটের দোতলার ছাদে চিলেকোঠায় কান্নায় ভারি হয়ে আসা বাতাসের মধ্যে মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে মনে মনে আবৃত্তি করে চললেন—
‘ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে, তারা বলে গেল ‘ক্ষমা করো সবে’, বলে গেল ‘ভালোবাসো’— অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো’। বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে’
আর আমি কাজী নজরুল ইসলাম—শ্যামবাজার স্ট্রিটের বন্দি খাচা থেকে চিৎকার করে গাওয়ার চেষ্টা করলাম:
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ, কাণ্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তিপণ! “হিন্দু না ওরা মুসলিম?” ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র!
কিন্তু খুব কম মানুষের কান অব্দি এই বাণী পৌঁছাল। দেশ নায়েক সুভাষ বসু অন্তর্ধান না হলে হয়তো তিনি এ গান শুনতে পারতেন।
জন্মের কিছুদিন পর থেকে আমি নিজের মায়ের অধিকার ছেড়ে যাদের মাতৃরূপে আঁকড়ে ধরেছিলাম—এই ভারতবর্ষ, এই অখণ্ড বাংলা মা—গিরিবালা দেবীর অন্তর্ধানের মধ্যে—তারাও—চিরদিনের জন্য আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেল। আমায় জন্ম দিয়েছিল ধর্মপ্রাণ এক মুসলমান মা, আমার স্ত্রীকে জন্ম দিয়েছিল ধর্মপ্রাণ এক হিন্দু মা—এক মুসলমান আর এক হিন্দু দুজনা মিলে তাকেই মা বলেছিলাম বহুদিন। যদিও সকল মায়ের মতো সে আজ সন্তানের দেহের সাথে বিলীন, তবু সন্তানের শরীরের সঙ্গে থেকে যায় সেই মায়ের শরীর।