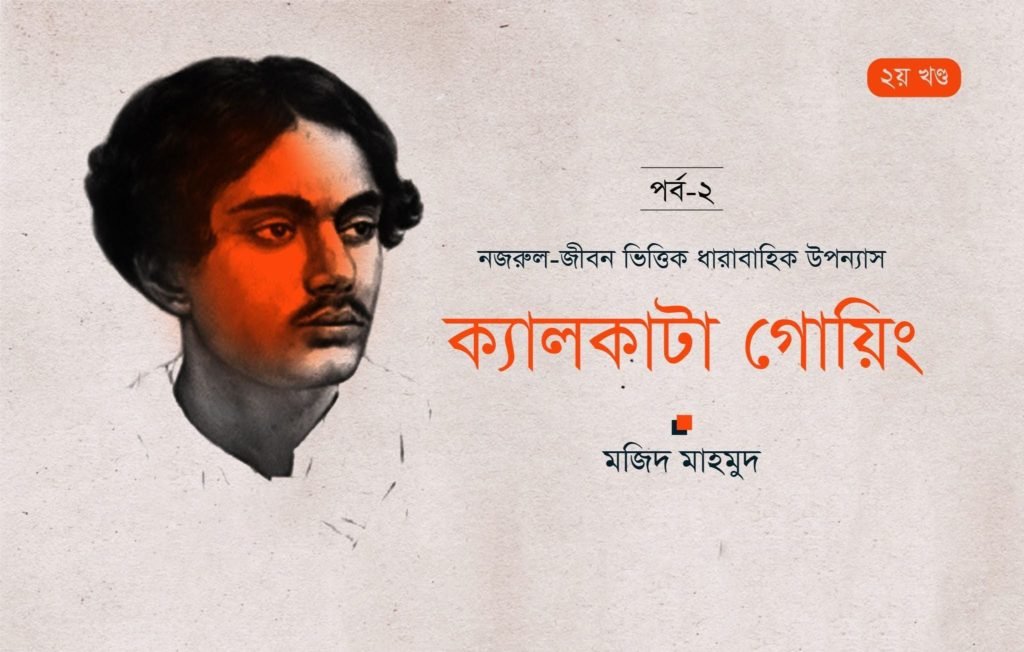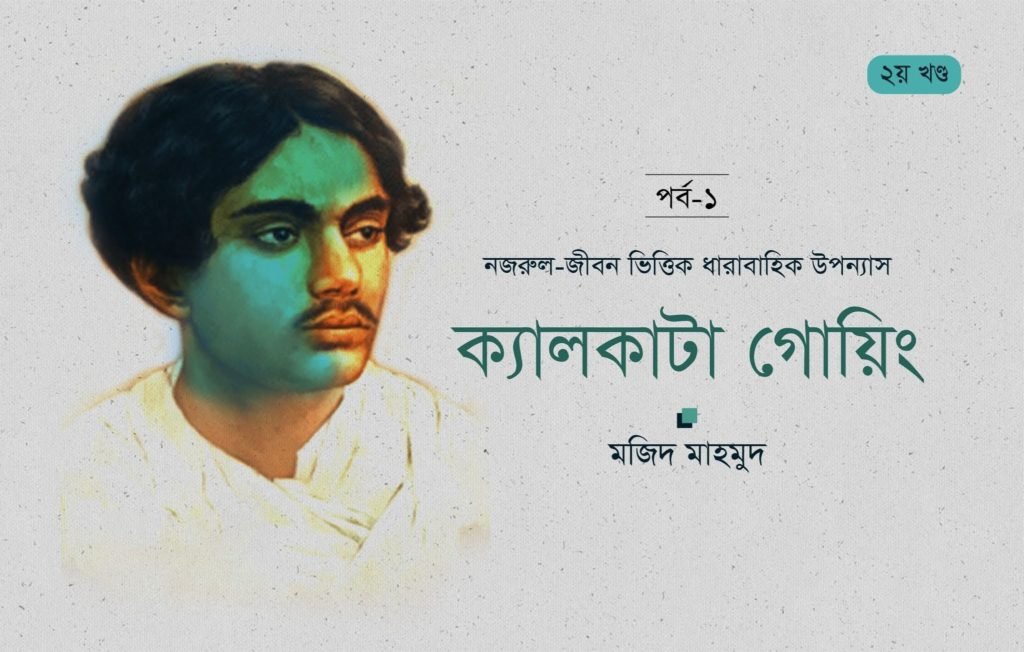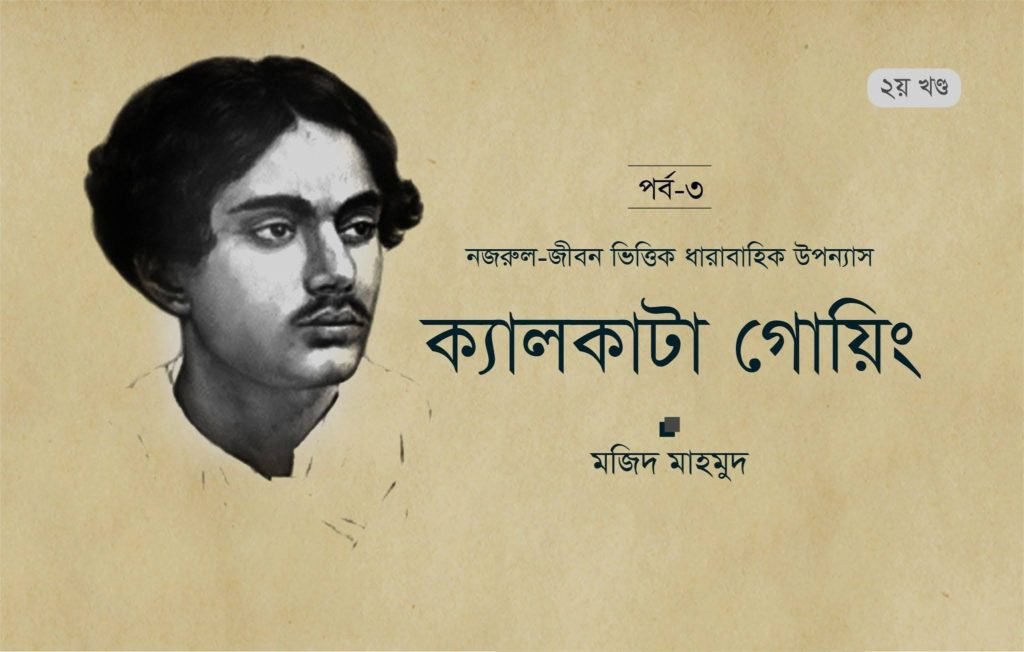পর্ব-২
উনিশ’শ আট সালে আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। যদিও তখন আমি নিতান্ত শিশু তবু অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি; যে শিশুকে আর মাত্র দু’এক বছরের মধ্যে নিজের জীবনের সব দায়ভার নিজেকেই বহন করতে হবে—তার জন্য বয়সের বেড়াজাল বিবেচ্য নয়। যে মৃগশিশু জন্মাবার মুহুর্তে অরণ্যে অধিকৃত সিংহ-ব্যাঘ্রের ভয়ে প্রাণ নিয়ে অতিষ্ঠ থাকে, তার জীবনে দৌড়ানো ও হাঁটা শিখবার বয়সের কোনো পার্থক্য থাকে না। মায়ের ফুল ঝরে পড়ার আগেই জীবন বাঁচানোর খেলায় তাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।
তুমি যদি সময়ের উপবাস সময়ে না করো তাহলে ভবিষ্যতের পুরো জীবন না খেয়ে থাকলেও তার সমান হবে না।
আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি, আমার শৈশবের দিনগুলোতে বয়স্করা সর্বদা মন খারাপ করে থাকত। বড়রা বড়দের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলত, মনে হাতো তারা মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছে, তার আশেপাশের কেউ জানতে পারলে তা এখনই কুড়িয়ে নিয়ে যাবে; কিংবা এমন কোনো অপরাধ—যা প্রকাশ হয়ে গেলে তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তারা শিশুদের সঙ্গেও এমনভাবে কথা বলত, মনে হতো—কোথাও তারা বেড়াতে এসেছে, যেন এই বাড়িটি তাদের নয়, কয়েকদিন পরেই তারা সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে—মুসাফির বা শরণার্থীদের মতো। এমনকি তারা নিজেদেরকেও এই দুনিয়ায় মুসাফির হিসাবে বর্ণনা করত, এটা একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র—নিয়মের বাইরে কিছু করার নেই। তারা সব কিছুতেই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করত, সতর্ক থাকত—যাতে বেড়াতে আসার ফলে তাদের বাচ্চাদের কোনো অভ্যাস পরিবর্তন না হয়ে যায়—যখন পুনরায় তারা বাড়িতে ফিরে দায়িত্ব বুঝে পাবে—তখন যেন সব ঠিকঠাক মতো করতে পারে। তাই তাদের শিশুদের পড়ানোর ভঙ্গিটিও অনেকটা প্রশিক্ষণের মতো ছিল। সকালে উঠেই তাদের সামরিক কায়দায় কসরত করতে হতো। সময়ের ব্যাপারে তাদের সর্বাধিক তাগিদ দেয়া হতো। মনে হতো তারা যেন সবাই এক অদৃশ্য সময়ের চাকরি করছে। সময়ের অধীনে তাদের বসবাস; সময়ের একটু হেরফের হলে মনে করা হতো তাদের দ্বারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে—এই অপরাধ থেকে তারা আর কখনো মুক্তি পাবে না। কারণ তারা সব কিছু ফিরে পেলেও বিগত সময়কে আর কখনো ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এমনকি তারা যা হারিয়েছে, তা মূলত সময়ের প্রতি অবহেলার ফল, সময়ের কাজ সময়ে না করার অর্থই হলো পাপ। তখনকার দিনে মুসলমান পরিবারগুলোতে সময়ের এটাই মূল্য ছিল—যার হেরফের হওয়া মানেই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবহেলা। আমি কিছুটা বড় হয়ে লক্ষ্য করেছি, শ্রীমদ্ভগবত গীতায় হিন্দুধর্মের মনীষীগণ যেভাবে কর্মযোগের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন—ঠিক সেভাবে ইসলাম ধর্মে ‘সময়নিষ্ঠা’র প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জীবনে সফলতা বিফলতা বলে মহাপ্রভুর কাছে আলাদা কিছু নেই। কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দেশিত কর্ম-সম্পাদন করে তাহলে তার দুনিয়ার কুরুক্ষেত্রের সফল সমাপন। মহানবীর একটি হাদিসে এ রকম আছে—‘তোমরা সময়কে গালি দিও না, সময়ই প্রভু।’ সব জাতির মধ্যে সময় গুরুত্বপূর্ণ হলেও মুসলমানরা সময়কে অনুসরণ করে যেভাবে তাদের উপাসনাদি পরিচালনা করত—তাতে মনে হতো তারা যেন সময়কেই উদ্যাপন করছে। তুমি যদি সময়ের নামজ ঠিক সময়ে না পড়ো, প্রভুর কাছে তার কোনো মূল্য থাকবে না, তুমি যদি সময়ের উপবাস সময়ে না করো তাহলে ভবিষ্যতের পুরো জীবন না খেয়ে থাকলেও তার সমান হবে না। কোরানে বলা আছে—‘যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে। আর অপরাহ্ণে ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও জমিনে সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।’—এর ব্যত্যয় করা যাবে না। যে এর অন্যথা করল সে ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদের শেখানো হতো—কেউ যদি এক ওয়াক্ত নামাজ ঠিক সময় মতো না পড়ল তাহলে পৃথিবীর সব সময় ধরে আদায় করলেও তার সমান হবে না; এমনকি তার শাস্তিও এত দীর্ঘ যে পৃথিবীর জীবনের সব সময় ধরে ভোগ করলেও শেষ হবে না। বড়রা বলতেন, মুসলমানদের যে আজ বড় দুর্দিন তার কারণ তারা সময়কে গুরুত্ব দেয়া ভুলে গিয়েছিল, মুসলমান রাজা বাদশারা সময়নিষ্ঠার বদলে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েছিল, তাই আল্লাহ তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।
আমাদের বলা হয়েছিল—আমি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলাম—তার নামের সঙ্গেও আমার পূর্ব-পুরুষের ইতিহাস জড়িয়ে ছিল। বলা হয়েছিল—চার আউলিয়া থেকে চুরুলিয়া হয়েছে—তার এক আউলিয়া ছিলেন আমার পূর্ব-পুরুষ, এলাকায় হাজী পালোয়ান নামে খ্যাত। ইসলামের শরিয়া অনুসারে তিনি তার কবরের উপরে কোনো মাজার তৈরি না করতে নির্দেশ দিয়ে যান। তার অনুসারীরা তার এই নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করেছে। আমরা ছোটবেলায় জঙ্গল ও ঘাসে ঢাকা পীর হাজী পালোয়ানের মাজার দেখে বড় হয়েছি। মাজারের খাদেমগণ বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তার কিছুটা পরিষ্কার করলেও কখনো পুরো সংস্কার করা হতো না। তরুণদের কেউ প্রস্তাব দিলে প্রবীণরা কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। হাজী পালোয়ান সাহেব বলতেন, আমাদের নবী এসেছিলেন কবর ভাঙার জন্য, কবর বাঁধাবার জন্য নয়। কবরের উপরে কোনো ইমারত তৈরি করা, পাকা কোনো স্মৃতিচিহ্ন করা সম্পূর্ণ বিদাত—অনৈসলামিক যুগের কাজ। যদিও বড় হয়ে দেখেছি, নবীর এই আদেশ মুসলমানরা খুব একটা মানে নি, কারণ তারা যে পরিমাণ কবর পাকা এবং মাজার তৈরি করেছে—তা আর কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় না। ভারতে মুসলমানদের সেরা কীর্তি তাজমহলও যে একটি কবরসৌধ এটি জানতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। হাজী পালোয়ান এলাকার মানুষের পানীয় জলের বন্দোবস্তের জন্য বিশাল একটি দিঘি খনন করেছিলেন। আগের দিনে ভারতবর্ষে যে সব মুসলিম পীর ও দরবেশ এ দেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের মানস নিয়ে, তাদের মধ্যে দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়—তারা ছিলেন শারীরিকভাবে বলশালী বা যোদ্ধা এবং অপরদিকে জনহিতৈষী। তারা সন্ন্যাস জীবনের পাশাপাশি স্থানীয় অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং গরিব অসহায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতেন। বর্তমান সময়ে তাদের খাদেমরা তাদের কবরকে ব্যবহার করে ভুলভাল ব্যাখ্যা দিয়ে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমার পূর্ব-পুরুষ হাজী পালোয়ানের শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে অনেক অলৌকিক গল্প এলাকায় চালু ছিল, হিংস্র বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে অন্ধকার রাতে এলাকা প্রদক্ষিণ করতেন, মানুষের যে কোনো বিপদাপদে তিনি ছুটে যেতেন, যাদের খাদ্য ছিল না—তিনি তাদের খাদ্য দিতেন। তার শারীরিক শক্তির কাছে দুই চার দশজন মানুষ সহজে ধরাশায়ী হতো বলে তার নামের সঙ্গে পালোয়ান নামটি যুক্ত হয়েছিল। হাজীও তার আসল নাম নয়, সে-আমলে হজ খুব সহজ ছিল না কিন্তু হাজী পালোয়ান সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সে-যুগে হাজী পালোয়ানের জন্য যে গল্পটি সত্য ছিল, সেই গল্পটিই শাহজালাল, খানজাহান, নিজামুদ্দীন আউলিয়া- সবার জন্যই সত্য ছিল। একজনের গল্প আরেকজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল—কখনো ইচ্ছেকৃত কখনো প্রক্ষিপ্ত। পীরের অনুসারীরা ভালোবেসে তাদের পীরের অনেক কেরামতির গল্প যুক্ত করে দিতেন। নানা দেবদেবির ভারতীয় সমাজ অলৌকিকত্ব ছাড়া কোনো কিছু সহজে গ্রহণ করতে চাইত না—বনবিবি, খোয়াজ-খিজির, গাজিকালু চম্পাবতী—বহু কাহিনির সমাহার ঘটেছিল। তাই তাদের দেবতা অবতারের মতো করে অনেকখানি গড়ে তুলতে হয়েছিল মুসলিম পীর-পয়গম্বরকেও। প্রথম দিকের একজন আউলিয়ার বর্ণনা ছিল এমন। এই গল্পের সঙ্গে তার পানীয় জলের দিঘি খনন ও ক্ষমতা বলয়ের ইতিহাস রয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ পারস্য রাজের আমন্ত্রণে সেদেশে গিয়েছিলেন মূলত হাফিজের সৌধ দর্শন করতে পারবেন এই ভরসায়।
১১৯২ সালে পৃথ্বিরাজ চৌহানকে পরাস্ত করে মোহাম্মদ ঘোরির কৃতদাস কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লির দখল নিয়েছিলেন। সেই থেকে দিল্লি মুসলিম শাসনের অধীনে ছিল প্রায় ছ’শ বছর। মুসলিম শাসকরা দিল্লির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বহুগুণে। ভারত একটি দেশ হলেও বাস্তবে এটি মহাদেশ; নানা ভাষা, ধর্ম, বর্ণ এমনকি নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অন্য কোনো একক দেশে আশা করা যায় না। দিল্লি থেকে দু’একবার রাজধানী স্থানান্তরের চেষ্টা যে হয় নি তা নয়; বিশেষ করে সুলতানী আমলের মুহম্মদ বিন তুগলুক দিল্লি থেকে রাজধানী সরিয়ে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিতে নিয়ে গিয়েছিলেন; নাম দিয়েছিলেন দৌলতাবাদ; কিন্তু সফল হতে পারেন নি। আবারও তাকে দিল্লি ফিরে আসতে হয়। তবে মুহম্মদ তুগলক ফিরে এলেও তার বাবা গিয়াসউদ্দিন তুগলক আর দিল্লিতে ফিরতে পারেন নি। তাঁকে নিয়েই বিখ্যাত সেই প্রবাদটি চালু হয়েছিল, ‘দিল্লি দূরাস্ত’। গিয়াসউদ্দিন শত্রুদমন করে মাসাধিককাল পরে রাজধানীতে ফিরে আসবেন; কিন্তু ফকির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে ছিল তার বিবাদ। একটি পানীয়জলের দিঘি খননের খয়রাতি কাজ নিয়ে তাদের এই দ্বন্দ্ব। সুলতানের অনুপস্থিতিতে তার নিষেধ সত্ত্বেও ফকিরের অনুগামীরা দিঘিকাটার কাজ সম্পন্ন করেন; সুলতানের ফেরার সময় ঘনিয়ে এলে তারই পুত্র পীরভক্ত মুহম্মদ বিন তুগলক বললেন, হুজুর এবার দিল্লি ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যান। আউলিয়া মুচকি হেসে বললেন, ‘দিল্লি হুনুজ দূরাস্ত’—অর্থাৎ ইঙ্গিত দিলেন সুলতানের আর দিল্লি ফেরা হবে না; তার জন্য দিল্লি এখন অনেক দূর। সত্যিই তাঁর আর ফেরা হলো না। দিল্লির উপকণ্ঠে সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠানে একটি পাগলা হাতি মঞ্চসহ উল্টিয়ে দিলে সুলতান চিরদিনের তরে তার নিচে চাপা পড়ে গেলেন। হস্তী-মহরতের দায়িত্বে ছিলেন, তারই পুত্র মুহম্মদ বিন তুগলক। অনেক ঐতিহাসিকই এই দুর্ঘটনার জন্য তার দিকেই আঙুল নির্দেশ করতে চান।
হাজী পালোয়ানের সঙ্গে এলাকার জমিদার রাজা নরোত্তম সিংহের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে অনেক লোক মারা যায়, যে মাঠে লড়াই হয়েছিল সেই মাঠটিকে আমরা মুড়মালা বলতাম। মানুষের কাটামুণ্ডের স্তূপ থেকে এ মাঠের নাম হয়েছিল মুড়মালা। যদিও রাজা নরোত্তম সিংহের দুর্গের কোনো ঐশ্বর্য আমার কালে টিকে ছিল না, তবু এই চুরুলিয়া ছিল নরোত্তম সিংহের রাজধানী। আমি শৈশবে রাজার এই গড় নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম।
আমাদের বলা হতো, ভারতের প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবউদ্দীনের সময়ে বাগদাদ থেকে এসেছিলেন আমার ভারতীয় প্রথম আদি পুরুষ সুফী সৈয়দ মুহাম্মদ ইসলাম। তার অধস্তন পুরুষ গোলাম মোহাম্মদ নখশবন্দ যখন পাটনা থেকে চুরুলিয়া আসেন তখন দিল্লির সম্রাট তাকে বহু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে-সব বিনা খাজনায় নিতে চান নি, সম্রাটও তার ইচ্ছেকে সম্মান দিয়ে নামমাত্র খাজনায় এই এলাকায় বিশাল তালুক প্রদান করেন। সেই থেকে কাজী বংশের সবাইকে আয়মাদার বলা হতো। আয়মাদার একটি সময়ে খুব সম্মানজনক উপাধি ছিল। যদিও আমার জন্মের পরে সে-সবের কোনো অর্থ ছিল না। তখন এদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানরা নিজ দেশে পরবাসীর মতো বসবাস করত। না তারা মূলধারার সঙ্গে মিশতে পারত, না নিজেদের সম্মান নিয়ে বাস করতে পারত। আমার জন্মের যদিও দেড়শত বছর আগেই ইংরেজ এদেশের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হয়ে বসেছিল, এমনকি মহাবিদ্রোহে নামকাওয়াস্তের দিল্লির সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের চূড়ান্ত পরাজয়ের অর্ধশত বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, তবু তারা তখনো এক অলীক স্বপ্নের জগতে বসবাস করত—একদিন হয়তো আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরে আসবে।
এসব গল্প শুনেই আমরা বড় হয়ে উঠছিলাম। আমাদের বাড়ির অন্দর মহলের সঙ্গে বাহির মহলের সম্পর্ক ছিল কম। পুরুষরা যখন তখন অন্দর মহলে ঢুকত না। বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে আদবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। দিনের বেলা তাদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কথাবার্তা শুনে বোঝার উপায় ছিল না, তাদের পরস্পরের সঙ্গে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে—যার বলে তারা একে আরেক জনের কাছাকাছি আসতে পারে। ছেলে শিশুদের বয়স পাঁচ ছয় বছর হওয়ার পর থেকে অন্দর-মহলে তেমন যাতায়াত করতে দেয়া হতো না। কেবল খাওয়া দাওয়া ও বিশেষ প্রয়োজনে তারা মা ও বড় বোনদের সঙ্গে মিশতে পারত। বাকি সময় তাদের মাদরাসা মক্তবে পড়াশোনা করে, খানকা ঘরে মৌলবি কিংবা বড়দের কাছে নানা কিচ্ছা কাহিনি পুঁথি শুনে সময় কাটাতে হতো। আর পাড়ার বয়স্ক ছেলে শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে তারা সময় কাটাত। খেলা বলতে তখন হাডুডু ও বলীখেলাই প্রধান ছিল, ডাঙ্গুলি ও গোল্লাছুট; মেয়েরা হাডুডু ও বলী না খেললেও অন্যারা গোল্লাছুট দাড়িয়াবান্দা ও লুকোচুরি খেলত; তবে ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্দর মহলে মেয়েরা দাবা ও লুডু খেলে সময় কাটাত। ফুটবল খেলারও প্রচলন ছিল, আমি শৈশব থেকে প্রায় সব ধরনের খেলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার সমবয়সীরা কেউ আমার সঙ্গে শারীরিক কসরতে পেরে উঠত না, খেলার প্রতি আমার আজীবন টান ছিল। বড় হয়েও খেলা দেখার নেশায় বিনা নোটিশে বাড়ি ছেড়েছি, শুধু পান-চায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবা খেলেছি। বাড়ির পাশের পীর পুকুরের সামনাসামনি ছিল প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি কে তৈরি করেছিল তার কোনো ইতিহাস নেই। তবে ধারণা করা হয়—হাজী পালোয়ানই প্রথম এ মসজিদ তৈরি করেন। আমার বাবা ছিলেন এই মসজিদের খাদেম, একই সঙ্গে তিনি হাজী পালোয়ানের দরগা ও পীরপুকুরেরও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। চুরুলিয়ার কাজীরা বংশ পরম্পরায় এই মসজিদ মক্তব ও দরগার খাদেমগিরি করার সম্মান পেয়েছিলেন। যে কারণে গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে আমাদের পরিবারকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হতো, যদিও অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারের চেয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। বাবা বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা খুব একটা বুঝতে পারি নি। বাবার সাথে আমরাও প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় বাড়ির পাশের মসজিদে যেতাম। পাশে পীরপুকুর থাকলেও খুব ছোট বেলায় সাঁতার শেখা হয় নি। পরে রানীগঞ্জ সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে শৈলজার অনুপ্রেরণায় সাঁতার শিখেছিলাম। বাবা ও চাচা বজলে করিমের মুখে তখন হাফিজ রুমি শাদির অনেক বয়াত শুনতাম। এখনো মনে আছে আমার পিতা প্রায়ই হাফিজের এই গজলটি গাইতেন—‘য়ুসোফ গুম্ গশতা বাজ্ আয়েদ ব-কিনআন গম মখোর’। এই কবিতার অর্থ তখন বুঝতে না পারলেও ভাবতাম—এমন কিছু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে—যা খুবই প্রত্যাশিত। আমারও কবিতাটি এতই ভালো লেগে গেল—অর্থ ছাড়াই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ফারসি শেখার পরে আমি এটি অনুবাদও করেছি। যার অর্থ ছিল—‘দুঃখ কি ভাই, হারানো ইউসুফ কেনানে আমার আসবে ফিরে।’ এরই অনুকরণে ‘বিশের বাশী’র বোধন কবিতায় লিখেছিলাম—
‘দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥’
হাফিজের এই কবিতার সঙ্গে মুসলমানরা তখন ভারতে তাদের হারানো স্বাধীনতার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিল। ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতায় পিতা ইয়াকুব নবীর কাছ থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। পিতার সেই দুঃসহ দিনগুলোর কথা, নতুন করে ইউসুফের রাজরূপে ফিরে আসার কথা এই কবিতাতে বিধৃত হয়েছে। কেবল এই কবিতাই নয়, হাফিজের আরো অনেক কবিতা আমার বাবা ও বজলে করিমের কণ্ঠে এক শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিত। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করতাম এই কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি ও মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ত। সত্যি কথা বলতে কি, হাফিজের মতো আর কোনো বাঙালি কবি আমাদের পরিবারে চর্চা ছিল না, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নাম তখনো আমরা শুনি নি। তবে হাফিজের কবিতার অর্থ ও তার প্রতি আমার বাবার ভালোবাসা আমাকে কবি হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বড় হয়ে জেনেছি—কবিগুরুর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। কবিগুরুর পিতার প্রিয়কবি ছিলেন পারস্যের শামসুদ্দিন হাফিজ। এমনকি এই মহির্ষি তাঁর পুত্রের নামের ক্ষেত্রেও এই মহাত্মার নামের বাংলা অর্থকে কাজে লাগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পারস্য রাজের আমন্ত্রণে সেদেশে গিয়েছিলেন মূলত হাফিজের সৌধ দর্শন করতে পারবেন এই ভরসায়। হাফিজের কবরে গিয়ে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একা একা সেখানে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন, আর ভেবেছিলেন কে এই সাধক কবি যে একই সঙ্গে প্রাচ্যের শিক্ষিত হিন্দু মুসলিমের প্রাণের কবি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হাফিজের কবরের কাছে এসে আফসোস করেছিলেন—তিনি যদি পিতার মতো ফারসি ভাষা শিখতে পারতেন, তাহলে এই কবিকে আরো বেশি করে অনুভব করতে পারতেন। কবিপিতা তার প্রার্থনার সময়ও এই কবির কবিতা সম্বলিত ঘণ্টা ব্যবহার করতেন, যেখানে লেখা ছিল—‘মা রা দর মনযিলে জানাঁ চে আম্ন ও আয়শ চুঁ হর দম/ জরস ফরিয়াদ মিদারদ কে বর-বনদিদ ম্যাহমিলহা।’—যার অর্থ ‘প্রিয়ার পথে চলতে গেলে বড় কঠিন সে গমন/ থামবে কখন—চলো চলো বলতে থাকে সারাক্ষণ।’
কবিগুরুর রচনা ধারা রায় বাবুর খুব একটা পছন্দ ছিল না।
হাফিজকে বলা হতো ‘লিসানুল গায়েব’—যিনি অদৃষ্টের কথা বলতে পারেন। কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করতে চাইলে ‘দিওয়ানে হাফিজ’ হাতে নিয়ে পাতা উলটে চোখ বন্ধ করে তাঁর গজলের উপর হাত রাখেন। রবীন্দ্রনাথ হাফিজের সমাধি দর্শনে গেলে, সমাধি রক্ষকরা তাঁর হাতে দিওয়ানে হাফিজ দেন। নিজ দেশের দুর্দশার কথা ভেবে কবি যে পঙ্ক্তিতে আঙুল রাখেন তার বাংলা অর্থ—
আর কি কখনো খুলবে হেতায় সরাইখানার বন্ধ দোর,
নিজের ঘরের বাইরে আসন থাকবি এমন ভাগ্য তোর।
যদিও কপট ভণ্ডরা আজ দিয়েছে কঠিন দরোজা খিল,
হতাশ হয়ো না নিশ্চয় প্রভু দরোজা খোলার দেবেন দিল।
কবিগুরু এই ভারতের এই দুঃসময়ে হাফিজের দিক নির্দেশনায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। আমিও তখন কবিখ্যাতির শীর্ষে। তিনি যখন পারস্যে যান তখন তার বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গেছে, পরাধীন দেশের এই কবি জীবন সায়াহ্নে এসে নিজের জাতির স্বাধীনতা দেখার জন্য কিছুটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। আমার শৈশবে পারিবারিক কারণে পারস্যের এই কবি বড় আপন হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি আমার চরিত্র গঠনে হাফিজের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল। পরবর্তীকালে কবিগুরু নোবেল পাওয়ার পরে যখন তার নামদাম হলো, আমারও বয়স বাড়তে থাকল তখন তাঁর প্রতিও হাফিজের মতো অনুরাগ তৈরি হয়ে গেল। আমি সে-সময়ে তার এত গান মুখস্থ করেছিলাম যে, আমাকে সবাই রবীন্দ্র সংগীতের হাফিজ বলত।
রবীন্দ্রনাথের আগে ডিএল রায়ের গান কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে আমাকে বিনোদ চাটুজ্জ্যের পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হয়। অনেকে মনে করে থাকেন বাড়ির পাশের মক্তবে আমার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল, সেখানে খুব বেশিদিন না থাকলেও চাটুজ্জ্যে পণ্ডিত আমায় খুব আদর করতেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান এমনকি সংস্কৃতি শ্লোকের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল। পাঠশালাটি ছিল গ্রামের এক প্রান্তে বেনিপাড়ায়, চুরুলিয়া গ্রামে মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করত। হিন্দুদের মধ্যেও অনেক জাত প্রথা থাকায় তাদের মধ্যে বর্ণভেদে পৃথক পাড়া-মহল্লা স্থাপিত হতো, নিচু বর্গের লোকজন উঁচু বর্গের মধ্যে খুব একটা বাস করতে পারত না। বেনিরা হিন্দু হলেও জাতে নিম্নবর্ণের হওয়ায় সেখানে আমার পাঠ গ্রহণে বাধা হয় নি। নিম্নবর্ণের হিন্দু ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বরং মুসলমান ছেলেমেয়েদের বেশি মিল থাকত। পাঠশালার পণ্ডিত বিনোদবিহারী নিজেও ধর্ম ও বর্ণ আলাদা করে দেখত না। বলা চলে এখানে জীবনের শুরুতে আমার এই শিক্ষা হয়েছিল, ধর্ম ও সংস্কৃতি আলাদা হলেও মানুষে মানুষে কোনো তফাত নেই। আমার পরিবারের মধ্যেও সেই শিক্ষা ছিল বলেই তারা কাজী বাড়ির নিজস্ব মক্তব থাকতেও পণ্ডিত বিহারীর পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। তখন একজন শিক্ষক পণ্ডিত বা মৌলবিকে কেন্দ্র করেই প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠত। যারা কিছুটা লেখাপড়া জানতেন দেশ দুনিয়ার খবর রাখতেন তারাই মুলত এ ধরনের পাঠশালা খুলে ছাত্র পড়াতেন। এদের অধিকাংশ ছিল দেশ মাতৃকার সন্তান—যারা মনে-প্রাণে বিদেশি শাসনের পতন চাইতেন। পুলিশের চোখ এড়িয়ে স্বাধিকার আন্দোলনে কাজ করতেন। আজ মনে হয় বিনোদ বিহারীও ছিলেন এমন একজন শিক্ষক। তার পাঠশালায় সমবেতভাবে দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হতো, তার অর্থ খুব ভালো করে না বুঝলেও গানের কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, পরে জেনেছিলাম এই গানের লেখক ডিএল রায়—যার পুত্র দীলিপ কুমার রায় ওরফে মন্টু দা আমার প্রাণের বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়েছিল—দীলিপ এবং সুভাষ বন্ধুও সহপাঠী ছিল। আমাদের শৈশবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিখ্যাতি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি ছিল। রায় বাবুও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো মস্ত পরিবারের সন্তান, রবিবাবুর পরে তিনিও লন্ডনে নিজের শিক্ষা জীবন শেষ করেছিলেন। বয়সে কবিগুরুর দুবছরের ছোট হলেও তার গান, নাটক কৌতুক প্রিয়তা মুখে মুখে ফিরত। কবিগুরুর রচনা ধারা রায় বাবুর খুব একটা পছন্দ ছিল না। আমার শৈশবে ডিএল রায় মহাশয়ের অনেক গান মুখস্থ হয়েছিল, তার মধ্যে একটি গানের কয়েকটি চরণ ছিল এমন:
‘বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রী আমার ! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ।’
এ গানটি গাওয়ার সময়ে আমার তরুণ প্রাণের কোথায় যেন দোলা লাগত, মনে হতো এটা সেই গান যা ফারসিতে তার পিতার মুখে শুনেছেন। আসলে সব মিলে কোথায় যেন একটি হারানোর বেদনা এক সুরে বেজে উঠেছিল—হিন্দু হোক মুসলমান হোক—কারো মনে তখন তার মাতৃভূমি নিয়ে সুখ ছিল না। এতবড় একটি ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটি তার সন্তান, অথচ বাইরে থেকে কিছু লোক এসে তাদের সব কিছু দখল করে রেখেছে।
আরেকজন কবির কথা আমি সেই শৈশবেই শুনেছিলাম, সেই কবিরও ছিলেন আমার জন্মভূমি বর্ধমানের মানুষ। যদিও তার জন্ম হয়েছিল হুগলির কালনায়, তবু সেটি বর্ধমান লাগোয়া। তিনি হুগলি মোহসিন কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের চরিত্র মাধুর্য ও দানশীলতা নিয়ে তখন মুসলামন পরিবারগুলো অনেক গর্ব অনুভব করত। এই মহাত্মা তাঁর বিপুল সম্পত্তি হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষা প্রসারে ব্যয় করেছিলেন। তাঁর দেয়া বৃত্তির অর্থে বঙ্কিম থেকে অনেক মহৎ সাহিত্যিকগণ লেখাপড়া করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির মহিয়সী স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে নিয়ে ‘হুগলির ইমামবাড়ী’ নামে উপন্যাস লিখেছিলেন। অনেকে মনে করে থাকেন কবিগুরু তাঁর এই প্রতিভাবান অগ্রজার প্রতি খুব সুবিচার করেন নাই, অনেকে বাড়িয়ে বলেন—ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিভা কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। যে কবির কথা বলছিলাম তাঁর নাম ছিল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দু’একটি গান আমার তখনই মুখস্থ ছিল—‘স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পড়িবে পায়।’ যদিও বড় হয়ে জেনেছিলাম এই কবিতাটি ইংরেজের বিরুদ্ধে লিখিত হয় নাই। এটি রাজস্থানে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাজপুত বীরত্বের কাহিনি গাঁথা ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’-এর অংশ। সে যাই হোক, তার এই কবিতার চরণের মধ্যে মানুষের চিরন্তন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অক্ষয় রূপ পেয়েছে। এই স্থলে বলে রাখি, আমার শৈশবে ডিএল রায়, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ইসমাইল হোসের সিরাজী মানস গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। আমার আগে সিরাজী সাহেবই একমাত্র কবি যিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে দুই বছর জেল খেটেছেন, তাঁর বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তাঁর হৃদয়ও ছিল অনেক বড়, আমি অনেক নারীকে মা বলে সম্বোধন করেছি, কিন্তু পিতা বলে একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করেছি।
এলাকার মহানন্দ আশ নামে এক জুয়াড়ির কাছে আমার সরল বোকা প্রকৃতির পিতা সব পাশা খেলে হারিয়ে ফেলেছে।
চাটুজ্জ্যে পণ্ডিতের পাঠশালায় আমার খুব বেশি দিন পড়া হলো না। সেখান থেকে নিয়ে এসে আমাকে বাড়ির পাশে মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হলো। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাদের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, আমায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমার পিতার উপলব্ধি হয়, সেটি আর তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সোমত্ত পরিবার থেকে আমরা পথের নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আমরা বুঝতে পারলাম, বাড়িতে খাবার কষ্ট হতে শুরু হয়েছে। বাবা প্রায়ই রাত করে বাড়িতে ফেরেন, মাকে প্রায়ই কাঁদতে দেখি। বড় ভাই সাহেবজানকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। সে সংসারের কাজে হাত লাগাতে শুরু করছে, অথচ এই কাজগুলো এতদিন অন্য লোকে করত। আমরা অল্পদিনের মধ্যে জানতে পারলাম, মাঠে আমাদের যে সব ধানী জমি ছিল সেই জমির মালিক এখন আর আমরা নই। এলাকার মহানন্দ আশ নামে এক জুয়াড়ির কাছে আমার সরল বোকা প্রকৃতির পিতা সব পাশা খেলে হারিয়ে ফেলেছে। এই ঘটনার পরে তিনি কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতেন না। মসজিদ আর হাজী পালোয়ানের মাজারে দিনরাত অধিকাংশ সময় পড়ে থাকতেন। মসজিদে ইমামতি ও খাদেমগিরি করে তার সময় পার হয়ে যেত। কখনো রাতে ফিরতেন, কখনো ফিরতেন না। অনেক রাতে ফিরলেও ফজর নামাজের আজানের আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। মূলত তখন থেকে আমার পরিবার অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। বাবার শরীর ভেঙে পড়ে, হয়তো জমি হারানোর বেদনায়, তার বোকামির কথা ভেবে, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি মুষড়ে পড়েন। একটি পরিবারের জন্য চল্লিশ বিঘা জমি যথেষ্ট ছিল, সোম বছরের খাওয়া দাওয়া সব খরচ সেখান থেকে আসত। মসজিদে ইমামতি ও খাদেমগিরি করে যে নগদার্থ পেতেন তা দিয়ে আমাদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য খরচ ও দান-খয়রাত চলত। আমি ভাবি, মহাভারতের কালের রাজ-রাজড়ার জন্য রাজ্য হারানো যেমন খেলাচ্ছলে ঘটে যেত, নবাবের জন্য তা আম্রবাগানে এক রাতে নির্ধারণ হতো কিংবা তাবত ভারতবর্ষ একদিন কিংবা এক রাতের কয়েক হাজার মানুষের প্রাণপাতে কার কাছে যাবে নির্ধারণ হতো, ঠিক সেভাবেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন জুয়া নির্ধারণ করে দিত।
এই ঘটনার পরে সত্যিই আমার পিতার পক্ষে বেঁচে থাকা সহজ ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি তার সুঠাম দেহ ভেঙে পড়ে। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় আমাদের ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু একই সঙ্গে আমাদের পরিবারকে অকূল সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল, আর আমাকে এক হেঁচকা টানে পৃথিবীর পথে বের করে এনেছিল।