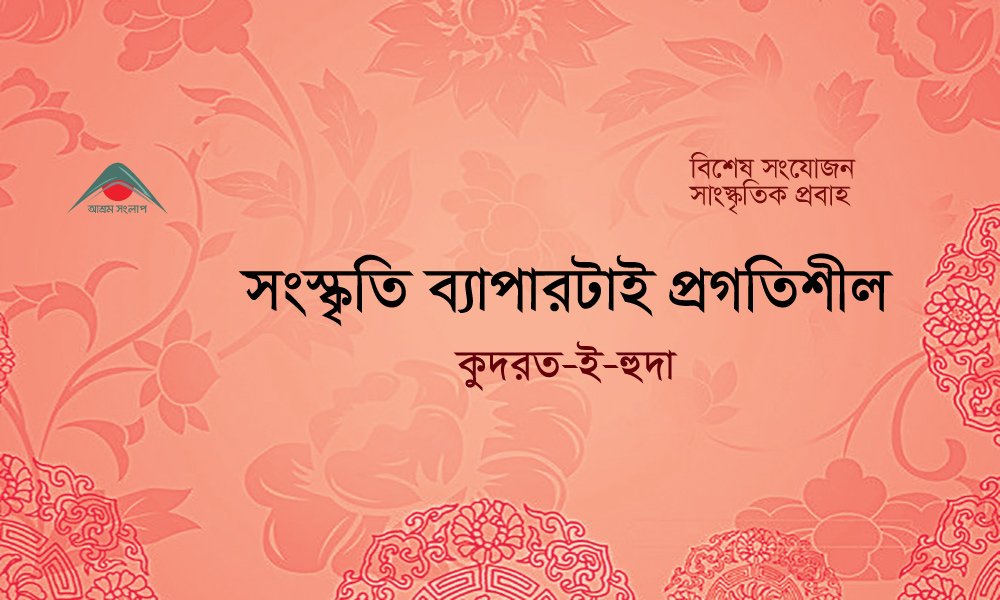মানুষ যা করে তাই সংস্কৃতি। সেই হিসাবে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যা করে সেটাই ওই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। যা করে বলতে বোঝাচ্ছি, একটা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত যত কর্মকাণ্ড ও ভাবনা-প্রকল্পনার ভেতর দিয়ে যায় তার সাধারণ (Common) প্রবণতাগুলোই তাদের সংস্কৃতি। ধরা যাক, বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা। অথবা ধরা যাক খাদ্যাভ্যাসের কথা। বাঙালির বিবাহ অনুষ্ঠানের কিছু রীতিপদ্ধতি সংস্কার চালু আছে। এই রীতিপদ্ধতি ও সংস্কারই বাঙালির বিবাহের সংস্কৃতি। আর খাবারের আয়োজনে মাছ-ভাত ও শাকান্নের যে অনিবার্য উপস্থিতি তা এই জনগোষ্ঠীকে খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়। এমনকি এসব খাবরের রন্ধন প্রক্রিয়া দিয়েও এই জনগোষ্ঠীকে অন্যদের থেকে আলাদা করা সম্ভব। ধর্মাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিনোদন ইত্যাদি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। সংস্কৃতি জনগোষ্ঠীর জীবনাচার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। এর সাথে জাতির সম্পর্ক জৈবিকসূত্রে গাঁথা। সংস্কৃতি জাতির জীবন্ত অস্তিত্বেরই অংশ।
কোনো জনগোষ্ঠী চিন্তায়-শিক্ষায়-রুচিতে-যাপনে চিরকাল একই জায়গায় স্থির থাকে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে রূপান্তর দেখা দেয়। সংস্কৃতির চলমান বাঁধা তারে এই রূপান্তরের ঝংকার ওঠে। এই রূপান্তরের ফেরে এক সময়ের জীবন্ত সাংস্কৃতিক উপাদান পরবর্তীতে অতীতের ফসিলে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এটি মানুষের জীবনের মতোই সদা পরিবর্তনশীল ও স্থিতিস্থাপক। ফলে সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় তেজাবি কোনো বিষয় নয়।
সংস্কৃতি শুধু পরিবর্তনশীল তা নয়, তা অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূগোলের রঙেও রঙিন থাকে। এ কারণে এক দেশ বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অন্য দেশ বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মতো হয় না। হতে পারে না। এমনকি একই ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সংস্কৃতির মধ্যেও রূপ-রঙের ভিন্নতা থাকতে পারে। ভিন্নতা থাকতে পারে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষদের সংস্কৃতির মধ্যেও। ইউরোপের সব এলাকার বা আরবের সব এলাকার মানুষের সংস্কৃতি নিশ্চয়ই এক নয়। হতে পারে না। বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের সব সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে মিল পাওয়া যাবে না। উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতিরই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আছে। দুই অঞ্চলের মানুষের ধর্মবিশ্বাস থেকে শুরু করে যাপন, বাস্তু-সংস্থাপনরীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিনোদনরীতিও নিশ্চই ভিন্ন। বহুবর্ণিলতাই সংস্কৃতির শোভা-সৌন্দর্য ও নিয়তি। সুতরাং সংস্কৃতি ব্যাপারটার মধ্যেই একটা স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপার আছে। জনগোষ্ঠীর নিজস্ব যাপনের পক্ষে থেকে এই সংস্কৃতির বাহারি ফুল ফোটে।
এ কারণে ব্রিটিশ আমল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস যেমন রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রামের ইতিহাস তেমনি তা সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রামের ইতিহাসও বটে। অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বে থেকে বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন অনুভব করেছে। একইভাবে পাকিস্তান আমলেও সে সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন অনুভব করেছে। কারণ, ওই দুই আমলেই বাঙালি বোধ করেছে যে, সে চাপানো একটা সংস্কৃতির তলে পড়ে ক্রমাগত হাঁফিয়ে উঠছে। একটু গভীরভাবে ইতিহাসের ভেতরে চোখ রাখলে বোঝা যায়, ওই দুই আমলেই অধিপতি সংস্কৃতিওয়ালাদের তরফ থেকে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এরই ফলশ্রুতি দেশভাগ ও বাংলাদেশ। তবে বলে রাখা দরকার যে, দুই আমলেরই এই সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির মূল নিহিত ছিল অবশ্যই অর্থনীতি ও আত্মমর্যাদাবোধের মধ্যে। অর্থনীতি ও আত্মমর্যাদা নামে সাংস্কৃতিক বিভাজনের নামই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।
সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল এবং যাপিত জীবনকেন্দ্রিক হলেও উপনিবেশিত দেশগুলোতে সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভাবনা একটু ভিন্ন হয়ে থাকে। উপনিবেশিত এলাকায় সংস্কৃতি বলতে ধ্রুব, শাশ্বত ও আদর্শ কোনো কিছুকে বোঝানো হয়। এখানে মনে করা হয়, সংস্কৃতি কোনো ‘ভালো একটা ব্যাপার’, ‘আদর্শ ব্যাপার’, ‘প্রমিত ব্যাপার’। এখানে এও ধারণা করা হয় যে, সংস্কৃতি বাইরে থেকে আসে এবং একটা জনগোষ্ঠীর কাজ এটিকে কসরত করে আয়ত্ত করা। এ কারণে আমাদের উপনিবেশিত বাংলায় সংস্কৃতির ‘ছোটলোক’ ও ‘বড়লোক’ ভাগ আছে। এই ভাগের ব্যাপারটা ইতিহাসবাহিত হয়ে বাঙালির মগজে ঢুকে গিয়েছে। অবশ্যই এই ইতিহাসের কারখানা বিলেতে অবস্থিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, উপনিবেশতত্ত্বের নিয়মানুযায়ীই ইংরেজ মনে করত, ভারতের বা বাংলার সংস্কৃতি মানে ‘অসভ্যের নিম্নমানের সংস্কৃতি’। তারা মনে করত, সাদা ইংরেজের সংস্কৃতিই ‘সেরা সংস্কৃতি’। সুতরাং ‘অসভ্যদের’ উচিত তাদের মতো ‘সভ্যদের’ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করা। তাদের ধারণা ছিল, এই অনুসরণ বা চর্চার ভেতর দিয়ে ভারতের বা বাংলার কালো কালো নেটিভরা কিছুটা ‘সংস্কৃতিবান’ হয়ে উঠতে পারে।
সংস্কৃতি বিষয়ক এই ধারণাটিই উনিশ শতকে বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আকরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতা আজো বিদ্যমান বলে মনে হয়। এই কারণেই বাংলা অঞ্চলে সংস্কৃতি মানে ‘সংস্কার’, ‘শুদ্ধিকরণ’; ‘অনুশীলনে অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষ’। এগুলো যারা সংস্কৃতির ওই আদর্শ ব্যাপারগুলোকে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারে তারা ‘সংস্কৃতিবান’, ‘পরিশীলিত’, ‘কৃষ্টিসম্পন্ন’। আর যারা পারে না তারা ‘আনকালচার্ড’। বাংলা ভাষায় ‘সংস্কৃতি’ ও ‘কৃষ্টি’ শব্দ নিয়ে যতই ঠেলাঠেলি হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ যা-ই বলুন না কেন, দুটোর ভেতরের কথা আসলে একই। অধরা আদর্শকে সামনে রেখে ‘চর্চা’ বা ‘অনুশীলন’ বা ‘কর্ষণের’ মাধ্যমে নিজেকে উর্বর করার নামই ‘কৃষ্টি’ বা ‘সংস্কৃতি’। সংস্কৃতি সম্পর্কিত এহেন ধারণা মনোজগতের উপনিবেশায়নের ফল বলেই মনে হয়। এবং যে কথা আগেই বলেছি, সংস্কৃতি সম্পর্কিত এই ধারণা অবশ্যই শ্রেণিবিভাজনে বিশ্বাসী; উচ্চ ও নিম্ন সংস্কৃতির তত্ত্বে আস্থাবান। কিন্তু সংস্কৃতি তো উচ্চ-নিম্নের ব্যাপার না; ‘বড়লোক’ ‘ছোটলোকের’ ব্যাপার না। সংস্কৃতি যেখানে যেমন সেখানে তেমন; যেখানে মানুষ ও যাপনপদ্ধতি যেমন সেখানে সংস্কৃতি তেমন। বৈচিত্র্য ও স্থিতিস্থাপকতাই সংস্কৃতির প্রধান সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য।
সংস্কৃতি বিষয়ক উপনিবেশিত চেতনার আরেক দিক নিহিত আছে এই ধারণার মধ্যে যে, সংস্কৃতি ব্যক্তিতান্ত্রিক ব্যাপার। কিন্তু আসলে সংস্কৃতি একটি সামষ্টিক ব্যাপার। সমষ্টির সাংস্কৃতিক চৈতন্য ব্যক্তির জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কিলবিল করতে থাকে। ব্যক্তির যাপনের বিচিত্র পরিসরে পানির নিচের মাছের মতো সামষ্টিক সংস্কৃতি তার ফুটকি ওঠাতে থাকে। ফলে ব্যক্তি ধরা পড়ে যায় তার সামষ্টিক সংস্কৃতির রূপবান ও রঙিলা জালে। ব্যক্তি ‘তারে পারে না এড়াতে’। তবে ব্যক্তিতান্ত্রিকদের মত এই যে, সমাজ যেহেতু বিচিত্র ব্যক্তির সমবায়ী প্রতিষ্ঠান সেহেতু ব্যক্তির সংস্কৃতিই সমাজের সংস্কৃতি। এজন্য বাংলার সংস্কৃতিকর্মী ও অধিকাংশ তাত্ত্বিক ব্যক্তিক চর্চাকেই গুরুত্ব দেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী থেকে শুরু করে অধিকাংশ বাঙালি সংস্কৃতিচিন্তক ব্যক্তিক চর্চাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সংস্কৃতি বিষয়ক এই ব্যক্তিবাদী ধারণাটার সাথে আসলে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের ‘রেনেসাঁস’ সমষ্টির অধিকাংশকে কিছুতেই আলোকিত করতে পারেনি। সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ প্রমুখ ঐতিহাসিক তাঁদের বিচিত্র লেখাপত্রে খুব স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছেন যে, সেকালে ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের মুষ্টিমেয় বড়লোক শ্রেণির মানুষ। তারাই ব্যক্তিগতভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয়। তৎকালীন সমাজ ও পরিবারে তারা অধিকাংশই বিবেচিত হতেন বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত মানুষ হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, উনিশ শতকের অন্যতম রেনেসাঁ-পুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে দারুণ এক কৌতুককর কিন্তু অব্যর্থ তথ্য দিয়েছেন। শাস্ত্রী বলছেন, তিনি যখন সনাতন থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন তখন কলকাতা থেকে এক ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে আসলে তাঁকে দেখার জন্যে গ্রামের অনেক মানুষ ভীড় করে। তাঁদের কৌতূহল ছিল ব্রাহ্ম হলে মানুষ দেখতে কেমন হয়! ঘরের মধ্যে বসে তিনি সম্ভবত মুড়ি খাচ্ছিলেন। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। এক কৌতূহলী নারী অবাক হয়ে পাশের একজনকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, ‘ওমা! দেখেছিস, এ তো দেখি আবার খায়ও!’ একই ধরনের বিস্ময় ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছিলেন ওই কালের ইয়ং বেঙ্গলের প্রায় সব সদস্য থেকে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত সবাই। আসলে একটু টেনে বললে বলতে হয়, উনিশ শতকের অধিকাংশ চিন্তক-বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সত্য ছিল। ফলে পরবর্তীতে এইসব রেনেসাঁ-পুরুষদের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কিছুতেই সমষ্টিকে যুক্ত করে কথা বলা যায়নি। তাই ওই সংস্কৃতি ও এর সাথে যুক্ত মানুষদের ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যক্তির ধারণা মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সংস্কৃতিচিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টি বা সমাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সামষ্টিক সংস্কৃতির ভিত এত শক্ত যে, তাকে আমূল নাড়িয়ে দেয়া একক ব্যক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। সামষ্টিক অন্তর্গত পরিবর্তনই পারে সংস্কৃতির পালাবদল ঘটাতে। আদতে সংস্কৃতি তো তাই, যা ব্যক্তির অজ্ঞাতেই সমষ্টির যাপিত জীবনের সমুদ্র মন্থন করে উঠে আসে ব্যক্তির আচারে অভ্যাসে প্রার্থনায় বিনোদনে। হয়তো এ কারণেই সংস্কৃতির আঁতুর ঘর সব সময় সামষ্টিক জীবনের আকর গ্রামাঞ্চলই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অন্তত তাই দেখি।
আমাদের উপরের আলোচনায় এই কথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের এই পৃথিবীতে সংস্কৃতি কিছুতেই কোনো অরাজনৈতিক নিরীহ ব্যাপার নয়। উপনিবেশোত্তর পৃথিবীতে তো সংস্কৃতি গভীর অর্থেই একটা রাজনৈতিক প্রপঞ্চ। উপনিবেশিত বিশ্বের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, সেখানে সংস্কৃতি সব সময়ই বিবেচিত হয়েছে রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি মজবুত করতে উপনিবেশক সব সময় চেষ্টা করেছে নেটিভ-সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে উপনিবেশকের নিজের সংস্কৃতি প্রতিস্থাপন করতে। উপনিবেশক গিলে খেতে চেয়েছে উপনিবেশিতের সংস্কৃতিকে; যাপন-কাঠামোকে।
যেহেতু সংস্কৃতি কোনো জমি নয় যে দখল দিলেই হয়ে যাবে। তাই উপনিবেশক উপনিবেশিতের ভেতর এমন একটা শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি করে যারা উপনিবেশকের সংস্কৃতির ধারক হয়ে ওঠে। তারা মননে-চৈতন্যে-রুচিতে উপনিবেশকের পক্ষের লোক হিসেবে তৈরি হয়। এক সময় তারাই ‘হেজিমনি’ তৈরি করে ঔপনিবেশিক শাসন ও সংস্কৃতিকে একটা পাকা ভিত্তি দেয়। এজন্য উপনিবেশিতের রাজনৈতিক সংগ্রামে বরাবরই সংস্কৃতি অন্যতম প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সংস্কৃতির ব্যবহার এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েই এখানে সংস্কৃতির রাজনৈতিকতা শেষ হয়ে যায়নি। বরং বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনোত্তর রাজনীতিও ওই সাংস্কৃতিক রাজনৈতিকতারই প্রকাশ। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক বিভাজন আসলে সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভাবনার পার্থক্যেরই ফল। এই দুই বিভাজনে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ ও ইতিহাসের উৎসমুখও আলাদা। সংস্কৃতি বিষয়ক এই দ্বিভাজিত ভাবনার সাথে কখনো ধর্ম ও ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যাপার মুখ্য হয়ে ওঠে আবার কখনো ধর্মের পরিচয়ের বাইরে গিয়ে নৃ-তাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যায়, বাংলাদেশের ওইসব সাংস্কৃতিক বিভাজন যতটা রাজনৈতিক ও কাগুজে ততটা বোধ করি বাস্তবের নয়। কারণ, বাস্তবে জনজীবনের পরিসরে মানুষ অত তেলে-জলের সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করে না। সেখানে সংস্কৃতির রং জীবনের মতোই ধূসর।
তবে হ্যাঁ, একটা সময় ছিল রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থা একটা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধরন-ধারণ নির্ধারণে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করত। বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও করে। তবে ভিন্নভাবে, ভিন্নমাত্রায়। কারণ ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। ব্যক্তি এখন রাষ্ট্রের সাথে বাঁধা থাকে। পুতুল যেমন সুতার সাথে বাঁধা থেকে নাচে- ব্যাপারটা অনেকটা তেমন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মাধ্যমে জনসমাজের চৈতন্যের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লাগলে ‘জাতীয় সংস্কৃতি’র বিভিন্ন জায়গায় তার প্রভাব পড়ে। ফলে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ক্রমে বদলাতে থাকে। এদিক থেকে সংস্কৃতি শুধু রাজনৈতিক ব্যাপার না, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারও বটে। বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, পাল শাসন, সেন শাসন ও মধ্যযুগের ছয়শ বছরের মুসলিম শাসন বাঙালির সংস্কৃতিতে ব্যাপক বদলের হাওয়া দিয়েছিল। ওইসব শাসনব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা শাসকশ্রেণির ধর্মের গভীর সম্পর্ক ছিল। ধর্ম ওইসব পর্বে বাঙালির সংস্কৃতিকে বদলে ফেলার ক্ষেত্রে বা নতুন নতুন উপাদানের সমাবেশের ক্ষেত্রে বড় নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। শাসকের ধর্ম বলে কথা! আবার ব্রিটিশ শাসনের আওতায়ও একটা নির্দিষ্ট জনপরিসরে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তনের দোলা লাগে। সেই প্রভাবের আওতা দিন দিন বেড়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার ফলে এই আওতা এখনো বেড়েই চলেছে বলেই মনে হয়। ফলে চিরায়ত সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও রূপ বদল ঘটে। তাই সংজ্ঞার্থগতভাবে সংস্কৃতি ব্যাপারটাই একটা প্রগতিশীল ব্যাপার। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন, রূপান্তর, নতুনকে আলিঙ্গন করাই সংস্কৃতির ভেতরগত স্বভাব। তবে হ্যাঁ সংস্কৃতির এও এক ধর্ম যে, এই গ্রহণ-বর্জন ও রূপান্তরের ভেতরেও আদি সংস্কৃতির একটা আভা আচ্ছন্ন করে রাখে রূপান্তরিত সংস্কৃতিকে।
সংস্কৃতির ওপর শুধু শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রভাব ফেলে তা নয়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবন একটা জাতির সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে পারে। যোগ করতে পারে নতুন নতুন উপাদান-উপকরণ। বর্তমান বিশ্ব মূলত তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব। মানুষের পক্ষে চাইলেও আর এসব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিনিয়ত মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, রুচি, অভ্যাস, বিনোদন, আকাঙ্ক্ষার বদল ঘটছে। এর সরল অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আসলে মানুষের সংস্কৃতিই বদলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে গত তিন দশকে তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে। ফলে জনপরিসরে মানুষের চিন্তা, খাদ্যাভ্যাস, যাপন, বিশ্বাস, রুচির ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি এত গভীরভাবে বাঙালির ঘরের ভেতরে হানা দিয়েছে যে, এর তোড়ে পুরোনোকে ধরে রাখাই মুশকিল হয়েছে। আসলে পুরোনোকে পুরোনো আকারে কখনো ধরে রাখা যায় না। বদল পৃথিবীর সবকিছুরই নিয়তি। বাঙালি সংস্কৃতিরও বদল ঘটছে। এই বদল ঘটছে ধীরে। খালি চোখে যেন দেখা যায় না এমন করে ঘটছে এই বদল। ক্রমে এইসব ছোট ছোট পরিবর্তনই পূর্বের সাংস্কৃতিক উপদানকে হটিয়ে জায়গা করে নেবে। তবে সংস্কৃতির স্বভাব সম্পর্কে যে কথা আগেই বলেছি তা আবারও বলা প্রয়োজন। কথাটি এই যে, পুরোনো সংস্কৃতি সব সময় তার জনগোষ্ঠীর মধ্যে চিহ্ন রেখে যায়। এই চিহ্নকেই কি আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নামে ডাকি!
যাহোক, এ কথা সত্য যে, বর্তমান যুগে আর আগের মতো উপনিবেশ স্থাপন করে সংস্কৃতি উৎখাতের রেওয়াজ নেই। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনীতি ও ক্ষমতার দেশের সংস্কৃতির দাপটে কম শক্তিশালী অর্থনীতি ও ক্ষমতার দেশগুলোর সংস্কৃতির থর হরিকম্প অবস্থা। দেশে দেশে এই-ই সংস্কৃতির নিয়তি। তবে, মনে রাখা দরকার, কখনোই বাইরের সাংস্কৃতিক উপাদান অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদানের জায়গায় হুবহু প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। বিদ্যমান সংস্কৃতির সাথে সংশ্লেষ ঘটায়। এবং এক নতুন রূপের সংস্কৃতি চালু হয়। ফলে বাঙালি সংস্কৃতিই শুধু সংকর ও স্থিতিস্থাপক- এই কথাটি পুনর্ভাবনার দাবি রাখে। বাইরের পৃথিবীর সাথে যুক্ত হয়েছে, বা শাসিত হয়েছে, পৃথিবীর এমন যেকোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিই সংকর ও স্থিতিস্থাপক। ফলে বাঙালির সংকর সংস্কৃতি নিয়ে আলাদাভাবে শ্লাঘার কিছু আছে বলে মনে করি না। এই শ্লাঘা একটি জাতীয়তাবাদী মিথ বলেই মনে হয়।
দুই
আগেই বলেছি সংস্কৃতি মানে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাধারণ (Common) প্রবণতার সমষ্টি। তাই কেবল খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মাচার, বিনোদন নয়- বরং মানুষের আচার-আচরণও এর অংশ। একটা জনগোষ্ঠী বিচিত্র পরিসরে পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করে তাও ওই জনগোষ্ঠীর আচরণ-সংস্কৃতির অংশ। যেমন, বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী কাউকে ভক্তি নিবেদন করতে হলে অনেক সময় ছয় অঙ্গ ভূমিতে লুন্ঠিত করে প্রণাম করে। এটাকে বলা হয় ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এটি ওই জনগোষ্ঠীর একটা আচরণ-সংস্কৃতিই বটে। দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষেরা কারো সাথে দেখা হলে নিজের হাত বুকে চেপে ধরে মাথা নিচু করে কুশল জিজ্ঞাসা করে। এটি ওই দেশের জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ আচরণ-সংস্কৃতির অংশ। বাংলাদেশে যেমন সালাম বা নমস্কার বা আদাব প্রদানপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করা হয়। কখনো কখনো বুকে বুক মেলানো হয়। এটাই বাংলার এক শ্রেণির মানুষের আচরণ-সংস্কৃতির একটা ধরন। এভাবেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে থাকে। আচরণের এই বিভিন্ন ধরনই বাঙালি জনগোষ্ঠীর আচরণ-সংস্কৃতির অংশ।
মানুষই সংস্কৃতির প্রধান কুশীলব। এই মানুষ অবিমিশ্র নয়; একটি মিশ্র প্রপঞ্চ। তার দুই সত্তা; ভালো আর মন্দ। ফলে মানুষের আচরণকেও মানুষই দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছে। ভালো আচরণ ও মন্দ আচরণ। একটা জাতির একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কীভাবে গ্রহণ করে তারও একটা সাধারণ (Common) ধরন থাকে বলে ধরে নেয়া হয়। মানুষের সাথে মানুষের আচরণের এই দিকটা ধরে অনেক সময় একটি জাতির ‘ভব্যতার’ মাত্রাও নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রায়ই শোনা যায়, ‘অমুক দেশের মানুষ যেকোনো মানুষকে সহজেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। সবার সাথে সুন্দর-শোভন আচরণ করে। হাসিমুখে কথা বলে। জাতি হিসেবে তারা খুবই ভদ্র।’ মানুষের সাথে মানুষের করা এই আন্তরিক ও ‘সুন্দর-শোভন’ আচরণকেই বাংলায় সম্ভবত ‘সদাচার’ বলা হয়।
‘সৎ’ ও ‘আচার’ শব্দযোগে সমাসবদ্ধ হয়ে গঠিত হয়েছে ‘সদাচার’ শব্দটি। এর সাধারণ অর্থ ‘ভালো ব্যবহার’। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধান বলছে- সদাচারের অর্থ ‘সদ্ব্যবহার’; ‘সাধু আচরণ’। কিন্তু বাংলাভাষায় শব্দটি ব্যবহারের সাথে কখনো কখনো ধর্ম যুক্ত হয়ে যায়। এজন্য ওই অভিধান বলছে, শব্দটির অন্য একটি অর্থ ‘ধর্মসম্মত’। যেমন ‘সদাচার অনুষ্ঠান’। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বাখানে না গিয়েও বলা, ‘মানুষের ধর্মের’ পক্ষে যা উচিত এমন আচরণ করার নামই ‘সদাচার’। ‘মানুষের ধর্ম’ বলতে বোঝাচ্ছি, মানুষ হিসেবে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে যে-আচরণ আশা তাকেই।
অবশ্যই মনে রাখা দরকার, মানুষের ধারণা পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এই ধারণা যেখানে যেমনভাবে নির্মিত হয়েছে সদাচারের ধারণাও সেখানে তেমন। যে-জাতির মধ্যে মানবিক মর্যাদার বোধ নিজস্ব প্রগতির ধারায় গভীরভাবে বিকশিত হয়েছে সেখানে সদাচারের ধারণা একরকম। আর যেখানে হয়নি সেখানে অন্যরকম। ফলে সদাচারেরও একটা ভূগোলগত ব্যাপার আছে। শুধু তাই নয়, এরও আছে প্রয়োগকালীন ইতর-ভদ্রতার ব্যাপার। আছে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির ভেদাভেদ। সদাচরেরও উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভেদ আছে। সাদা-কালোর ব্যপার-স্যাপার তো আছেই। কে, কার সাথে, কখন, কতটুকু সদাচার করে সে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা বটে। কিন্তু আমরা এখানে সদাচারকে সাধারণভাবে ‘ভালো আচার’ হিসেবেই বিবেচনা করছি।
আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি, সদাচারের ধারণা একটা জাতির বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার নিজের মতো করে নির্মিত হয়। বাইরের কোনো এক জাতির অর্জিত সদাচার কখনো অন্য কোনো জাতি আয়ত্ত করতে পারে না। বাঙালি যদি ভেতর থেকে সদাচারী না হয়ে ওঠে তবে তার পক্ষে- ইউরোপের সদাচারই (Etiquette) বলি আর ধর্মের সদাচারই বলি- কিছুতেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার কারণে মনে করা হয়, সদাচারও সংস্কৃতির মতো বাইরের জিনিস। মনে করা হয়, এটা ব্যক্তিক পর্যায়ে চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু আসলে তা যায় না। ব্যক্তি কসরৎ করে বাইরের সদাচারের যতটুকু আয়ত্ত করে সেই আচরণকে জাতীয় সংস্কৃতি বলা হয় না। সদাচার আসলে সংস্কৃতির অংশ আবার সংস্কৃতিরই একটা বাইপ্রোডাক্ট। সদাচার সংস্কৃতিসমুদ্রমথিত অমৃতের নাম। এটা বাইরের আলগা কোনো বিষয় নয়।
কিন্তু আমাদের দেশে সদাচারের কান্ধে আদর্শের বোঝা আরোপ করা হয়ে থাকে। এ কারণে এখানে সদাচারী হওয়ার কসরতের কথা বারবার বলা হয়। প্রায়ই বলা হয়, পশ্চিমা দেশের মতো আমাদের সদাচারী হতে হবে। বা কখনো কখনো ধর্মের দোহাই পাড়া হয়। কিন্তু এসব করে কখনোই সদাচার আয়ত্ত করা যায় না। মানুষ স্বভাবতই অধর্মচারী; কদাচারী। তাকে কসরত করেই সদাচারী হতে হয়। কিন্তু এই কসরত অবিরাম চলতে থাকে নিজের সাথে নিজের। এই সংগ্রামে জয়ী মানুষই সদাচারী হয়। ব্যাপারটা অনেকটা ব্যক্তিগত সাধনার মতো। কিন্তু সদাচার যেহেতু সাংস্কৃতিক ব্যাপার সেহেতু এটাকে একটা জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে ব্যক্তির সদাচার এখানে কোনো ব্যাপার না। সমষ্টির সদাচার গুরুত্বপূর্ণ। এই সামষ্টিক সচাচার দিয়েই একটি জাতিকে চিহ্নিত করা যায়। সমষ্টির মধ্যে সদাচারের সংস্কৃতি তখনই দেখা যায় যখন একটি জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয়ভাবে বা জাতিগতভাবে একটা সদাচারী মনোভঙ্গি অর্জন করে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি সদাচার গুণটি অর্জনের চেয়ে অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। ফলে, সদাচারও সংস্কৃতির মতোই বাইরে থেকে আসা বিষয় বলে এখানে কীর্তিত ও চর্চিত হয়। এটাও এক ধরনের ঔপনিবেশিক ব্যাধিই বটে। কোনো এক ধরনের জাতীয় জাগরণের ভেতর দিয়েই শুধু নিজস্ব সদাচারী সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। নতুবা এটি কাগুজে ফুলের মতো শুধু শোভা বিলাবে, সুগন্ধ ছড়াবে না।
বাংলাদেশের শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি দ্বিভাজিত। এখানকার সমাজ, রাষ্ট্র আর চিন্তার মধ্যে সংলাপের জন্য স্পেস কম। ফলে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ঘৃণা। দ্বিভাজিত দুই প্রান্ত পরস্পরের জন্য পর্যাপ্ত ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতা জমিয়ে রাখে চেতনায়, মনে, মননে ও জিহ্বায়। এই ধরনের সমাজে সদাচারের সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। একারণে- বিশেষত সরকারি দফতরগুলোতে বা প্রশাসনে- সম্প্রতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ‘সদাচার’ শব্দটি শুনতে ভালো লাগলেও এটি যে আরোপণ ও বাইরের ঠাঁট তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সদাচারের ব্যাপারটা তো ঘোষণা করার কোনো বিষয় না। এটি একটি জাতির ‘ভব্যতা’র মাপকাঠি। তবে হ্যাঁ, এই ধরনের ঘোষিত ও আদর্শিক চর্চারও হয়ত আলাদা একটা গুরুত্ব আছে।
তিন
একটি জাতিকে চিহ্নায়নের সাধারণ (Common) সূত্রগুলো নিহিত থাকে সংস্কৃতির মধ্যে। কারণ আগেই বলেছি, সংস্কৃতির সাথে নির্দিষ্ট ভূগোল ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যেমন, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীকে কেউ যদি বিশেষভাবে শনাক্ত করতে চায় তবে তা বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য দিয়ে শনাক্ত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা চোখ বন্ধ করে বলে দিই যে, এই জনগোষ্ঠীর বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ রীতি আছে, ধর্মচর্চার আছে এক বিশেষ ধরন। খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও বাঙালির বেশ কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ে। জারি-সারি-বাউল-দেহাতি-বিচ্ছেদি-রাখালি-মুর্শিদি গান এই জনগোষ্ঠীর বিনোদন সংস্কৃতিকে একটা বিশেষত্ব দান করেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীকেন্দ্রিক কিছু স্বাত্রন্ত্র্যসূচক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’ কথাটার উৎস হয়ত এখানেই। নৌকা বাইচ ও সেই কেন্দ্রিক গানের মধ্যে, পালতোলা নৌকায় মাঝির ভাটিয়ালি টানের ভেতর, দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথে গাড়িয়ালের ভাওয়াইয়ার বেদনাবিধুর সুরের মধ্যেও এই জনগোষ্ঠীর মুখাবয়ব মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রমকেন্দ্রিক নানা লোকগানও এই জাতির চিহ্নায়নের অন্যতম উৎস। পহেলা বৈশাখ ও এই কেন্দ্রিক আড়ং-উৎসব বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যা-ই আলোচিত হোক না কেন, বাংলাদেশের জনসমাজের পরিসরে একটা যথার্থ অসাম্প্রদায়িক যাপনের চিত্র আছে। এই যাপনের ধরনটি বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপরে বর্ণিত সব সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণের উপর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যকেও সেঁটে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।
তবে বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিক চিহ্নিত করার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি এই জনগোষ্ঠীর প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এগুলোর সাধারণীকরণ করা মুশকিল। কারণ, সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যাবে না। এগুলোরও একটা একটা আঞ্চলিক চেহারা আছে। শুধু তাই নয়, আমরা যখন বাংলার পহেলা বৈশাখ উদ্যাপনের কথা বলি এবং সেই কেন্দ্রিক আড়ং-উৎসবের কথা বলি, তখন মনে রাখতে হয় যে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নববর্ষ উদ্যাপনেরও আলাদা সংস্কৃতি আছে। আবার নানা ধর্মের রঙে রঙিন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপার তো আছেই।
বাংলাদেশের বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের অধিকাংশই চিহ্নায়কই গ্রামকেন্দ্রিক। এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির চিহ্নসূত্রগুলি জনপরিসরেই আকরিত হয়ে আছে। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতি মূলত একটা স্মৃতির ব্যাপার। বইয়ের পঠন-পাঠনের ব্যাপার। এবং অধিকাংশ সময় এই শ্রেণিটির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সূত্রগুলি উঠে আসে ইতিহাসের পৃষ্ঠার ভেতর দিয়ে। এ কারণে তা তার অস্তিত্ব ও যাপনের অংশ না হয়ে আলগা বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। এ জন্য সে বিতর্ক করে হয়রান হয়ে যায় যে, চলমান সংস্কৃতির এবং সংস্কৃতি বিষয়ক আলাপ আলোচনার মধ্যে কতটুকু তার আর কতটুকু তার নয়। এইসব আলোচনা ও বাদ-বিসম্বাদের কেন্দ্রে ধর্ম আর ইতিহাস যতটা থাকে যাপিত জীবন ততটা নয়। কিন্তু সংস্কৃতি তো যাপিত জীবনেরই উপজাত। যাপিত জীবনকে সংস্কৃতির প্রধান পরিচায়ক ধরলে আমরা দেখব, যাপনের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু তবু এই পরিবর্তনের গভীর তলে ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলে চলেছে আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ। আমরা চাইলেও তাকে নেভাতে পারি না এবং পারবও না।

কুদরত-ই-হুদা। প্রাবন্ধিক ও গবেষক। জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৮; বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙা উপজেলায়। সরকারি কলেজে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘ডিসেমিনেশন অফ নিউ কারিকুলাম স্কিম’-এ উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার [২০১৩], জসীমউদ্দীন [২০১৮], জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ : বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা [২০২২]। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বাংলা একাডেমি পত্রিকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা-জার্নালের সংখ্যা বিশের অধিক। গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছেন ‘মহাকবি মধুসূদন পদক-২০২৩’।