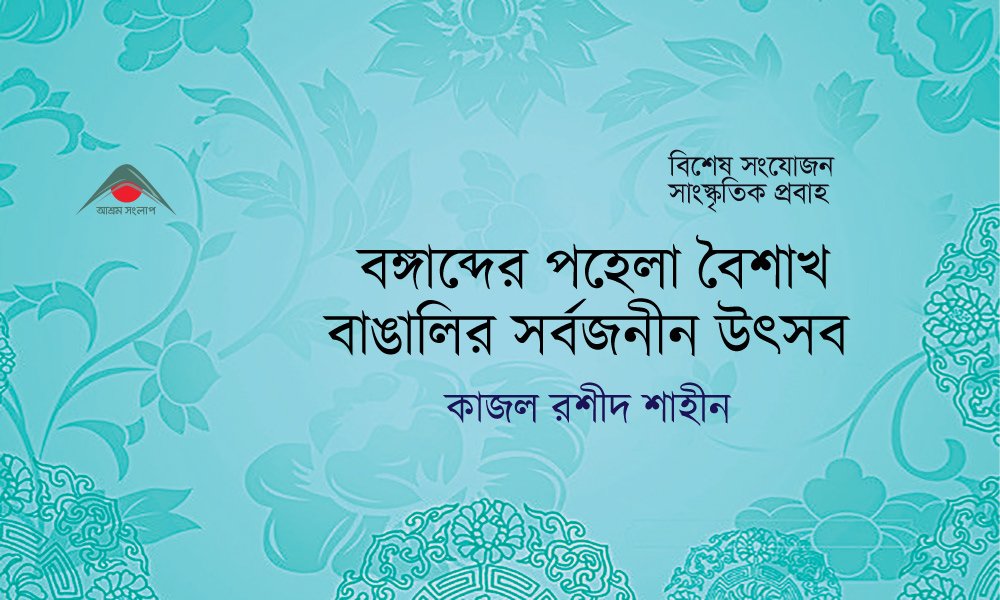বাঙালি জীবনে নববর্ষ আসে সর্বজনীন উৎসবের বিপুল সম্ভার নিয়ে। নতুন বছরের প্রথম দিন এবং বিদায়ী বছরের শেষদিনকে ঘিরে নানা ধরণের আয়োজন ছুঁয়ে যায় সকল বাঙালিকেই। বিশেষত পহেলা বৈশাখের আয়োজন বাঙালির সর্বস্তরের জনজীবনকেই রাঙায়িত করে নানানভাবে। বাঙালির ঘরে, জনজীবনে এবং আর্থ সামাজিক সংস্কৃতিতে এরকম উৎসব দ্বিতীয়টি নেই। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের যেমন এই উৎসবের সঙ্গে থাকে গভীর যোগসূত্রতা, তেমনই সকল সম্প্রদায়ের, জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরাও শামিল হন এখানে। সকল উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখের উৎসবের স্বাতন্ত্রিকতা ও সবিশেষ তাৎপর্য হল সকলেই এখানে নিজেদের মতো করে অর্থবোধক প্রাপ্তির ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রত্যয় খুঁজে পান।
পহেলা বৈশাখের যে উৎসব তার আতুড়ঘর, সৃষ্টির ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদে। নববর্ষ অর্থাৎ নতুন বছর, একেবারে নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় নতুন বঙ্গাব্দর জন্ম মোগল বাদশাহ আকবরের দরবারে। আকবরই এই সনের প্রবর্তক।
বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখিত হয়েছে, ‘কৃষিকাজের সুবিধার্থেই মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন এবং তা কার্যকর হয় তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে (৫ নভেম্বর ১৫৫৬)।’ প্রধানত কৃষকদের খাজনাপাতি দেওয়ার সুবিধার্থে এই সনের প্রবর্তনকরা হয়। এ কারণে এই সনের আরেক নাম ‘ফসলি সন’। প্রথমে এটিই প্রচলিত ছিল, পরে এর পরিচিতি দাঁড়ায় বঙ্গাব্দ নামে, যা আজও কার্যকর রয়েছে।
চন্দ্রের নিয়মে প্রচলিত হিজরী সন ও সৌর নিয়মে প্রচলিত বাংলা সনের সঙ্গে সমন্বয় করে স্থানীয় মানুষের সুযোগ ও সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সনের প্রবর্তন করা হয়। এর আগে এই অঞ্চলের মানুষেরা ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকলেও বঙ্গাব্দ সন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে বৈশাখের প্রথম দিনের উৎসব তাদের জীবনের অন্যতম আনন্দঘন দিনে পরিণত হয়।
বৈশাখের এই উৎসবকে সর্বজনীন উৎসব বলা হয় এই কারণে যে এই উৎসবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে। বাঙালি জীবনের মৌলচেতনা হল অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করা। সেই চেতনা এখানে হাজার বছর ধরে প্রবহমান। এই সমাজের গড়নই হল এমন যে, এখানে সবাই যার যার মতো করে জীবনকে যাপন করতে পারে এবং নিজস্ব রীতিনীতি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মানুযায়ী আচার ও ধর্ম পালন করতে পারে। প্রশ্ন হল, এই সমাজের গড়ন একম কেন? এর কারণ হল এই সমাজ হল নদীবাহিত সমাজ। এই দেশ হল নদীমাতৃক দেশ। নদীমাতৃক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল, তার স্থিতি, গড়ন ও বিকাশের মধ্যে স্বতান্ত্রিকতা বিদ্যমান। বাঙালি বা পূর্বভারতের সমাজের ধরণটাই এরকম। আদি থেকে সে আলাদা ও সম্পূর্ণ নিজস্ব সত্তায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ কারণে এখানকার সমাজের সঙ্গে আমরা যদি উত্তর ভারতের সমাজের গড়ন ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে সহজেই এই পার্থক্যটা টের পাওয়া যাবে। উত্তর ভারত যতটা আর্য ও বিভাষী-বিজাতীয়দের দ্বারা প্রভাবিত পূর্বভারত মোটেই তেমনটা নয়। ফলে, পূর্বভারত তারা স্বতান্ত্রিকতা নিয়েই বিকশিত হয়েছে। তার এ স্বতান্ত্রিকতা কেবল মানুষে নয়, এর সমাজে, এর প্রকৃতিতে, এর পরিবেশে, এর জল-মাটি-হাওয়া-নদী নালায় বিরাজিত রয়েছে। এমনকি আবহাওয়া ও জলবায়ুগত দিকেও পূর্বভারত উত্তর ভারত কেবল আলাদা নয়, স্বাতন্ত্রমণ্ডিতও।
বর্তমানের বাংলাদেশ একদা যা ছিল পূর্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ভারতের প্রকটি প্রদেশ বা রাজ্য। এই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিবঙ্গ মিলে একদা ছিল বঙ্গ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। এই বঙ্গের অতীত জুড়ে রয়েছে ভাঙ্গাগড়ার আরো ইতিহাস। সংক্ষেপিত সাম্প্রতিক ইতিহাস অবশ্য এরকমই। এখানে প্রধানত দুই ধর্মের মানুষের বসবাস। এর বাইরে আরও কয়েকটি ধর্ম বিশেষ করে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং নৃতাত্বিক ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে। জাতিগতভাবে এরা বাঙালি হলেও ধর্মীয় দিক দিয়ে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে ধর্ম পালন করে। এখানকার রীতি ও নীতি হল, রাষ্ট্র-সমাজ সকলের, ধর্ম যার যার। এখানকার প্রধান দুই ধর্ম হল ইসলাম ও সনাতন ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রধান দুই উৎসব হল দুটি ঈদ, যা ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আযহা নামে সর্বজনে পরিচিত। অন্যদিকে, সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের রয়েছে নানান দেবদেবীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বণ। এসব উৎসবগুলো নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সীমায়িত থাকলেও এখানে চাইলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং কখনো কখনো এলাকা ও অঞ্চলভেদে অংশগ্রহণও করে থাকেন। এই যে একের উৎসবে অন্যের অংশগ্রহণ সেটাতে কোনো রকমের বাধার সৃষ্টি বা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপত্তি না ঘটলেও এই অংশগ্রহণে সকলের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি ঘটে না।
বঙ্গ অঞ্চলে এসবের বাইরে রয়েছে লোকধর্মকেন্দ্রিক কিছু উৎসব। যেসব অঞ্চলে লোকধর্মের প্রভাব বেশি সেখানে এই ধর্মের বৈশিষ্ট্যগত কারণে রয়েছে সকল ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ করার প্রবণতা। আবার পীরালী ব্রাক্ষ্মণদের অনুসারীরা হিন্দু মুসলমানসহ অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের নিজস্ব উৎসবসমূহে সকল ধর্মের লোকজনই অংশগ্রহণ করেন।
বাউলদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এঁরা যেহেতু ধর্ম ও জাত পাতের উর্ধ্বে থেকে নিজেদের জীবন ও কর্মকে ধারণ ও প্রবহমান করতে চান, এ কারণে তাদের আয়োজনে-উৎসবে সকল ধর্মের মানুষেরা অংশগ্রহণ করতে পারেন, এবং করেনও।
লক্ষ্যণীয়, এসবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করলেও সেটা যেমন বৃহত্তর সামজের প্রতিনিধিত্ব করে না, তেমনই বৃহত্তর সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণকেও নিশ্চিত করে না। কিন্তু পহেলা বৈশাখের উৎসবের ব্যতিক্রমীতা ও স্বতান্ত্রিকতা হল এই উৎসব সর্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে। বর্তমানের বাংলাদেশে এবং ভারত রাষ্ট্রের পশ্চিবঙ্গ রাজ্যে এই উৎসবের সৌন্দর্য হল এর সর্বজনীন রূপ। যার তুলনা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, তাবৎ পৃথিবীর কোথাও, কোন প্রান্তে রয়েছে কি না তা আজোবধি জানা যায়নি।
বঙ্গাব্দ সনের শুরু হয় প্রধানত কৃষকের সুবিধার্থে। কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজেদের জীবনের আর্থিক রোজনামচাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন এই সনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বণিকের স্বার্থ, বিশেষ করে খুচরো ও মধ্য পর্যায়ের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হিসাবের খাতা সংরক্ষণ ও কার্যকর রাখা হত এই সনের দিন তারিখ ও মাসের সঙ্গে মিলিয়ে। কারণ এভাবে হিসাব রাখার ফলে তাদের বছরের শেষে গিয়ে পুরো বছরের ব্যবসার দেনা পাওনার গতিপ্রকৃতির কী রূপ তা বুঝতে যেমন সুবিধা হত, তেমনি বছর শেষে গিয়ে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে নতুন বছরের হিসাবের খাতা খুলতে সুবিধা হত।
বাঙ্গালি ব্যবসায়ীদের জীবনে হালখাতার প্রচলন শুরু হয় এই সনের বিদায়ী মাসের শেষের কয়েকদিন ও আগমনী বর্ষের শুরুর কয়েকটা দিনকে ঘিরে এবং এর মধ্যে মুখ্য হয়ে দেখা দেয় পহেলা বৈশাখের দিনটা, যা বৈশাখী উৎসব হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত ও বিশেষভাবে নন্দিত। হালখাতাকে ঘিরে এই যে আয়োজন ও উৎসব এটা প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও এখানে সীমিত পরিসরে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে এবং বাস্তবিকই সেই ধরণের উপস্থিতি ঘটেও থাকে।
হালখাতা যে প্রথা বা উৎসব সেটা শুরু হয়, মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারী ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। বাঙালি সমাজে ব্যবসার গোড়াপত্তনও হয় অবশ্য এদের হাত ধরে। সনাতন ধর্মের অনুসারীরা প্রায় সারা বছরই নানান ধরণের উৎসবের রীতি মেনে চলেন। বার মাসে তের পার্বণের যে প্রবাদ বাক্য বাংলা ভাষায় জোরদারভাবে চালু রয়েছে তা মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারীদের পার্বন প্রথাকে কেন্দ্র করেই। এঁরাই যখন ব্যবসাকে আরও সহজ, ক্রেতা-বিক্রেতা বান্ধব, এবং স্বচ্ছ ও লাভজনক করার চেষ্টার নিমিত্তে হালখাতা সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ততা ঘটাল সেখানে ঈপ্সিত লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই সেটাকে উৎসবমুখর করে তুললো। এবং হালখাতা সংস্কৃতি রীতিমতো একটা অংশগ্রহণমূলক আনন্দদায়ক উৎসবে পরিণত হল।
এই উৎসবের কেন্দ্রে অর্থনীতির যোগসূত্রতা মূখ্য হিসেবে থাকলেও এর পরিপার্শকে এমনভাবে রাঙায়িত করা হল সেটা যেন অন্তরঙ্গে অর্থযোগ আর বহিরঙ্গে আনন্দযোগ হিসেবে সকলের জন্য উৎসবমুখর একটা উৎসবে পরিণত হয়, বাস্তবিকই হলও সেটাই। সনাতন ধর্মের ব্যবসায়ীদের দেখাদেখি মুসলিম ধর্মের অনুসারী ব্যবসায়ীরাও হালখাতাকেন্দ্রিক উৎসবকে সাঙ্গীকরণ করে নিল। এই সাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কিছু জিনিস কেবল সাঙ্গীকৃত অবস্থায় থাকল না, তার আত্তীকরণও ঘটল।
এভাবে নববঙ্গাব্দের মুখ্যত প্রথম দিনটা দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে হালখাতার রং ধরে উৎসবের আমেজ নিয়ে এল। অন্যদিকে, পহেলা বৈশাখের দিনটা কেবল খাজনা আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলেই এই দিনটাতে নানারকমের উৎসবেও মেতে উঠল। বাংলার সমাজ যেহেতু কৃষি প্রধান এবং এর অর্থনীতি আজও কৃষি নির্ভর। ফলে কৃষি সংশ্লিষ্ট রীতি নীতি ও উৎসব একক কোন বৃত্তে আটকে রইল না। বিশেষ কোন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সমাজ-গোষ্ঠীতে সীমায়িত না থেকে তা ছড়িয়ে পড়ল সকলের মাঝে। এখনও বাংলার ঘরে ঘরে সেই রীতি বহমান রয়েছে। এখনও পহেলা বৈশাখের দিন ধানের বীজ ছড়িয়ে কৃষকের বাড়ি আগমন ঘটে বরণের মধ্যে দিয়ে। উঠানে আগে থেকে রেখে দেওয়া হয় পানি। তাতে দেওয়া হয় কচি আম পাতা, দুর্বাঘাসসহ আরো নানা কিছু। উঠান লেপানো হয়। বাড়িতে আলাদা করে রান্নার আয়োজন থাকে। হালের গরুকে গোসল করানো হয়। ইত্যকার আয়োজনে পুরো দিন কেটে যায়।
আগ্রহোদ্দীপক বিষয় হল, পহেলা বৈশাখের আয়োজন এভাবে উৎসবের আমেজ ছড়াতে ছড়াতে এই অঞ্চলের, এই বঙ্গের, পূর্বভারতের, বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে প্রধান উৎসবে পরিগণিত হয়। লক্ষ্যণীয়, একদা যে উৎসব ছিল কেবল কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের, যে উৎসব ছিল কেবলই অর্থের কারবার করা ব্যবসায়ী সমাজ ও তার বান্ধববেষ্টিত ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই উৎসব নানা রূপে, নানা যোজন বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে সকলের উৎসব হয়ে উঠেছে। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এটাই একমাত্র উৎসব যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে। এমনকি যে বাউল সমাজের প্রচলিত রীতি নীতিকে সাঙ্গীকরণ না করে চলে নিজের মতো তিনিও এই উৎসবে শামিল হল তার গান নিয়ে, একতারার বাদনে মনের মানুষকে খোঁজার বাসনায়।
ধনী গরীব মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সকলেই এই উৎসবে শামিল হন, আনন্দকে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে। পহেলা বৈশাখের উৎসবের সঙ্গে সকলেরই যোগ হওয়ার সুযোগ ঘটে। কারণ এই উৎসবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। যখনই কোন উৎসবের সঙ্গে অর্থনীতির নানা প্রান্তের যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় তখনই সেই উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে, পহেলা বৈশাখের উৎসবের ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে। এই উৎসবে কেউ ক্রেতা হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন আবার কেউ বিক্রেতা হয়ে আনন্দ উদযাপনের অংশ হন।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরাও পহেলা বৈশাখের আনন্দোৎসব করেন। উনারাও নিজেদের মতো করে নিজেদের স্বাজাত্যবোধ বজায় রেখে উৎসবের রঙ ছড়ান। সেখানেও দেখা গেছে চমৎকার সব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। উনাদের অন্যান্য উৎসব নিজেদের মধ্যে বৃত্তবন্দী থাকলেও পহেলা বৈশাখের উৎসব তেমনটা নয়। বিদায়ী বর্ষের চৈত্রসংক্রান্তির দিন এবং নতুন বর্ষের প্রথম দিনকে ঘিরে পাবর্ত্য জেলাসমূহে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব ‘বৈসাবি’ উদযাপিত হয়। এর নামকরণ হয়েছে বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজু এই শব্দগুলোর আদ্যক্ষর থেকে। উল্লেখ্য, এ উৎসবকে চাকমারা বিজু, মারমারা সাংগ্রাই, ত্রিপুরারা বৈসুক বলে অভিহিত করেন। পুরো পার্বত্য এলাকায় এর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ‘বৈসাবি’ নামে।
পহেলা বৈশাখের সর্বজনীন রূপ নানানভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে সংহত এক অবস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এই সংহত রূপের প্রকাশ দেখতে পাই রাজধানী ঢাকার মঙ্গল শোভাযাত্রায়। প্রতিবছর মঙ্গল শোভাযাত্রার যে আয়োজন তাতে বাঙালির অসাম্প্রদায়িতক মননচর্যার চিত্রই উপস্থাপন করা হয়। এখানে নানা মোটিফে যা কিছু হাজির করা হয় তার সঙ্গে রয়েছে বাঙালির দীর্ঘদিনের সাহচর্য। এই সব মোটিফের ভেতর দিয়ে তার বিশ্বাসও উন্মীলিত হয়। সেই বিশ্বাসে ধর্মীয়বোধের চেতনা হাজির যেমন থাকতে পারে, তেমনই থাকতে পারে লোকধর্মের অন্তরঙ্গ উপস্থিতিও। এ কারণে মঙ্গল শোভাযাত্রা মূলত বাঙ্গালি হাজার বছরের পথচলার সম্মিলিত সহাবস্থানের প্রতীকী উপস্থাপনা। যার মধ্যে আমরা অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ যেমন রচনা করি তেমনি আমাদের প্রত্যয়ের অনুষঙ্গগুলোকেও হাজির রাখি। বাঙ্গালি সত্তার চিরন্তন রূপের যে আধার ও আধেয় সর্বৈবরূপের প্রকাশ ঘটে নব বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে।
রমনার বটমূলে ১৩৭২ বঙ্গাব্দ থেকে পহেলা বৈশাখের উৎসবের আয়োজন করে আসছে ছায়ানট। গানে গানে তাদের যে আহবান, তা মূলত বাঙ্গালীর প্রার্থনা সঙ্গীত বিশেষ। ‘এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।/ তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,/ বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।।/ যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,/ অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।।/ মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।/ রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,/ আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।/ মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক।।’ এ গানের ভেতর দিয়ে বাঙালি প্রতি বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে নতুন করে বাঁচতে শেখার পুণ্যমন্ত্রই উচ্চারণ করে।
রাজধানী ঢাকাতেই নয় শুধু, দেশের প্রায় সকল বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে বঙ্গাব্দ নববর্ষের প্রথম দিনে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উৎসবের আয়োজন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় এই উৎসবের আয়োজন এত বেশি বর্ণাঢ্য হয়ে থাকে যে তা দেখার জন্য দেশের ভেতরের এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায় তো যায়ই দেশের বাইরে থেকেও অনেকেই আসেন। প্রবাসী বাঙ্গালিদের অনেকেই দেশে আসার ক্ষেত্রে পহেলা বৈশাখের উৎসবে যেন শামিল হতে পারেন, নতুন প্রজন্মকে যেন পহেলা বৈশাখের বর্ণময় উৎসবের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে পারেন সেদিকেও বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন। কেননা, এই উৎসবকে ঘিরে গ্রামবাংলা ও নগর জীবন যেভাবে সাজ সাজ রবে সেজে ওঠেন তার কোনো তুলনা আক্ষরিক অর্থেই হয় না।
বাংলার ঘরে ঘরে এই উৎসব যেন প্রাণের বান ডেকে আনে। বাঙ্গালি জীবনে বিবিধ সমস্যায় আকীর্ণ। এখানে আনন্দ যেমন আছে তেমন দুঃখ আছে। এর প্রকৃতিই এমন কখনও বন্ধুর কখনও সৌহার্দ্যপূর্ণ। বাঙ্গালি এর মধ্যে দিয়েই রপ্ত করেছে বাঁচতে শেখার মন্ত্র। এবং সেই মন্ত্রকে কীভাবে নিজের জীবনের চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করেছেন, তার অনুপম দৃষ্টান্ত হল পহেলা বৈশাখের উৎসব।
এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নদী জেগে ওঠে নৌকাবাইচকে ঘিরে। গ্রামের বটতলায় প্রাণের জাগরণ ঘটে নাগরদোলার মতো নানা আয়োজনের উপস্থিতিতে। হাটে মাঠে ঘাটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও জারি সারি ভাটিয়ালি গান থেকে শুরু করে হাল আমলের গানেরও তুফান ওঠে। রকমারি পিঠার মনোহরা গন্ধে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয় থেকে লোকালয়ে। মোরগ লড়াই যেমন হয়, তেমনি ষাঁড়ের দৌড়- ঘোড়া দৌড়ের আয়োজন হয়। বেদে বেদেনিরা সাপের খেলার আর গানের ঝাঁপি খুলে বসে। চরকি ওড়ে, ঘুড়ির মেলা বসে, নানা রংয়ের পুতুলের উপস্থিতির সঙ্গে থাকে পুতুল নাচের আয়োজনও। বাঁশিবিক্রেতা বাঁশি বাজিয়ে মুখর করে তোলা মেলা প্রাঙ্গণ। এই উৎসবকে ঘিরে যাত্রাপালার আয়োজনও করা হয়। সেখানে রাধা কৃষ্ণের বিরহে যেমন আকুল হয় মানুষের মন তেমনি লাইলি মজনুর বিরহগাঁথাও তাদেরক ব্যথিত করে। বাংলার কত রূপ যে আছে, যে রূপের তালাশ করে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল, জীবনানন্দ। সেই রূপের সকল আধার যেন হাজির হয় বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখের উৎসবে। ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর’। জীবনানন্দ দাশের অমোঘ এই উচ্চারণের সত্যতা কেবল বাংলার প্রকৃতিকে মেলে না, তার উৎসব-পার্বণেও হাজির হয়।
বাঙ্গালীর গণমাধ্যমেও বৈশাখ, নববর্ষ, চৈত্রসংক্রান্ত্রি, বিদায়ী বর্ষও নানানভাবে হাজির হয়। এসবকে ঘিরে নানা রকমের আয়োজন থাকে। কেবল বিনোদনের জায়গা থেকে নয়, ফিচার বা লাইফস্টাইলের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর থেকেও সৃজন-মননশীল দৃষ্টিকোণ থেকেও এর গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়। যার সর্বৈব প্রকাশ ঘটে পহেলা বৈশাখের ক্রোড়পত্র ও বিশেষ আয়োজনসমূহকে ঘিরে।
একটা উৎসব কীভাবে সর্বজনীন হয়ে উঠে। কীভাবে তার প্রসার ঘটতে পারে, তার নজির জারি রয়েছে বাঙ্গালির পহেলা বৈশাখের উৎসবে। পৃথিবীতে একটা উৎসবের এরকম ব্যাপকতা বিস্তার গ্রহণযোগ্যতা ও মান্যতা বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই।

ড. কাজল রশীদ শাহীন। সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও গবেষক। তিনি মনে করেন, ১৯০৫ থেকে ১৯৭১ সময়পর্বে আজকের বাংলাদেশ ভূগোলে ‘বাংলাদেশের নবজাগরণ’ সংঘটিত হয়। যার উন্মেষ ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭-এ, বিকাশ ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৬-তে, নির্মাণ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১-এ। ‘বাংলাদেশের নবজাগরণ ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ: অন্বেষা-অবলোকন-তত্ত্ব’ উনার এ সম্পর্কিত চিন্তা ও যুক্তির প্রস্তাবন বই।
গবেষণা করেছেন ‘বাংলাদেশবাদ’ নিয়ে। যেখানে তিনি হাজির করেছেন এই সিদ্ধান্ত, নতুন আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ নির্মাণ ‘বাংলাদেশবাদ’ প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়।
জন্মেছেন বাংলাদেশের নবজাগরণ সংঘটিত হওয়ার চার বছর পর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগরে। সরকার উমমত আলী ও খোদেজা খানমের আত্মজ, আট ভাইবোনের মধে ষষ্ঠ।
পড়াশোনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। পিএইচ.ডি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবুল আহসান চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ‘আবু হেনা মোস্তফা কামালকে নিয়ে।
স্বপ্ন- জাতীয় পর্যায়ে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা।
প্রথম বই ‘একবার বিদায় দে মা’ ক্ষুদিরামকে নিয়ে বিশেষ চিত্রনাট্য। দ্বিতীয় বই ‘এই আমি কোথাও নেই’ কবিতার। তৃতীয় বই ‘বাংলাদেশের নবজাগরণ ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ : অন্বেষা-অবলোকন-তত্ত্ব’ প্রবন্ধ-গবেষণা। চতুর্থ বই ‘প্রশ্নমঙ্গল : বুদ্ধিজীবীর অ আ ক খ’ প্রবন্ধ-সাহিত্য।
সাংবাদিকতা করেছেন ‘দৈনিক রূপালী’, ‘সংবাদ’, ‘প্রথম আলো’, ‘আলোকিত বাংলাদেশ’সহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে। ছিলেন দৈনিক বাংলা’র নির্বাহী সম্পাদক ও ‘খোলা কাগজ’ এর সম্পাদক।