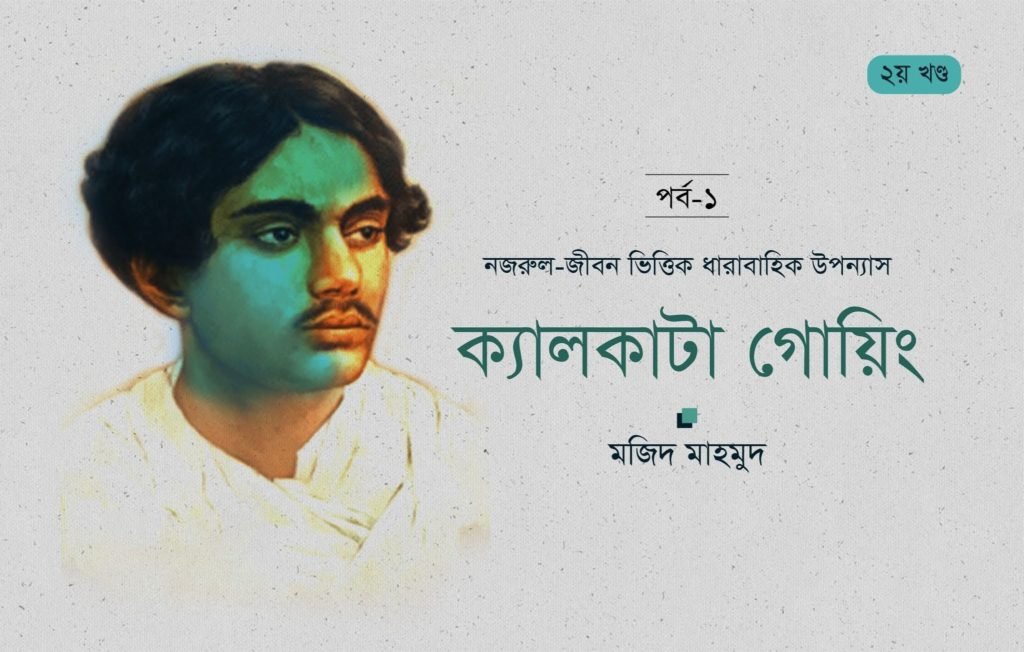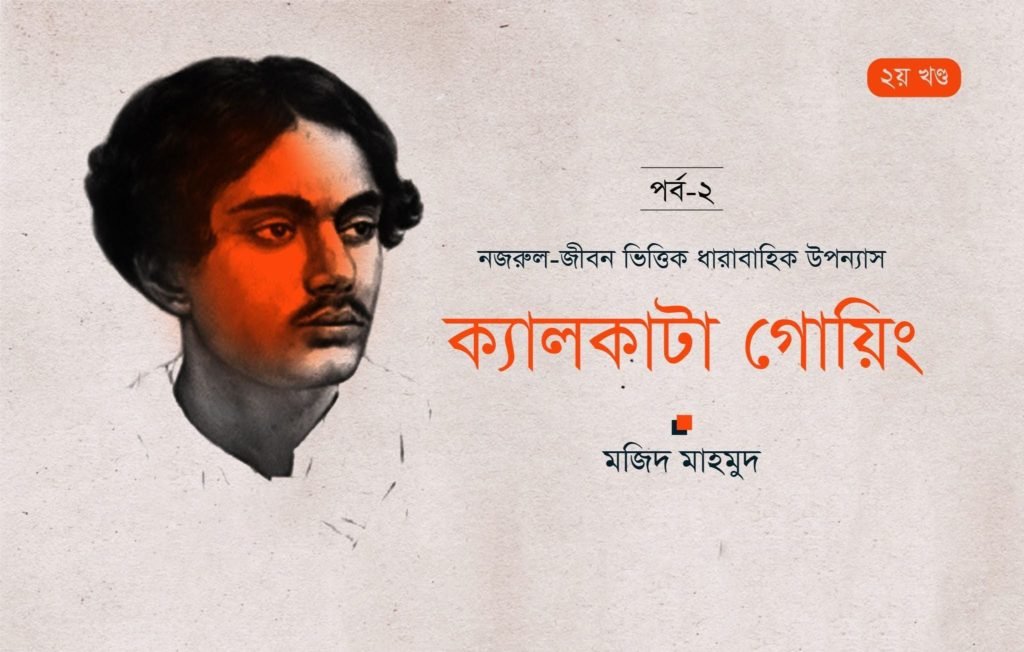পর্ব-৪
একদিকে গায়ে-গতরে বেড়ে উঠছিলাম, শরীরে ছিল অসুরের শক্তি, অন্যদিকে মন-মেজাজের স্থিরতা ছিল না, আমার দুষ্টুমিতে সমবয়সীরা—এমনকি গ্রামের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। মক্তব থেকে প্রাথমিক পাস করে সেখানেই শিক্ষকতার কাজ করছিলাম। এ কাজ আমার জন্য নতুন নয়, সর্দার-পড়ো হিসাবে অভিজ্ঞতা ছিল, এখন কিছু টাকা পয়সাও পাচ্ছি, খুব সামান্য, অনিয়মিত—মাসে পাঁচ টাকা। প্রবীণ শিক্ষক পেতেন দশ টাকা।
মক্তবের ফারসি হুজুর বজলে আহমেদ বলতেন, জানিস দুখু ব্রিটিশ আসার আগে এদেশে সবার জন্য শিক্ষা চালু ছিল। প্রতি চারশ জনের জন্য ছিল একটি স্কুল। ভাবিস নি এটা আমি বানিয়ে বলছি, এটা সাহেবদের কথা। অ্যাডামসন সাহেবকে দিয়ে বাংলা-বিহার অঞ্চলে কোম্পানি বাহাদুর জরিপ কাজ করেছিল—উনিশ’শ পঁয়ত্রিশ সালে, একবার নয় তিন তিন বার জরিপের ফল। তখন এ দেশে এক লক্ষ স্কুল ছিল, জনসংখ্যার তুলনায় প্রতি চার’শ জনে একটি বিদ্যালয়। ভাবা যায়!
সেগুলো কই গেল, মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে কিভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল হুজুর! কিভাবে সম্ভব, মোগল নবাবরা এত স্কুল কিভাবে গড়ে তুলেছিল? নবাবদের হাতে কি জাদুর কাঠি ছিল!
কেন, আমাদের এই মক্তবের কথাই ধর না। এটা হলো একটা পদ্ধতি, নবাবরা এদেশে বিদ্যালয়কে স্বয়ং-সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলেছিল। জনগণের শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের হাতে ছিল। যেখানে মক্তব গড়ে উঠত, টোল গড়ে উঠত—নবাব সেখানে আয়মা লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন। সেই আয় দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলতে পারে। ধনীরা তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুহাতে দান-খয়রাত করত। মুসলমানরা মনে করে এটি সদকায়ে জারিয়া, একবার কোনো ছাত্রকে শিক্ষার জ্ঞান দিতে পারলে আখেরাতে সে তার ফল পাবে। এসব বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণির ছাত্ররা নিম্ন ক্লাসে শিক্ষাদান করত, আলাদাভাবে বেশি শিক্ষকের প্রয়োজন হতো না। হিন্দুরাও ব্রাহ্মণ-সন্তানদের শিক্ষাকে পুণ্যকর্ম মনে করত।
মা চাইতেন লেখাপড়া শিখে আমি যেন পুলিশের দারোগা হই।
হুজুরের আক্ষেপ উসকে দেয়ার জন্য বলেছি, এটা কী ধরনের শিক্ষা? মসজিদে মন্দিরে একজন শিক্ষক কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বসে আছেন। পাটিতে বসে পড়াচ্ছেন, ব্যাস- একেই আপনি শিক্ষা বলবেন।
তোকে একটা কথা বলি দুখু, সেই পদ্ধতিটাও কি এখন চালু আছে! এমনকি ইংল্যান্ডেও সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা সম্ভব ছিল না তখন। কোম্পানির সাহেবরা জরিপ কালে এদেশে এত উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ডক্টর বেল সাহেব তার দেশে এই পদ্ধতি মনিটরিং নামে চালু করে—সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি হিসাবে। আজ দেখ মসজিদগুলো খালি পড়ে আছে, সকাল-বিকাল ছাত্রছাত্রীর কোলাহল সেখানে শোনা যায় না। মসজিদগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ করলে সরকারের অনেক অর্থ বেঁচে যেতে পারে।
কয়েক বছর আগে হান্টার সাহেবও তার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এই পদ্ধতির প্রতি সুপারিশ করেছিলেন। সরকার কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় করবে না, স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যক্তিবর্গের অধীনে তা পরিচালিত হবে। এখনো তো সারা দেশে একশটা স্কুলেও নেই যেখানে ব্রিটিশ সরকারের অবদান আছে। অবশ্য কার্জন সাহেব প্রাথমিক স্কুলগুলোতে খরচের অর্ধেকটা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। জানি না কবে আমরা পাব। অথচ একদিন এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের উপরে নির্ভরশীল ছিল না।
শিক্ষাদান যত মহৎকাজই হোক না কেন—আমার মন সে-কাজে আনন্দ পেত না, কেবল অস্থিরতা, কেবল ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়ার আহ্বান শুনতাম। সবখানে হতাশার ধ্বনি। সারাদিন মক্তবে, মসজিদে হাজী পালোয়ানের মাজারের কাজ করে রাতে বাড়িতে ফিরে এসেও ভালো লাগত না। জীবন অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি তখনো আমার কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার বয়স হয় নি। নতুন করে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য পয়সা ছিল না, চুরুলিয়া গ্রামে পড়ার মতো বিদ্যালয়ও ছিল না। ভাবছিলাম কিছু টাকা পয়সা হাতে এলে মাথরুন বা রানিগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি হব।
একদিন বজলে করীম চাচা বললেন, ‘দুখু, তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে, রাতে একবার দেখা করিস।’
এমনভাবে তিনি কথাগুলো বললেন, মনে হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু। বুঝলাম সংসারে আমার কিছু গুরুত্ব তৈরি হচ্ছে। বজলে চাচার প্রতি ছিল আমার ভারি আকর্ষণ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধাও ছিল। অনেকবার তার কাছে আমার গানের প্রশংসা শুনেছি। বাবা মারা যাওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে যদিও তার আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল, আমাদের খোঁজখবর একটু বেশিই নিতেন। পর্দার আড়াল থেকে মায়ের কাছে জানতে চাইতেন, ভাবি সাহেবা, কোনো কিছু লাগলে বলবেন। আমার প্রতিভার তারিফ করতেন। বলতেন, দুখু এখনই যে শের শায়েরি রচনা করে, দেখেন ও একদিন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির মতো নাম করা কবিয়াল হবে।
মা এই কবিয়াল হওয়া পছন্দ করতেন বলে মনে হতো না। বলতেন, মিয়া সাহেব থাক, ওকে আর আপনার মতো কবিয়াল বানাতে হবে না। কবিয়ালরা ভালো হয় না। আমি ওকে লেখাপড়া শেখাব।
করীম চাচা হাসতে হাসতে বলতেন, ভাবি সাহেবা, আমি কি লোক খারাপ?
না আপনি অনেক ভালো! সারাজীবন তো গান গেয়েই কাটিয়ে দিলেন। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবু আপনার মনের ভাব গেল না।
সেদিনকার মতো রাতে হাজী পালোয়ানের দরগার মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে, রাতের জন্য কয়েকটি আগরবাতি জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মা তখন রাতের খাবার পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বারান্দায় পাটি পেড়ে বড়ভাই ও কনিষ্ঠ আলী হোসেন আমার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করে। আলী হোসেনকেও মক্তবে ভর্তি করা হয়েছে, ওর অভিভাবকের স্থানে বাবার অনুপস্থিতিতে আমার নাম লেখা হয়েছে। আজ আমায় কিছুটা আগে বাড়িতে ফিরতে দেখে বললেন, দুখু যে আজ সবার আগে, কি ব্যাপার কোথাও যাবি নাকি?
মা বললেন, তোর চাচার সাথে অত মাখামাখি করবি না। কবিয়ালগিরি কোনো ভালো কাজ না। মক্তবের কাজ ছেড়ে দে, আগামীবার মাথরুন বা রানিগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি হ। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে তোর পড়তে খরচ লাগবে না, উপরি জলখাবার পাবি।
মা চাইতেন লেখাপড়া শিখে আমি যেন পুলিশের দারোগা হই। আমার এক দাদা নজীবুল্লাহ বিহারে পুলিশের দারোগা ছিলেন। তার কাছে থেকে বাবা লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। আকস্মিক মৃত্যুতে ছেদ পড়ে, তার লেখাপড়া খুব বেশি দূর এগোয় না। ঠিক মতো লেখাপড়া জানলে এ অবস্থা হতো না।
আমি কোনো মতো নাকে মুখে কিছু গুঁজে, বজলে চাচার বাড়িতে গেলাম। চাচা আমার জন্য আগে থেকেই বাইরের খানকাঘরে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে আগে থেকেই কয়েকজন উপস্থিত ছিল, অনেকে আমার চেনা, চাচার লেটোদলে গান করে। বজলে চাচার বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়, কাঁচাপাকা দাড়ি, চুল বাবড়ি করে ছাটা, দেহসৌষ্ঠব সুগঠিত। যখন ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় ছেলেবুড়ো সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে, বলে কাজীর ব্যাটা আজ কোনো আসর হবে না! করীম চাচা সৌখিন মানুষ, চাষবাসের সঙ্গে খুব একটা জড়িত ছিলেন না, তিনিও বাবার মতো জমি জমার দলিল লেখক হিসাবে কাজ করতেন।
বজলে চাচার একটি শখের লেটো গানের দল ছিল। এটি তার পেশা নয়, নেশা। নিজের কবিত্ব শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসাবে তিনি এই গানের দল করেছিলেন। আমি তার কাছে হারমোনিয়াম বাজানো শিখেছিলাম।
শীতের দিনে কিংবা ফসল উঠার পরে যখন হাতে খুব একটা কাজ থাকত না, তখন কবিগান, লেটোগান, যাত্রাপালায় অভিনয় করে, অভিনয় দেখে সময় কাটাত মানুষ। চাচার জানাশোনা দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। মুখে মুখে কবিতা বাঁধতে পারতেন, ফারসি উর্দু বয়াত বলতেন। মুখে মুখে গান বাঁধতেও পারতেন। তার নিজের লেখা একটি গান তিনি প্রায়ই গাইতেন—
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড় জবানে
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড় একিনে।’
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়েও তিনি গান লিখেছিলেন—
‘গেল নিশি, কালা কই এলো সই
ঝঙ্কারে কোকিল দেখ্ দেখ্ লো ঐ।’
বজলে চাচার কাছে প্রথম শুনেছিলাম অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কথা।
বলেছিলেন জানিস দুখু, এই ভারত একটি কুহুক-জাদুর দেশ। যারাই এখানে এসেছে তারাই এর প্রেমে পড়ে গেছে, তবে শাসনে নয় স্নেহে, প্রভুত্বে নয় বন্ধুত্বে যারা দেখেছে—তাদের কাছে এদেশের রূপ উন্মোচিত হয়েছে। এদেশ যত না দেখার, তার চেয়ে বেশি অনুভবের। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির নাম নিশ্চয় শুনেছিস? হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা এরাই আমাদের এই পথের গুরু।
চাচা বলতেন, তবে মুসলমান কবিয়ালদের রীতি কিছু আলাদা ছিল। তারা এ ক্ষেত্রে বটতলার পুঁথি সাহিত্যও রপ্ত করেছিল। কবি গরীবুল্লাহ, আমির হামজা রচিত পুঁথির রস তারা তাদের কবিগানে নিজেদের মতো পরিবেশন করত।
তারা যেমন দিয়েছে নিয়েছেও অনেক। এদেশে যেমন ইরান তুরান থেকে আসা মুসলমানের গল্প আছে, তেমন ইংরেজ ফিরিঙ্গিরও গল্প আছে। এখানে আসা সব পীর আউলিয়ার গল্পের যেমন মিল আছে, কিছু ইংরেজ ফিরিঙ্গির গল্পেরও মিল আছে। ফিরিঙ্গিরা এদেশটাকে মুসলমানদের মতোই ভালোবেসেছিল। তারা এদেশে এদেশি হিসাবে থাকতে চেয়েছিল। ইউরোপীয়দের মধ্যে তারাই এদেশে প্রথম, ইংরেজের কাছে মার খেয়ে ভারতকেই নিজের দেশ করে নিয়েছিল, ভারতীয় নারীদের বিয়ে করে এখানকার রক্ত ধারায় মিশে গিয়েছিল। কেবল অ্যান্টনি নয়, আধুনিকদের গুরু ডিরেজিও নিজেও একজন ফিরিঙ্গি, অ্যান্টনির মতো ডিরোজিও নিজেকে এ দেশকেই তার দেশ মনে করতেন। তিনিই ভারতকে মাদারল্যান্ড বলে কবিতা লিখেছিলেন।
বজলে চাচার কাছে ফিরিঙ্গি শব্দটি শুনে জানতে চেয়েছি, ফিরিঙ্গি কী?
বজলে চাচার জ্ঞান ছিল অগাধ, বলেছিলেন, পর্তুগিজ শব্দ ফ্রান্সেস থেকে ফিরিঙ্গি শব্দের উদ্ভব হয়েছিল। এক সময়ে সব ইউরোপীয়কেই এদেশের লোক ফিরিঙ্গি বলত। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ও ভারতীয় মিশ্রণজাত ইউরেশিয়ান ও খ্রিষ্টানদের বোঝানো হতো। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে শব্দটি সম্মানসূচক হলেও পরে তুচ্ছার্থে ব্যবহার হতে থাকে।
অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি জন্মেছিলেন খ্রিষ্টানের ঘরে। হিন্দু ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তার পরিবারে ছিল লবণের ব্যবসা, অনেক পয়সা করেছিলেন। নিজের ধর্ম ত্যাগ না করেই তিনি বাংলা শিখেছিলেন। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থর পাঠ করে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, বউবাজারের কালী মন্দির তার করা—যেটি এখন ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি নামে পরিচিত—এই মন্দিরে তিনি সর্বধর্মের সমন্বয়ের কথা বলতেন। তার আসল নাম হেনসম্যান অ্যান্টনি। অ্যান্টনি কবিয়াল বা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বলেই এখন সমধিক পরিচিত।
দুই পক্ষের আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ শেষে দুই মহাকবিয়ালের মহামিলন। জয়ের পরেও অ্যান্টনি ভোলার কাছে হার মেনে নেয়, গুরু বলে সম্বোধন করে।
করিম চাচার এমনভাবে অভিনয় করে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ও ভোলা ময়রার কবিগানের বর্নণা দিতেন, আমার মন তখন কোলকাতার ফরাসডাঙ্গায় ছুটে যেত। দেখতাম বিশাল এক বৈঠকখানায় ফরাসের উপরে এলাকার গণ্যমান্য লোকজন বসে আছে, জমিদার বাবু আছে, অন্দরমহল থেকে কখনো মহিলারাও দেখার সুযোগ পেত, তবে ঝুমুর-খেউড় গানে অনেক অশ্লীল উপস্থাপনা থাকায় পুরুষরা তাদের এড়িয়ে চলত। সামনের দিকের এক কোনায় অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি তার দলবল নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ভোলা ময়রার চাপান শুনছেন। ভোলা ময়রা তাকে আক্রমণ করে বলছে—
‘এ ব্যাটা পুজোর বাড়ি ভোজোর লোভে নাচতে এসেছে।
ব্যাটা সাহেব ছিল, ছিল ভালো হলো বাঙালি
এখন কবির দলে এসে মিলে পেটের কাঙালি।
জন্ম যেমন যার কর্ম তেমন তার
ব্যাটার ভেড়ের ভেড়ে নেমক ছেড়ে কবির ব্যবসা ধরেছে।’
অ্যান্টনির লবণের ব্যবসা ছিল। জবাবে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নেচে নেছে জবাব দিচ্ছেন—
‘যে শক্তি হতে উৎপত্তি
সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ?
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ।
সমুদ্র-মন্থনকালে বিষ পান করেছিলে
তখন ডেকেছিলে দুর্গা দুর্গা বলে
রক্ষা কর আপনি, সেই দিন
সেই দিন কি ভুলে তাহারে বলেছিলে জননী৷’
ভোলা ময়রার উত্তর—
‘আমি সে ভোলানাথ নই রে সে ভোলানাথ নই!
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা বাগবাজারে রই
চিন্তামণির চরণ চিন্তে ভাজনা খোলায় ভাজি খই।
সবাই পূজে ভোলার চরণ আমার চরণ পূজে কই?
অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি—
‘প্রশ্নটা তো এড়িয়ে গেলি ওরে ভোলানাথ
ভবেছিস উল্টোপাল্টা কথা বলে করবি আসর মাত’
তখন ভোলা ময়রা—
‘শোনরে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট, তুই রে নষ্ট মহাদুষ্ট
তার কি ইষ্ট কালীকেষ্ট, ভজগে যা তুই যিশুখ্রিষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে’
অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি—
‘সত্য বটে সত্য বটে!
আমি জাতেতে ফিরিঙ্গি
ঐহ্যিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী’
দুই পক্ষের আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ শেষে দুই মহাকবিয়ালের মহামিলন। জয়ের পরেও অ্যান্টনি ভোলার কাছে হার মেনে নেয়, গুরু বলে সম্বোধন করে। বলে, তার কবি গানে অনুপ্রাণিত হয়ে সে এই পথে এসেছে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভোলা ময়রার কবিগানের স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেখানে ফিরিঙ্গি হয়ে তার কি সাধ্য তাকে অবজ্ঞা করা। সে তো একলব্যের মতো একান্ত মনে তার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে এই কবিয়ালি শিক্ষা লাভ করেছেন। ভোলা ময়রার প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।’
করীম চাচা বলত, এসব হলো জনগণের কবিতা। জনগণকে সঙ্গে করেই এই কবিতা লেখা হতো। কবিয়ালরা তার সামনের শ্রোতৃমণ্ডলীকে সামনে রেখে এই গান কবিতা রচনা করতেন।
কবিয়ালদের আরেকটা গুণ ছিল জাতপাত বিভেদ ভারতীয় সমাজে সাম্যের কথা বলা। কারণ যারা এই কবিগান গাইতেন তারা অধিকাংশ ছিল সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ, এমনকি তাদের শ্রোতারাও ছিল সমাজের নিম্নবর্গের—যারা তথাকথিত উঁচু জাতের মানুষের দ্বারা ছিল নিগৃহীত। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই গানের কদর ছিল। এরাই ছিলেন তখন অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রচারক, বহুবিভক্ত সমাজে শান্তির বার্তাবাহক। ভোলা ময়রার গুরু হরু ঠাকুর ছাড়াও তখন রাম বসু, বলাই সরকার, যজ্ঞেশ্বর ধোপা, হোসেন খাঁ’র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ভোলা ময়রার জামাই নবীনচন্দ্র দাস এ দেশে প্রথম রসগোল্লা উদ্ভাবন করেন। এটি বাঙালির নিজস্ব সৃষ্টি।
করীম চাচার গানের দলে যারা কাজ করতেন তাদের অধিকাংশ ছিল শৌখিন গায়েন। চুরুলিয়া, নিমসা ও রাখাখুড়া গ্রামের মধ্যেই ঘুরেফিরে তারা পালা গান গাইত। চাচার চেয়ে বাসুদেব ও শেখ চকোর দল অধিক পেশাদার ছিল, সারা বছরই তারা কোানো না কোনো বায়না নিত। আর করীম চাচা প্রায় প্রতিবছর নতুন করে দল গঠন করতেন পৌষ-মাঘ মাসে শীতের মৌসুমে। এই মৌসুমে বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলটি মেলায় মেলায় মুখরিত হয়ে উঠত। চুরুলিয়া থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অজয় নদীর তীরে কেন্দুলি গ্রামে কবি জয়দেবের মেলায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়। বাউলদের থাকার জন্য তিন শতাধিক আখড়া নির্মাণ করা হয়। একই জেলায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত পৌষমেলার সুনামও ততদিনে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের জেলা বীরভূমের এই মেলার বাউল ও কবিগান আমায় এমনভাবে টানত, ভাবতাম আমিও একদিন এরকম কবি গানের দল গড়ে তুলে গ্রামে গ্রামে মেলায় ঘুরে বেড়াব।
করীম চাচা বললেন, দুখু, তোর তো এখন পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই। মক্তবও তো বন্ধ আছে, চল এবার আমার সাথে, গান বাঁধবি, দোহারের কাজ করবি, তোর যা গলা—মাশাল্লাহ, আমার ধারণা ভালোই পারবি, খুব অল্পদিনে ওস্তাদ হয়ে উঠবি।
চাচার এই প্রস্তাব আমার কাছে হাতে চাঁদ ধরার মতো ছিল। এমন কিছুর জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু নিজ থেকে বলার সাহস পাই নি। মক্তবের বন্দিত্ব, একঘেয়েমি আমার ভালো লাগছিল না।
নানা বয়সের প্রায় বিশ জনের দল ছিল চাচার। একটি পূর্ণাঙ্গ লেটোদল বানাতে লাগত একজন ম্যানেজার, দোহার, মাস্টার, ব্যাঙাচি, বিবেক, ছোকড়া, সঙদার, পুরুষ শিল্পী, একজন অর্ধনারী গায়েন, বাই, চারজন সখী, একজন গোদা কবি বা দল প্রধান। এছাড়া দলে আরো কিছু কাজ থাকত যেমন মঞ্চ পরিকল্পনা, সাজঘর তৈরি, বাজনাদার, পেইন্টার, আগলদার। অবশ্য এসব কাজের অনেকটা সম্পাদন করত ওইসব এলাকার লোক—যারা গানের বায়না নিয়ে যেত। নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তখনো মেয়েরা আসতে শুরু করে নি। পুরুষদেরই এ দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাদের এমনভাবে সাজিয়ে তোলা হতো, নৃত্য পরিবেশনা ও শারীরিক ভঙ্গী তাদের মেয়ে বলেই ভ্রম হতো। গান গাইতে গেলে অনেকে তাদের পাশে ঘুরঘুর করত।
বজলে চাচার দলে তিনি নিজেই ম্যানেজার ও গোদা কবির দায়িত্ব পালন করতেন।
লেটোগানের একক কোনো জাত ছিল না। কখনো কবিগানের মতো দুই পক্ষ মুখোমুখি—একপক্ষ আরেক পক্ষকে ছন্দ ও সুরে কথার প্যাঁচে ফেলে দর্শকদের ভাবনা উসকে দিত। তারা একপক্ষের যুক্তির অকাট্য আক্রমণ কিভাবে অন্যপক্ষ রুখতে পারবে—এইসব ভাবনার মধ্যে দর্শকের মনে গোলক ধাঁধার সৃষ্টি হতো। বিষয় হিসাবে কখনো রাজা-রাজড়ার কাহিনি, হিন্দু পুরাণ, মুসলমানদের পুঁথির গল্প, আবার পাশাপাশি খুব আটপৌরে ধরনের স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক কলহের মধ্যেও রস খোঁজা হতো। তবে যে পালাগুলো সবচেয়ে বেশি হতো—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, জেলে ও জেলেনি, আজব বিয়ে, অপূর্ব বিচার, রাধা-বিনোদ, রাজা হরিশচন্দ্র, জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা, দস্যু বাহারাম, বীর হাম্বির, মাটির কেল্লা, শয়তানের চর প্রভৃতি।
আমি লেটো দলে যোগ দিয়ে বেশ কয়েকটি পালা রচনা করে গোদা কবিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। শকুনি বধ, চাষার সঙ, রাজপুত্র, আকবর বাদশা—আমার রচিত এই পালাগুলো দল ত্যাগ করার পরেও দীর্ঘদিন চুরুলিয়া, নিমসা, কৈলাসপুর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে মঞ্চস্থ হতে থাকে। আমি তখন ব্যাঙাচির পাঠ করতাম। শেখ চকোর দলে যোগ দিয়েছি, আমার গান রচনা করা, উপস্থাপন ও যুক্তির মারপ্যাঁচ দেখে গোদাকবি ওস্তাদ শেখ চকোর বলেছিলেন—‘আমার ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে।’
গোদাকবি হওয়ার মতো সব সম্ভাবনা আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন দলের আধিকারিকগণ। কিন্তু এ পথ আমার নয়—বুঝতেও খুব একটা দেরি হয় নি।
লেটো গান আমার জীবনকে পরবর্তী ধাপের জন্য নির্মাণ করে তুলছিল। সামনে অসংখ্য সাধারণ মানুষ যারা মুগ্ধ হয়ে এই সব গান ও সস্তা বিনোদন পেতে চাইতেন—তারা সারাদিন পরিশ্রমের পরে কী কথা শোনার জন্য এখানে ছুটে আসতেন—সে-সব আমি তাদের মুখ দেখে বুঝতে চেষ্টা করেছি। জাতপাতের বেড়াজালের সংসার, নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসারে স্বামী-স্ত্রীর কোলাহল, ইংরেজ শাসনের ফলে জনগণের অর্থনৈতিক কষ্ট ও ব্যর্থতার হাহাকার—অতীতে তাদের একটা সুখী জীবনের গল্প ছিল সে-সব শুনে দীর্ঘশ্বাস—এসবই ছিল তাদের শোনার চাহিদা। তবে নারী-পুরুষের সম্পর্কেও হাসির গানগুলো নিষ্পাপ হাসির জন্ম দিত। এক আসরে যখন গাইলাম—
‘আমি করব না আর বিয়ে।
আমার বিয়ের শখ মিটেছে দাদার বিয়ে দিয়ে।’
তখন দর্শকরা বড়ই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পাশাপাশি গাইতাম—
‘সে কেন আমারে মজাইল সই।
আমি যে তার বিয়ে করা বৌ যে না হই।’
রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহের গানেও শ্রোতার যারপর নাই আনন্দ পেত—
‘জল আনিতে যাব না আর ঐ যমুনার কূলে।
কদম গাছের সাথে কালা বাঁশীতে সুর তোলে।’
কিংবা ‘কালো রূপে আমি কেন নয়ন দিলাম সই।
কালো দেখে কালার রূপে আমি পাগল হই।’
ব্যথা দেয়ার কাজটি আমি সারাজীবন ধরে করেছি, নিজের ব্যথা জনতার ব্যথা ও জাতির ব্যথা আমার জীবনে একাকার হয়ে গেছে।
লেটো গানের দলে এসে এই শিল্প মাধ্যমে আমি কোনো ভিন্ন অবদান রাখতে পেরেছি মনে হয় না। গ্রাম-গঞ্জের সাহিত্যের এই ক্ষয়িষ্ণু ধারা নাগরিকজনের মনে কোনো দাগ কাটতে পারে নি। ভাড় সঙ বিবেকের হালকা রসিকতা বলেই তা উপেক্ষিত থেকেছে, তবে এ ধারার অন্যান্য কবির সঙ্গে আমিও শ্রেণিপাতের দুঃখ-কষ্ট এখানে গ্রথিত করে রাখতে চেষ্টা করেছি। সেদিনের রচিত সঙদের দুঃখ নিয়ে একটি পদ এখনো মনে আছে খানিকটা—
‘মোদের এ সঙ নয় শুধু কালি মেখে সঙ সাজা,
নয়কো শুধু হালকা হাসি নয়কো শুধু মজা..
সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি আদি
বলতে গিয়ে কারো প্রাণে ব্যথা দি যদি..’
এই ব্যথা দেয়ার কাজটি আমি সারাজীবন ধরে করেছি, নিজের ব্যথা জনতার ব্যথা ও জাতির ব্যথা আমার জীবনে একাকার হয়ে গেছে। দলের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দর্শক শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে রামায়ণ-মহাভারত, হাদিস কোরানের নানা সূত্র থেকে গান রচনা করতে হতো। বিশেষ করে এ ধরনের গানবাজনা যে শ্রেণি হারাম বলে ঘৃণা করত কিংবা শাস্ত্রে নিষেধ বলে দূরে রাখত তাদের অবিমৃষ্যকারিতার জবাব দিতে গিয়ে এসব গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হতো। এই সব অধ্যয়ন পরবর্তীকালে আমার কবি জীবনে ব্যাপকভাবে প্রভাব তৈরি করেছে। এই জন্য আমি চাচা বজলে করীম, শেখ চকোর, বাসুদেব কবিয়ালসহ আমার অবহেলিত অনুল্লেখিত অসংখ্য গুরুদের কাছে ঋণী। এতটা পেছনে এসে মনে হয়, সেদিনের সেই লেটোগানই আমায় জনগণের কবি হওয়ার পথে এগিয়ে দিয়েছিল।
শেখ চকোর দলে যোগ দেয়ার পরে সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে, বিশেষ করে নারী পুরুষের সম্পর্ক, পর্দাপ্রথা, তৎকালীন মানুষদের চোখে মেয়েদের বেলেল্লাপনা, নরাীর সেবাধর্ম, পুরুষের বীরধর্ম আমার গানের বিষয় হয়ে দেখা দেয়। গ্রাম-গঞ্জে আমরা কবিগান গেয়ে বেড়ালেও শহরের কবিদের কথা তখন একেবারে অজানা ছিল না। তাদের আমরা শহুরে বাবুদের কবি বলে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলে রাখতাম। ঈশ্বরগুপ্তের কিছু কিছু কবিতা তখন আমাদের কবির দলে গাওয়া হতো। তিনিই এখন পর্যন্ত শেষ কবি যিনি আধুনিক শহর ও ইংরেজের অবহেলিত গ্রাম জীবনের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ রচনা করে গেছেন। তার একটি কবিতার বিষয় ছিল—বেথুন সাহেবের শিক্ষার ফলে মেয়েরা যে সব গোল্লায় যাচ্ছে, তাদের আর বাবদাদার সংস্কারের দিকে মুখ ফেরানো যাচ্ছে না, কবি আসরে গাইলে শ্রোতারা পছন্দ করত। এইসব গানের দলগুলো নিঃসন্দেহে কিছুটা রক্ষণশীল ধ্যানধারণা লালন করত। যেমন—
‘যত ছুড়িগুলো, তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন ‘এ বি’ শিখে ‘বিবি সেজে’,
বিলাতি বোল কবেই কবে।’
আমার গানের মধ্যেও তখন ইংরেজি বাংলা অপভ্রংশের ব্যাপক মিশ্রণ ঘটছিল। নব বাবুদের আচরণ অনুকরণে উপহাস ও শ্লেষের বাহন হিসাবে এই খিচুড়ি ভাষার প্রয়োগ বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল। একবার শেখ চকোর ওস্তাদের দলের সঙ্গে গান গাইতে গেছি জেলার পূর্ব দিকে কাঁকুরা থানার কৈলাসপুরে। এ জেলারও অনেকে কৈলাসপুর চেনেন না, কৈলাসপুর বলতে অনেকে মনে করে উত্তর ভারতের রাজধানী। লেটোদলের সুবাদে নিজ গ্রামের বাইরেও দূরদূরান্তে আমাদের ডাক আসত, দূরের আহ্বান সব সময়ে আমাকে ডাকে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তাৎক্ষণাৎ ছুটে গেছি সেই সব স্থানে, লক্ষ করেছি সেখানকার মানুষজনের আর্থিক অবস্থা, ভাষা ও সংস্কৃতি। কৈলাসপুর একটি ছোট্ট পঞ্চায়েত হলেও সেখানেও ঠেকানো যায় নি ভাঙন—অবক্ষয়। গ্রামের যুবক শ্রেণি, দুএক ক্লাস লেখাপড়া শেখার আগেই চলে যাচ্ছে ইংরেজ শহর কোলকাতায়, ভুলে যাচ্ছে বাপদাদাদের সংস্কৃতি। গ্রামে আলো নেই, স্বাস্থ্য নেই, কর্ম নেই, কোলকাতায় গেলে অন্তত কিছু একটা করতে পারবে বলে আশা। সাহেবদের শহর, কিছু একটা কাজ জুটে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন ছিল, তেমন আধুনিক শহরের হাতছানি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে যেতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। তাদের এই উন্মূল গমন গ্রামের প্রবীণদের পছন্দ নয়। কৈলাসপুরে গানের বায়না নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানকার আয়োজকরা অনুরোধ করলেন, তাদের এলাকার হালফিল নিয়ে যেন আসরে গান গাওয়া হয়। আসি এই আসরে তাৎক্ষণাৎ রচনা করলাম—
‘রবনা কলৈাসপুর, আই এম ক্যালকাটা গোয়িং
যত সব ইংলিশ ফেসেন, আহা মরি কি লাইটনিং।
ইংলিশ ফেসেন সবি তার, মরি কি সুন্দর বাহার।
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার, কাম অন ডিয়ার গুড মর্নিং।’
কোলকাতা থেকে কৈলাসপুরের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়—মাত্র পঞ্চাশ/ষাট মাইলের ব্যবধান। আমিও কোলকাতা যাওয়ার আগে আমার গ্রাম চুরুলিয়া ও জেলার পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়েত কৈলাসপুরের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো আটকে রইলাম।