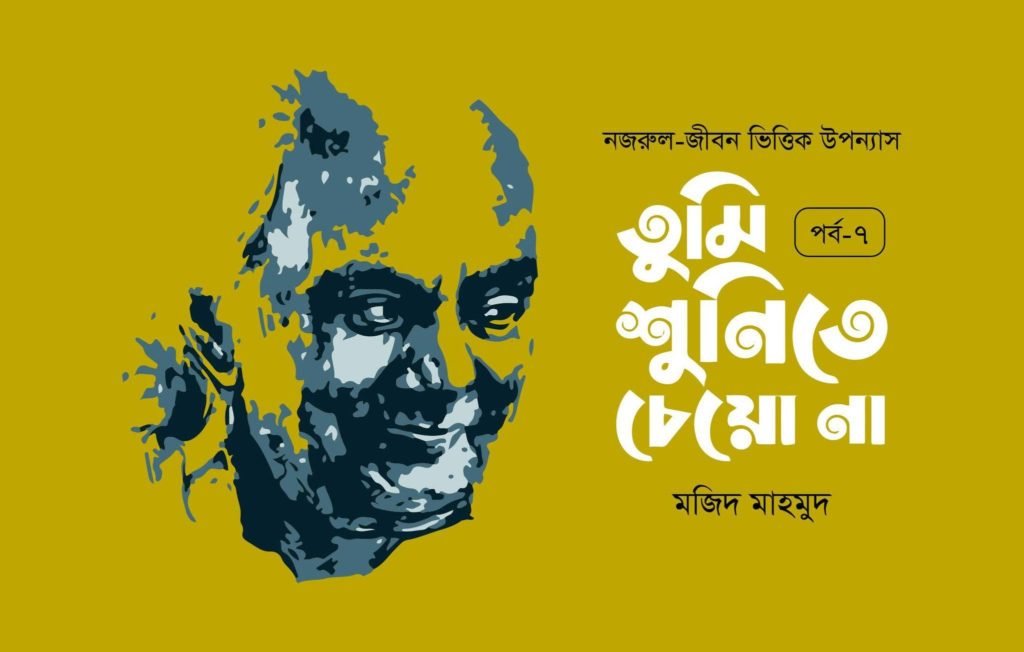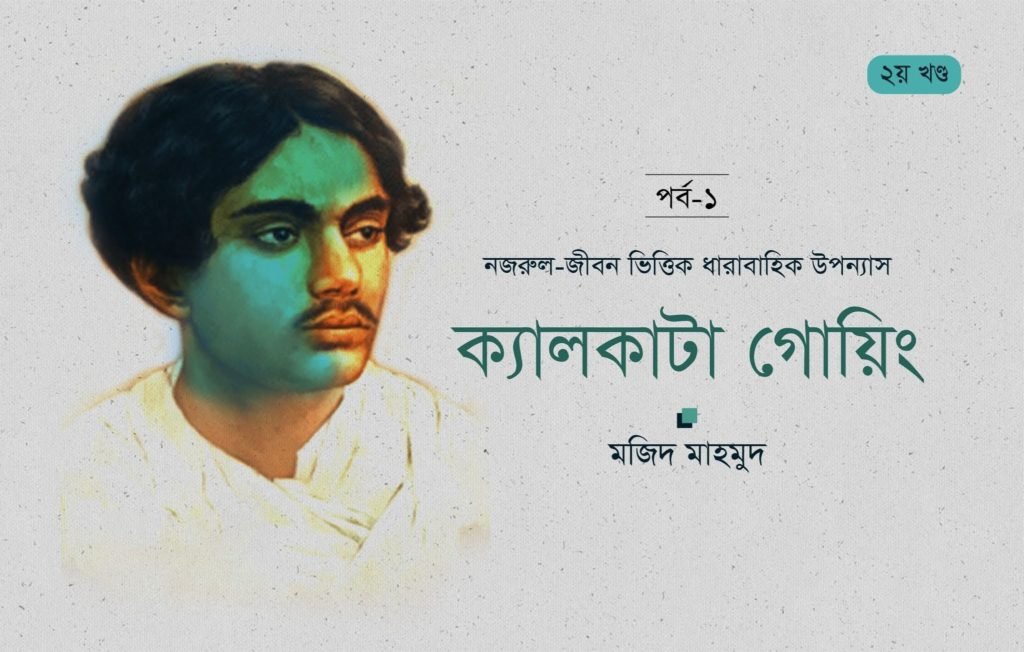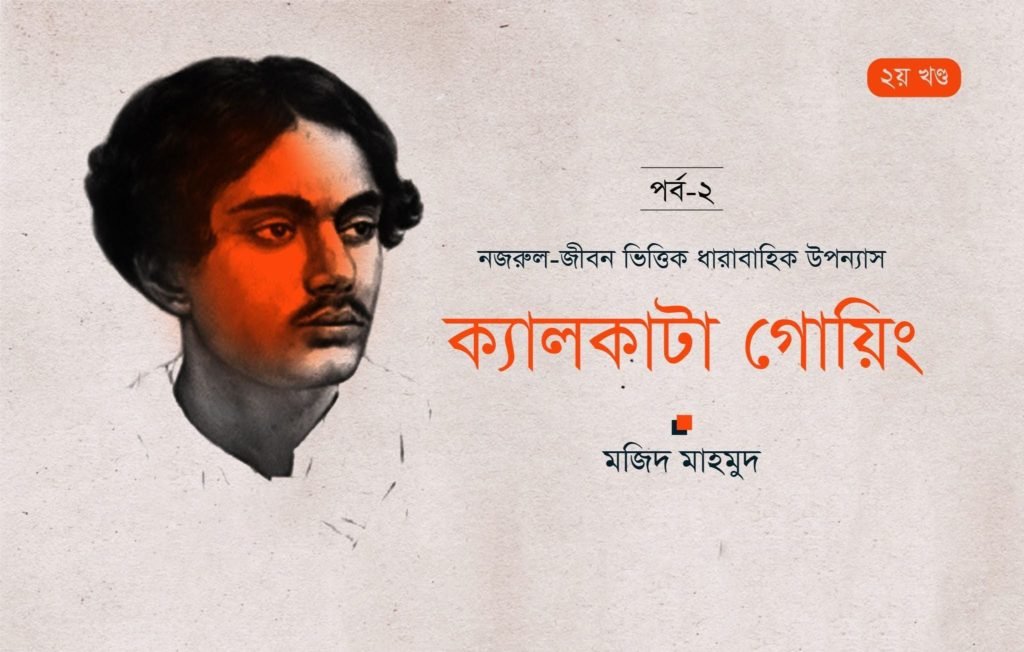পর্ব-৭
রহস্যজনকভাবে ভয়ংকর ‘দীর্ঘ ছুরির সপ্তাহ’ পরের এক বছরের মাথায়, ঠিক একই দিনে এই ঘটনা ঘটে। মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা দেশ হওয়ায় ভারত থেকে অনেকে পাকিস্তানে চলে গেছে। জসীম, নাহার, মঈনউদ্দীন, বন্দে আলী, গোলাম মোস্তফা, কাদির, আব্বাস, ফিরোজা, সওগাতের নাসিরউদ্দিন এখন পাকিস্তানে থাকে। এছাড়া এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দি, নাজিমউদ্দিন, মনসুর, বাহার—যাদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় পাকিস্তান হয়েছে তারা তো সেখানে আছেই। আবার আবদুল ওদুদ, এস ওয়াজেদ আলী, আফজালুল হক—আগে থেকে এখানেই আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুবাদে ওখানেই থাকে, মোহিতলাল চাকরি শেষে কোলকাতা ফিরে এসেছে। আমি অথর্ব কোলকাতায় থাকলেও জনদাবি অনুসারে এখন দুই দেশের নাগরিক।
এখন চাইলেই বন্ধু ও ভক্তরা আমায় দেখতে আসতে পারে না। যদিও তাদের ভৌগোলিক দূরত্বে কোনো পরিবর্তন হয় নি। শুধু মাঝখানে পথরোধ করে দুই দেশের কিছু লোক বসে আছে, তাদের কাজ এপার থেকে ওপার যেতে চাওয়া মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমার অবস্থা এখন ত্রিশঙ্কু। ভারত যেমন আমার দেশ—তেমন পাকিস্তান আমার দাবি ছাড়তেও নারাজ। তবে আমি যে কাজী নজরুল ইসলাম—ভারত তথা অখণ্ড বাংলার কবি, সেটি আর কেউ মানতে চায় না। সন্ত কবীরের ভক্তের মতো কেউ করতে চায় দাহ, কেউ দিতে চায় কবর।
আমার চার পুত্রের তিন পুত্র আমার জীবদ্দশায় মারা গেছে।
পাকিস্তান হওয়ার পরে অন্নদাশঙ্কর রায় আমায় নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিল। কবিতাটি আবদুল কাদির ওর ‘মাহে নও’ পত্রিকায় ছাপার পরে গোলাম মোস্তফা খুব রুষ্ট হয়েছে। এখন মোস্তফার চরিত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে। কিছুটা খেপাটেও হয়ে উঠছে। ইসলামি তমুদ্দুনের প্রতি ওর ভালোবাসা খাঁটি। তাই বলে সব কিছু বাদছাদ দিয়ে একেবারে একটি ইসলামি সংস্করণ কি বাস্তবে সম্ভব! ও তো কোলকাতার প্রাণকেন্দ্র হেয়ার স্কুলেও দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করল। জীবনের বেশিরভাগ কাটাল কোলকাতায়—মিশ্র সংস্কৃতির রাজধানীতে। ওর ছাত্রছাত্রীদের সবাই যে মুসলমান তাও তো নয়, বরং অধিকাংশ হিন্দু। ‘বিশ্বনবী’ লিখলেও বিশ্বনবীর সব ইঙ্গিত তার কাছে ধরা দেয় নি। আমি পাকিস্তানের জাতীয় কবি হওয়ার যোগ্য নই বলে ‘নও বাহার’ পত্রিকায় সে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ওর যুক্তিতে হয়তো ভুল ছিল না। সত্যিই কি আমার পাকিস্তানের জাতীয় কবি হওয়ার যোগ্যতা আছে? মোস্তফা লিখেছে—
হিন্দু কালচারের দ্বারা নজরুল সম্পূর্ণ বিজিত হইয়াছিলেন। পাকিস্তানের কথা বলিতে তাই তিনি লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেন। ঐসব বিষয়ে কবিতা বা গান লিখিলে পাছে তার সাম্প্রদায়িক রূপ প্রকট হইয়া পড়ে, এই ছিল মনের আতঙ্ক। এই জন্য পাকিস্তান বা কায়েদা আজম সম্বন্ধে একটি কবিতা বা গানও রচনা করেন নাই। তিনি আগে ভারতবাসী পরে মুসলমান।
সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদর্শন না করাও যে একটি অপরাধ—সেটি আমি জীবনভর মোকাবেলা করেছি। এটি ইংরেজের দুশ বছরের শিক্ষার বিভাজন-নীতি ছাড়া আর কী হতে পারে। আটশ বছরের মুসলিম শাসনে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উত্তারাধিকার হয়ে উঠেছিল ভারত। হিন্দুদের ঘৃণা করে ভারতে শাসন জারি রাখা মুসলিম শাসকদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।
আবদুল কাদির এখন পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মাহে নও’ পত্রিকার সম্পাদক। এক সময়ে আমার বন্ধুতালিকা বিচিত্র হলেও আবদুল কাদির ও তার শ্বশুর মোজাফ্ফর আহমদ—দুইজনই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল—আমার জীবনে তাদের অবদান অনেক। কাদির আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট, আর তার শ্বশুর মোজাফ্ফর আহমদ আমার কয়েক বছরের বড়। কাদিরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠানে। কোলকাতায় সে ‘নবযুগ’ পত্রিকায় আমার সহকর্মী হিসাবেও কাজ করেছে। কাদিরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দিলরুবা’ প্রকাশিত হলে আমি ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায় একটি পরিচিতিমূলক আলোচনা লিখেছিলাম। তার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি—যথাস্থানে বর্ণনা করা যাবে। তবে দেশ ভাগ আমার মতো কাদিরকেও বিভাজিত করেছে। তার শ্বশুর কোলকাতায় থেকে গেছে, আর কাদির ও তার স্ত্রী আফিয়া খাতুন ঢাকায়। নিন্দুকেরা বলে, মোজাফ্ফর আহমদের স্বপ্ন ছিল আমার সঙ্গে আফিয়া খাতুনের বিয়ে দেয়া।
কাদিরের সঙ্গে দেশ-বিভাগের প্রায় তিরিশ বছর পরে আমার দেখা হয়েছিল—বাংলাদেশে থাকা-কালে। আমি তখন ধানমন্ডি বাসবভনে, যেটি এখন নজরুল ইনস্টিটিউটের অফিস। আমার কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলে তারা চেহলামে এসেছিল। মৃত্যুকালে অনিরুদ্ধ ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোলকাতায় আর আমি স্বাধীন বাংলাদেশে। পুত্রের অন্তিম যাত্রা আমার দেখা হয়ে ওঠে নি। হয়তো সংসারীদের কাছে এর কোনো অর্থও ছিল না। তাদের কাছে আমি তখন শোক-দুঃখের অতীত। কিন্তু বিষয়টি মোটেও তেমন ছিল না। আমার চার পুত্রের তিন পুত্র আমার জীবদ্দশায় মারা গেছে। আমাকে যে কারণে দুখু মিয়া বলা হয়, আমার পুত্রদেরও সেই কারণে ওই একই নামে ডাকা যেতে পারে।
কাদির বলেছে, ‘আমি অনিরুদ্ধের চেহলামে ধানমন্ডি কবিভবনে গেলে কবিপুত্র সব্যসাচী ও পুত্রবধূ উমা কাজী কবিকে বৈঠকখানায় নিয়ে এল। কবি আমার পাশে সোফায় বসে কয়েক মিনিট হাত ধরে আমার দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন। আমি আমার শ্বশুর, কবির শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মোজাফ্ফর আহমদের মৃত্যু খবর দিতেই, কবি ঠোঁট নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন।’
মোজাফ্ফর আমার এমন বন্ধু যে, আমি ছাড়া তার কর্মের কোনো ইতর-বিশেষ হতো না। মোজাফ্ফর ছাড়া আমি নেই। আমি না থাকলেও তার যা করার কথা সে তাই করত। তার রক্তে ছিল সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি—মার্কসবাদ। আমি কবি হতাম নিশ্চয়, কিন্তু ওর সান্নিধ্য ছাড়া সাম্যবাদী, সর্বহারা কাব্যগ্রন্থ লিখতাম কিনা বলা মুশকিল।
তার মৃত্যুর খবর শোনার পর কাদির লক্ষ করল, ‘হঠাৎ আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং তার হাত ধরে বাড়ির এ-কক্ষে সে-কক্ষে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলাম। তারপর বৈঠকখানায় ফিরে এসে সোফার উপরে কাদিরের পাশে স্থির হয়ে বসে পড়লাম।’
‘এই শোকের দিনে একজন পুত্রহারা পিতা আর একজন বন্ধুহারা বন্ধু এর চেয়ে কিভাবে শোক প্রকাশ করতে পারতেন।’
এই তো আমার জীবনে দেশবিভাগের ফল। আমি বাকরুদ্ধ না হলে কিভাবে প্রকাশ করতাম এই দুঃসহ যন্ত্রণা!
মহাকাব্যের ট্র্যাজিক নায়করাও ভয়াল শত্রুর কাছে নিহত পুত্রের সৎকারের জন্য লাশ ভিক্ষা করতে পেরেছিল।
ট্রয়যুদ্ধে প্রতিপক্ষ একিলিসের হাতে বীর হেক্টর নিহত হয়েছিল। একিলিস রথের চাকায় হেক্টরের মৃতদেহের পায়ে রশি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় গ্রিক শিবিরে। একিলিসের ইচ্ছা কেবল হেক্টরকে হত্যাই নয়, তার লাশও বিকৃত করা, যেহেতু সে তার তুতো ভাই পেট্রোক্লাসকে হত্যা করেছে। হেক্টরের পিতা রাজা প্রিয়াম পুত্রের এই অবমাননা সইতে পারলেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন সে একাই যাবে শত্রুশিবিরে—পুত্রহন্তার কাছে লাশ ভিক্ষা চাইবে। লাশের অধিকারও হত্যাকারীর। একিলিস তাকে দেখে চমকে উঠল। কে এই ভয়ংকর বৃদ্ধ যে এত রাতে একাই ঢুকে পড়েছে ভয়াল রণ-শিবিরে।
একিলিস : কে আপনি! এত রাতে আমার শিবিরে?
প্রিয়াম একিলিসের সামনে জানু পেতে বসে, তার হস্ত চুম্বন করে বলল, ‘আমি দুনিয়ায় সেই হতাভাগা পিতা—যার ঠোঁট স্পর্শ করেছে তার পুত্র হত্যাকারীর হাত।’
—প্রিয়াম! আপনি? কিভাবে এই দুর্গের ঘোর পথ চিনে এখানে আসতে পারলেন!
—এটি আমারই দেশ একিলিস, এর সব রাস্তাঘাট আমার চেনা আছে।
—আপনি তো আমার শত্রু—রাত পোহালেই আপনার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ।
—তুমি তো এখনো এই রাতেও আমার শত্রু একিলিস। কিন্তু যুদ্ধেরও তো নিয়ম আছে।
—কী অভিপ্রায় আপনার এখানে আসার?
—তুমি আমার প্রিয় পুত্রকে হত্যা করে রথের চাকায় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসেছ। তার শরীরে অনেক ময়লা লেগেছে, শরীর হয়েছে ক্ষতাক্ত। আমি আমার প্রিয় পুত্রের শরীর থেকে সে সব ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ করতে চাই। তাকে শান্তিতে দাফন করতে চাই। তার দুই চোখে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রাখতে চাই—যাতে শেষ পুলসিরাত নিরাপদে পেরুতে পারে সে।
—সে আমার তুতো ভাই পেট্রোক্লাসকে হত্যা করেছে।
—তুমি প্রতিদিন কত তুতো ভাইকে হত্যা করছ একিলিস। কত নারীকে করছ বিধবা, কত মায়ের কোল করছ খালি। আমি তোমার কাছে এসেছি—তোমার বাবা হলেও হয়তো তা-ই করতেন। তোমার বাবা মেনালাউস ছিলেন আমার বন্ধু। আমাদের ভালোভাবে চেনাজানা ছিল।
একিলিস এ কথা শুনে স্মৃতি-তাড়িত হয়ে প্রিয়ামের মতো কেঁদে ফেলল। প্রথমে সে তার পিতার কথা মনে করে কাঁদল, তারপর পেট্রোক্লাসের জন্য, এমনকি পুত্রহারা পিতার জন্যও কাঁদল। তারপর হেক্টরের লাশ ফেরত দিল। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নয় দিবসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল।
মেঘনাদ নিহত হলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য রাম তার স্ত্রী হরণকারীকেও সময় দিয়েছিলেন। পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে ‘সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।’ তার মানে রাবণকেও পুত্র সমাহিত করার জন্য শত্রুপক্ষ সাত দিন সময় দিয়েছিল।
আমি মহাকাব্যের সেই ট্র্যাজিক পিতা—যার পুত্র ও পিতা দুই দেশের নাগরিক। আমি রাজা প্রিয়ামের চেয়ে হতভাগ্য যে তার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য ও জাতীয় দুর্ভাগ্যের কারণে নিজের পুত্রের লাশ শেষবারের মতো দেখতে পারে নি।
আমার ছোট ভাই আলী হোসেন, আমার শাশুড়ি গিরিবালা দেবী—তারাও দেশভাগের গভীর ক্ষতে হারিয়ে গিয়েছিল। এমনকি শেষ বিদায়ে আমার একমাত্র জীবিত পুত্র সব্যসাচীর এক মুষ্টি মাটি আমার জোটে নি। দেশবিভাগের ফলে পিতার কাছে থেকে পুত্র এভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আমার অসুস্থতার প্রথম পর্যায়ে বড় ভাই সাহেবজান মৃত্যুবরণ করে।
গিরিবালা দেবী দাঙ্গার মধ্যে হারিয়ে গেলে অনেকে ভাবল—‘বিধবা মানুষ, সংসারের জ্বালা সইতে না পেরে হয়তো চলে গেছে কাশি-বৃন্দাবন-মথুরায়। আচারনিষ্ঠ হিন্দু হয়েও মুসলমানের সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়ে যে পাপ করেছে, তার পায়শ্চিত্ত করার জন্য চলে গেছে কোনো তীর্থ-ধামে। জসীমের একটা স্মৃতি-চারণের সাক্ষীতে আমার জীবনীকাররা ধরেই নিয়েছিল—আমার শাশুড়ি বাড়ি ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে গেছে শ্রীকৃষ্ণ-ধামে। ‘আমি একদিন এই সংসার ছেড়ে যে দিকে খুশি চলে যাব।’ এটি বিশ্বাসযোগ্য! গিরিবালা দেবী যে তার একমাত্র মেয়ের সুখের জন্য এক বস্ত্রে ঘর ছেড়েছিল, সে তার অসুস্থ মেয়েকে ছেড়ে, অসুস্থ জামাইকে ছেড়ে, তার নাবালক দৌহিত্রদের অতল সমুদ্রে ভাসিয়ে—নিজে পারলৌকিক শান্তির জন্য ঘর ছেড়ে যাবে! অথচ তার নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার সপ্তাহের দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ হলো নিহত।
তারা আমার সাহিত্যের কর্তন করছে এই ভেবে যে, আমি পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই নি।
আমরা তখন থাকতাম শ্যামবাজার স্ট্রিটে—হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকায়, আমার নিরাপত্তা নিয়ে আমার বন্ধু-বান্ধবরা থাকত উদ্বিগ্ন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে, নলিনীর কাছে বন্ধু-বান্ধব অনেকেই খোঁজ-খবর নিয়েছে। চিঠি লিখে অনুরোধ করছে, ‘নজরুল পরিবার নিয়ে তো আমরা ভয়ে আছি।’ ওরা জানে গিরিবালা দেবীর প্রতি রাগ আছে—হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের। গিরিবালা মুসলমানের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিয়ে তাদের ধর্মের অবমাননা করেছে। মুসলমানরা মনে করে—গিরিবালা দেবী না হলে নজরুল হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি এতটা ঝুঁকে পড়ত না। গিরিবালা দেবী ছিল দুপক্ষেরই লক্ষ্য।
দেশভাগের পর পর আমার ছোট ভাই আলী হোসেন নিজ এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হয়। দেশবিভাগের ফল, হিন্দু মুসলিমকে হত্যা করবে, মুসলিম হিন্দুকে হত্যা করবে—এই ধর্মীয় রাজনৈতিক অনুমোদন যদি কেবল কাজী নজরুল ইসলামের পরিবারে ঘটে থাকে তাহলে এর প্রকৃত ক্ষত কতটা গভীরে!
এর বিষাক্ত বাষ্প ছড়িয়ে পড়েছিল একই বিদ্যালয়ের সতীর্থ ও শিক্ষকদের মনের গভীরে। গোলাম মোস্তফা হেয়ার স্কুলে পড়ানোর সময়ে নিয়মিত ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে আসত আড্ডা দিতে। আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিল। লেখাটি বেশ নাম করেছিল, খুব অল্প কথায়—মাত্র পঁচিশ শব্দে আমার চরিত্র নাকি নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছিল। নাকি বললাম এই জন্য যে, নিজে তো নিজের চরিত্র নিরপেক্ষভাবে আঁকা যায় না। অচিন্ত্য ‘কল্লোল যুগে’ ওর কবিতাটি উদ্ধার করেছিল, বুদ্ধদেব বসুও আমায় নিয়ে তার রচনায় ব্যবহার করেছিল। বয়সের কিছু হেরফের হলেও ওরা আমার বন্ধু। ওদের কাছে যদি মনে হয় আমি তেমন, কিভাবে তার বিরোধিতা করি। ওর কবিতাটি ছিল এমন : ‘কাজী নজরুল ইসলাম/ বাসায় একদিন গিছলাম।/ ভায়া লাফ দেয় তিন হাত/ হেসে গান গায় দিন রাত/ প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়/ ধরার পর তার কেউ নয়।’
অচিন্ত্য আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। ওর বিয়েতে আমরা অনেক মজা করেছিলাম। এখানে শুধু একটি কথা বলে রাখি। ওর নববধূকে আমি বই উপহার দেয়ার সময়ে যে স্বাক্ষর করেছিলাম, সেখানে লিখেছিলাম—‘অচিন্ত্যনীয়াসু।’
অচিন্ত্য দেখে বলল, ‘য-ফলাটা বোধ হয় হবে না কাজী।’
আমি হাসতে হাসতে বললাম, ‘তা না হলে এ যে তোমার বৌ তা বোঝা যাবে কী করে?’
আমাদের এ ধরনের রসিকতা দেখে নববধূও হেসে ফেলল।
বন্ধুদের বিয়েতে গেলে এমনিতেই নববধূরা শাড়ির ঘোমটার ফাঁকে আমায় দেখে নিতে চেষ্টা করত। স্বামী বেচারা তো হারাচ্ছে না, এই ধূমকেতুকে পরে আর দেখা নাও যেতে পারে।
বুদ্ধদেব আর অচিন্ত্যের একটা জায়গায় মিল ছিল, দুজনেরই জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। দুজনেই ইংরেজি সাহিত্য পড়েছিল। তবে প্রেমেন্দ্রের মতো অচিন্ত্যও তথাকথিত বন্ধুদের আধুনিকতায় পাদপ্রদীপের নিচে চলে গেছে। ওর সময় এতটা জনপ্রিয় লেখক আর ক’জন ছিল। ওর ‘পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’ প্রকাশের পরে দীর্ঘ লাইন দিয়ে সবাই বই কিনেছিল। আমায় নিয়েও ‘জ্যৈষ্ঠের ঝড়’ নামে একটি বই লিখেছিল।
গোলাম মোস্তফাসহ যারা পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমার কর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের আজ অনেকেই দায়ী করতে চায়। তাদের বিরোধিতার দ্বারা এটি বোঝায় না যে, তারা আমার প্রতিভার অবমূল্যায়ন করেছিল। বরং বলতে চেয়েছিল, যে কারণে আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছি, তার সঙ্গে কাজীর যুক্ততা নেই। কাজী অখণ্ড বাংলার পক্ষে ছিলেন, অখণ্ড ভারতের পক্ষেও। সুতরাং কাজী যত বড় কবিই হোক না কেন, পাকিস্তানের জাতীয় কবি হওয়ার যোগ্য নয়।
গোলাম মোস্তফার যুক্তিতে ভুল ছিল না, হয়তো ভক্তিতে কম ছিল।
ইংরেজ এদেশ থেকে চলে গেল, ফেলে গেল গভীর সংকটে—এক. পরিচয়ের সংকট, দুই. যতদিন দেশ আছে ততদিন বহন করো নিজেদের ভাতৃহত্যার গ্লানি। এই ভারতের আর কোনো ইতিহাস তারা রেখে যায় নি। পাক-বাংলা সরকার আমায় পেতে চায়, পাকিস্তানি কায়দায়। ব্রিটিশ-রাজ আমার কিছু বই বাজেয়াপ্ত করেলেও গোলাম মোস্তফার মতো পাকিস্তানি কবিবন্ধুরা চায় প্রতিটি বইয়ের মুসলিম সংস্করণ প্রকাশ করে পরিশুদ্ধ করতে। শুনেছি আমার কবিতা ইতোমধ্যে পাকিস্তানের পুস্তক-ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে মতো পরিবর্তন পরিবর্ধন করে প্রকাশ করছে। আমার পরিবারকে রয়ালিটিও দিচ্ছে না।
তারা আমার সাহিত্যের কর্তন করছে এই ভেবে যে, আমি পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই নি। চাইলেও সম্ভব ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেধেছিল চল্লিশের পরে, তখন থেকে আমার লেখার আর সামর্থ্য নেই, তার আগে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান মিলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল। আমার সাহিত্য সেই যুগের রচনা। সুতরাং খণ্ডিত দেশে আমার সাহিত্য খণ্ডিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
যদিও অন্নদাশঙ্কর রায় লিখল: ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল।’
অন্নদাশঙ্করের লেখাটি আবদুল কাদিরের ‘মাহে নও’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ‘নও বাহার’-এ এই অখণ্ডতার প্রতিবাদ করল। ‘নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই নজরুল যা নয়, তাঁর উপর তাই আরোপ করিলে তাঁকে হেয় করা হয়।’ আজ ভাবি, আমার বন্ধু মোস্তফা অন্তত আমায় অনেক অপবাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।
‘নও বাহার’ লিখল, অগ্নিবীণার ‘ভেতরে ৭টি ইসলামী ভাবাপন্ন, বাকি ৫টি (প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী ও ধূমকেতু) ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাজেই আমাদের মতে এগুলি বর্জন করতে হইবে।’
‘বিষের বাঁশী’তে মোট ২৫টি কবিতা। তন্মধ্যে একমাত্র ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম’ ছাড়া বাকি সবগুলো কবিতা ও গানই ভারতীয় টেকনিকে লেখা।’
অন্নদাশঙ্করের নির্ভাগ তত্ত্ব এখানে খাটছে না। যে বিদ্রোহী লেখার কারণে আমি কাজী নজরুল ইসলাম সেই বিদ্রোহী চলে গেল ভারতের ভাগে। এবার বিভক্ত ভারতে বিদ্রোহী ভৃগুর কী অবস্থা হতে পারে!
অবশ্য বিপরীত যে ছিল না, তা নয়। মওলানা আকরম খা’র ‘মোহাম্মদী’ এক সময় আমার বিরোধিতা করলেও, ‘পাকিস্তান আজাদ’ যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আকরম খাঁ এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ, ধর্ম ও যুক্তিশীলতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মওলানা হলেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা তেমন চালিত নয়। তিনি মুসলিম সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও শিল্পসাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে যুগসন্ধিক্ষণের কাজ করেছিলেন। প্রাচীনতা ও আধুনিকতার মিশেল মানুষ।
দেশবিভাগের ফলে আমার পরিবার নতুন করে অর্থকষ্টের শিকার হয়। রাজ্য-সরকার আমার মাসিক ব্যয় দুশ টাকা থেকে কমিয়ে একশ পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণ করেছে। যুদ্ধ মন্বন্তর দেশভাগের ফলে দেশে যে চরম মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, আমার মতো পঙ্গু কবির কাছে থেকে পঞ্চাশ টাকা কর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে।
অবশ্য হাবীবুল্লাহ বাহারের চেষ্টায় পূর্ব-পাকিস্তান সরকারও আরো একশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাতা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু সে টাকা আমার পরিবার পাচ্ছে না। এক দেশের টাকা অন্য দেশে আসা সহজ নয়—যদি বৈধ পথে হয়। দেশ ভাগ হলেও টাকার গোপন লেনদেন কমে নি। শুধু রাষ্ট্রের নির্দেশিত পথে একশত পঞ্চাশ টাকা দুস্থ কবির জন্য কোনো ভাবেই আসা চলবে না।
সানি ঢাকায় গিয়েছিল, অনেক ঘোরাঘুরি ক’রে এ যাত্রা বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। বাহারও নাকি কিছু করতে পারে নি। আসবে হয়তো নিয়মতান্ত্রিক পথে, আসতে সময় লাগবে।
এ দিকে আমার নামে সরকারি বাড়ির বরাদ্দ বাতিল হয়েছে। ১৬ নম্বর রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের ছোট একটি বাড়িতে আমায় ওঠানো হয়েছে। পাগল মানুষ, আমার জন্য একটু বেশি জায়গা দরকার। বন্দি করে না রাখলে ঘোরাঘুরি করতে একটু বেশি জায়গা লাগে।
এই বাসাটি আমার জন্য যে খুব কষ্টকর হয়েছে, সে-ব্যাপারে ‘দৈনিক আনন্দ বাজার’, ‘দৈনিক অমৃত বাজার’ খবর প্রকাশ করছে। নজরুল সুহৃদ সংগঠনগুলো যদিও আমায় একটু শান্তিতে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর।
প্রমীলার পাশেই আমি প্রায় সারাদিন শুয়ে-বসে থাকি। আমাদের দুজনের খাট এখন পাশাপাশি।
আমার শাশুড়ি চলে যাবার পরে সংসারের মূল দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রমীলার উপর। প্রায় এক যুগ প্রমীলা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। যখন সুস্থ ছিল তখন এ সংসারের সকল ঝাপটা তার মা গিরিবালা দেবী এক হাতে সামলেছে। কখনো তাকে নিজে কিছু করতে হবে সেটা হয়তো ভাবনাতেই ছিল না। ও অসুস্থ হওয়ার পরেও ঘটে নি সংসারের তেমন ব্যত্যয়। সবকিছু আগের মতো চলছিল। তবে আমার অসুস্থতা এক ঝাপটায় সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে যায়। অসুস্থ কন্যা, অসুস্থ জামাই, ছোট ছোট দুটি নাতি নিয়ে তিনি ভালোই সামলিয়ে আসছিলেন।
সব মেয়ের মধ্যেই থাকে সংসারের সহজাত দক্ষতা, ছোট বড় বৃদ্ধ বা পঙ্গু হলেও সেই সংসারী নারীর গুণাগুণ নষ্ট হয় না। প্রমীলা তার উদাহরণ। সে খাটে শুইয়েই সব কিছু সামলে নিচ্ছে। এমনকি তরকারি কুটা, চা বানানোর মতো কর্মকাণ্ড সে বিছানায় শুয়ে কাত হয়ে দিব্বি চালিয়ে নিচ্ছে। শাহু, কাটিয়া—কে কখন কী করবে বিছানায় শুইয়ে তার নির্দেশ দিচ্ছে প্রমীলা। রান্না-বান্নায় কাটিয়া বেশ দক্ষ। আমার গোসল, খাওয়া প্রমীলা ঠিক সময় মতো তদারকি করে।
প্রমীলার পাশেই আমি প্রায় সারাদিন শুয়ে-বসে থাকি। আমাদের দুজনের খাট এখন পাশাপাশি। আমি আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে এসেছি। আমার নিয়তিকে নিয়েছি মেনে। আমি যে ধ্যানের স্তরে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম, সে স্তরে পৌঁছালে কেউ ফিরে আসে না, সেটা আমি ধ্যানের প্রথম পর্যায়ে বুঝতে পারি নি। আমি তো তা-ই চেয়েছিলাম। ‘আমি যুগ যুগ ধরে লোকে লোকে, যে প্রভুরে খুঁজে ফিরছিলাম, তার সন্ধান আমি পেয়েছি। আমার আর কোনো বিকার নেই, আর কোনো তাড়া নেই। সংসারে থেকেও আমি মহাস্থবির যোগী। প্রমীলার পাশে শুয়ে থাকি আর বিস্ময়ে তাকে দেখি, ভাবি বিধাতা কিভাবে আমাদের এতটা কাছাকাছি রেখেছে। যাকে পাওয়ার জন্য কত উতলা ছিলাম, অথচ তাকে কখনো দিতে পারি নি সময়। কিন্তু আমি আমার ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছি—আমার আশালতা ওরফে দুলির জন্য। ওর অসুস্থতা জয় করার জন্য আমি গিলগামেশের মতো মহাকাল পাড়ি দিয়েছিলাম, আমি জয়ও করেছিলাম, ভুলও করেছিলাম—তাই পুরোপুরি তাকে সুস্থ করে তুলতে পারি নি। তার আর ক্ষতি হতে দিই নি। সেই থেকে তাকে এক মুহূর্তের জন্য কাছ ছাড়া করি নি। মনে মনে গুনগুন করি, কেউ শুনতে পায় না। আমি বাকরুদ্ধ হওয়ার পর প্রথম সত্য চৌধুরী যে গানটি রেকর্ড করেছিল, সেটিই বেশি গাই—
‘মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে॥’
দেশ ভাগের ধাক্কায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। বন্ধু-বান্ধব ভক্তকুল এতদিন অনেকটা ভুলেই ছিল। সরকারের পক্ষ থেকেও আমার চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় নি কোনো উদ্যোগ। ড. বিধানচন্দ্র রায় এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আমার অসুস্থতা সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত থাকলেও তার পক্ষে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। তাকে দেশবিভাগের উদ্ভূত নানা পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে। বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের আবাসন সমস্যা মোকাবেলা তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অবিভক্ত বাংলায় কোলকাতা রাজধানী হলেও সরবরাহ ব্যবস্থা যুক্ত ছিল পূর্ব-বাংলার সঙ্গে, হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অনেক কিছু নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে। পাটশিল্পের কাঁচামাল, খাদ্য ও দুধের চাহিদা মেটাতে নতুন করে কাজ করতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় এইসব গুরুদায়িত্ব পালন করে এখনো দিনে এক বার রোগী দেখছেন। অবিমিশ্র সুনাম তার জন্য এখন আর অবশিষ্ট নেই। ওপার থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের চাপ সামলাতে এপারের মুসলমানদের প্রতি ভেতরে ভেতরে তিনি বিরূপ হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। শুরুর দিকে ড. বিধান রায়ের পেনিসিলিন চিকিৎসার পরে আবারও হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদি দিয়ে আমার চিকিৎসা চলছিল।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নতুন করে ‘নজরুল সাহায্য সমিতি’ গঠিত হয়েছে। এই সমিতির সভ্যরা হলেন আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন, আবদুল ওদুদ, এস.এ. মাসুদ এবং রামচন্দ্র অধিকারী। শ্রীকুমার ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ লিখে খুব নাম করেছিল।
এর কিছুদিন পরে আমার তিপান্নতম জন্মোৎসবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুল ওদুদ মিলে ‘নজরুল পাঠাগার’-এর পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়। তারাশঙ্কর ও শ্রীকুমার দুজনই বীরভূম জেলার মানুষ।
তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ মিল ছিল—আমারও ডাক নাম তারাক্ষ্যাপা। দেবী তারার ভক্ত বামাক্ষ্যাপার আশীর্বাদে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম বলে আমায় অনেকে তারাক্ষ্যাপা বলে ডাকে। তারাশঙ্করেরও নামের ইতিহাস এমন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বামাক্ষ্যাপাকে দেখার জন্য তারা পিঠে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় বামাক্ষ্যাপা মহর্ষিকে বললেন—
‘ফেরার পথে ট্রেন থেকেই দেখতে পাবে একটা বিশাল মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে আছে একটা ছাতিম গাছ। তার নিচে বসে ধ্যান করবে। দেখবে মনের ভিতরে আনন্দের জ্যোতি জ্বলে উঠছে। ওখানে একটা আশ্রম বানাও দেখি। আহা, শান্তি শান্তি!’
ফেরার পথে সেই মাঠ এবং ছাতিম গাছ দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন। সেখানে বসে ধ্যান করলেন। ঠিক করলেন তিনি এখানে আশ্রম স্থাপন করবেন। এটিই আজকের শান্তিনিকেতন। তারাক্ষ্যাপার মন্দিরে আমিও গিয়েছিলাম।
তারাশঙ্করের সাথে পরিচয় আমার বেশি দিনের নয়। তার বাড়িতে এক রাত্রি যাপনের আগে আমদপুর রেলস্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল। নলিনীদার সঙ্গে যেদিন আমি তার বাড়িতে যাই সেদিনই তার এক পুত্র মারা গিয়েছে। এই অবস্থায় তার বাড়িতে কিছুতেই থাকা উচিত হবে না। অন্দরে মেয়েদের শোক প্রকাশের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হবে। তারাশঙ্কর কিছুতেই আমাদের বাইরে থাকতে দিলেন না। তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তা বোঝার জন্য তার ‘অগ্রদানী’ গল্পটি পাঠ করা জরুরি। আজ তার পুত্রবিয়োগের শোকের মধ্যে যখন তার বাড়িতে থাকতে হলো, তখন আবার অনুভব করলাম এই মানুষটির সাধক সত্তা, নিস্পৃহ ‘অগ্রদানী’।
আমি গিয়েছিলাম মূলত তার লাভপুর গ্রামের পাশে ‘বেল’ গ্রামের ধর্মঠাকুরের কাছে—প্রমীলার পক্ষাঘাতের ওষুধের জন্য। বেলের এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও তেল বহুকাল থেকে বাতের ওষুধ হিসাবে সুপরিচিত ছিল। আমার জন্মস্থান বর্ধমান এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, ছোটবেলা থেকেই আমি শুনে আসছিলাম এর খ্যাতি। বহু স্থান থেকে লোক আসত। বহু ডাক্তাররাও এই তেল ব্যবহার করত। নিশ্চয় কিছু গুণাগুণ ছিল।
তারাশঙ্কর অবশ্য আমাদের আগে জানায় নি যে তার ছেলে মারা গেছে। আমরা জানলে হয়তো তার বাড়িতে থাকতে রাজি হতাম না।
আমরা তার পুত্রবিয়োগের দিনে রাত ন’টায় লাভপুর স্টেশনে নামলাম। সেদিন ছিল শনিবার। রোববার ধর্মঠাকুরের বিশেষ দিন।
তারাশঙ্কর লিখেছে, ‘আমার আগ্রহে ও অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমার ওখানেই এলেন। রাত্রে থাকলেন। সকালে ট্যাক্সি করে বেলে গিয়ে দুপুরে ফিরে এসে আহারাদির পর বললেন, “রাত্রে আসন পাতো। গান গাইব।”
বিকেলে আমাদের ওখানে ফুল্লরা মহাপীঠে গিয়ে দেবীর মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে পদ্মাসন হয়ে বসে কাজী সাহেব প্রাণায়াম যোগে জপ শুরু করলেন। দেখতে দেখতে মনে হ’ল মানুষটা নিস্পন্দ বা সমাধিস্থ হয়ে গেছে। কুম্ভকে এতক্ষণ অবস্থান খুব বড় যোগী ভিন্ন সম্ভবপর নয়। সমস্ত শরীরে ঘামের বন্যা বয়ে গেল। যখন জপ সেরে উঠলেন তখন চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল, এবং তখনো ঠিক যেন জাগ্রত চেতনায় ফেরেন নি। সেই অবস্থাতেই একখানি গান রচনা করে সুর দিয়ে দেবতাকে এবং সমবেত লোকদের শুনিয়ে বাড়ি ফিরলেন।
তারপর সন্ধ্যায় বসল গানের আসর। লোকে লোকারণ্য সৃষ্টি হলো। স্থানীয় মুসলমানরা এসেছিল দলে দলে। তাঁরা ইসলামি সংগীত শুনতে চেয়েছিল। তিনি গাইলেন। রাত্রির মধ্যখানে গেয়েছিলেন শ্যামাসংগীত। সে-সময়ে আশ্চর্য ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তার মধ্যে কবি ও ভক্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের সাধক ও মহাজনকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।
আমার হৃদয়ে সন্তান-বিয়োগ বেদনার নিঃশেষ উপশম হয়েছিল এমন কথা বলব না, তবে তার উপর যে তিনি আনন্দ শ্বেতচন্দনের একটি স্নিগ্ধ-শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। এ শতবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলব।’
তারাশঙ্কর সারাজীবন এই রাতের ঘটনা ভুলতে পারেন নি। তার কাছে মনে হয়েছিল, তার পুত্রহারা হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ বোলাতে ভগবান আমাকে ওই দিন পাঠিয়েছিল। তিনি সেদিন থেকে এটি বিশ্বাস করতেন, কাজী নজরুল ইসলামই ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত বাংলা।
শেষ পর্যন্ত আমায় রাঁচি যেতে হলো চিকিৎসার জন্য। অসুস্থতার প্রথম পর্যায়ে রাঁচি মানসিক আশ্রমে যাওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশে ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দে ও ডাক্তার মোহম্মদ হোসেন সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেলেছিল। প্রমীলা ও আমার শাশুড়ির রাজি না হওয়ায় সে-যাত্রায় সম্ভব হয় নি। রাঁচির বদলে তখন লুম্বিনীতে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। অনেকের ধারণা সেই সময় রাঁচিতে গেলে আমার মানসিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারত।
রাঁচি বিহারের ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শহর। আমার জন্ম-জেলা বর্ধমানের দূরত্ব কোলকাতা থেকে কম। আমি এর আগে বহুবার দেওঘর, সমস্তিপুর, মধুপুর এলাকায় থেকেছি। তাছাড়া রাঁচি আমার ভারতবর্ষের অন্যতম প্রিয় শহর। কারণ ব্রিটিশবিরোধী বীর বিরসামুণ্ডার জন্মস্থান। মাত্র বিশ বছরের এক তরুণ বিশ শতকের সূচনা লগ্নে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভুদের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। তার উপরে ঐশ্বরিক শক্তি ভর করেছিলেন, মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যে মুণ্ডারা তাকে বিরসা ভগবান হিসাবে মনে করতে শুরু করে। বিরসা ইংরেজ পার্দিদের স্কুলে পড়তে গিয়ে বুঝেছিল, ইংরেজের ঈশ্বর তাদের নিজস্ব ঈশ্বর। মুণ্ডাদের জন্য সে ঈশ্বর কিছু করে না। মুণ্ডাদের হাতে বাইবেল ধরিয়ে দিয়ে তাদের জমি কেড়ে নেয়। তাদের নিজেদের নাম পরিবর্তন করে গোমেজ বা কস্তা লাগিয়ে দেয়। আর তাদের কেবল শান্তির বাণী শোনায়। বলে, তোমাদের এক গালে চড় মারলে তোমরা আরেক গাল পেতে দেবে—কখনো প্রতিবাদ করবে না।
ডাক্তারদের পরীক্ষা অনুসারে প্রমীলার রোগের উৎপত্তিস্থল মেরুদণ্ড থেকে, আর আমার মস্তিষ্ক থেকে।
ফাঁসির আগের রাতে পঁচিশ বছর বয়সী এই মুণ্ডাবীরকে ব্রিটিশ জেল-পুলিশ রাতের খাবারে বিষ প্রয়োগ করে। তার শতাধিক সাথির কাউকে ফাঁসি, কাউকে দীর্ঘমেয়াদি কারাবাস ও দ্বীপান্তরে পাঠায়।
রাঁচি মানসিক হাসপাতালে আমায় পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য, সঙ্গে প্রমীলাও আছে। চিকিৎসা কী হবে তা আমার জানা আছে, কারণ দুনিয়ার সচরাচর রোগীর সঙ্গে আমার পার্থক্যটা ডাক্তারের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমার ভালো লাগছে এই কথা ভেবে নিম্নবর্গের এক মুক্তি-শহিদ বিরসা মুণ্ডার স্পর্শিত ভূমিতে আসতে পেরে। এটি আমার জন্য তীর্থভূমি। আমায় ভর্তি করা হয়েছে তিন নম্বর কটেজে। ডাক্তার ডেভিস রসের অধীনে। এখানে আমাকে জেনারেল প্যারেসিস এবং ইনভলিউশনাল সাইকোসিস ধরে নিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। প্রথমে ওষুধ ছাড়াও পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসায় কোনো ফল না হওয়ায় পনেরোটি রাসায়নিক শক দিয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে ইলেক্টিক শকও দেয়া হয়। আমার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ডাক্তার ঝুঁকি নিতে চায় নি।
ডাক্তারদের ভাষ্যানুসারে এতে নাকি আমার কিছুটা উপকার হয়েছিল। বিছানো ভেজানো কমে গিয়েছিল। নিজে নিজে টয়লেটে যাবার তাগিদ দেখিয়েছিলাম। দুএকটি শব্দ এবং একটি পুরো বাক্যও নাকি উচ্চারণ করেছিলাম। এখানেও প্রমীলার রোগের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আছে কী না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। ডাক্তারদের পরীক্ষা অনুসারে প্রমীলার রোগের উৎপত্তিস্থল মেরুদণ্ড থেকে, আর আমার মস্তিষ্ক থেকে। ফলে একজনের সঙ্গে আরেকজনের রোগের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।
রাঁচি অ্যাসাইলামে বেশি দূর এই চিকিৎসা এগোয় নি। যেহেতু আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য নজরুল নিরাময় কমিটি আমায় ইউরোপে পাঠানোর কথা ভাবছে, সেহেতু চার মাসের মাথায় রাঁচি থেকে কোলকাতায় ফিরে আসি।
তবে আমার কৌতূহল রয়েছে রাঁচি অ্যাসাইলামে সেদিন আমি কোন বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলাম, ১৫টি রাসায়নিক শকের পরে। অ্যাসাইলামের ডাক্তার নার্সরা এ ব্যাপারে কিছু বলে নি। মনে হয় সেদিন বলেছিলাম—
‘গেছে দেশ দুঃখ নেই, আবার তোরা মানুষ হ।’