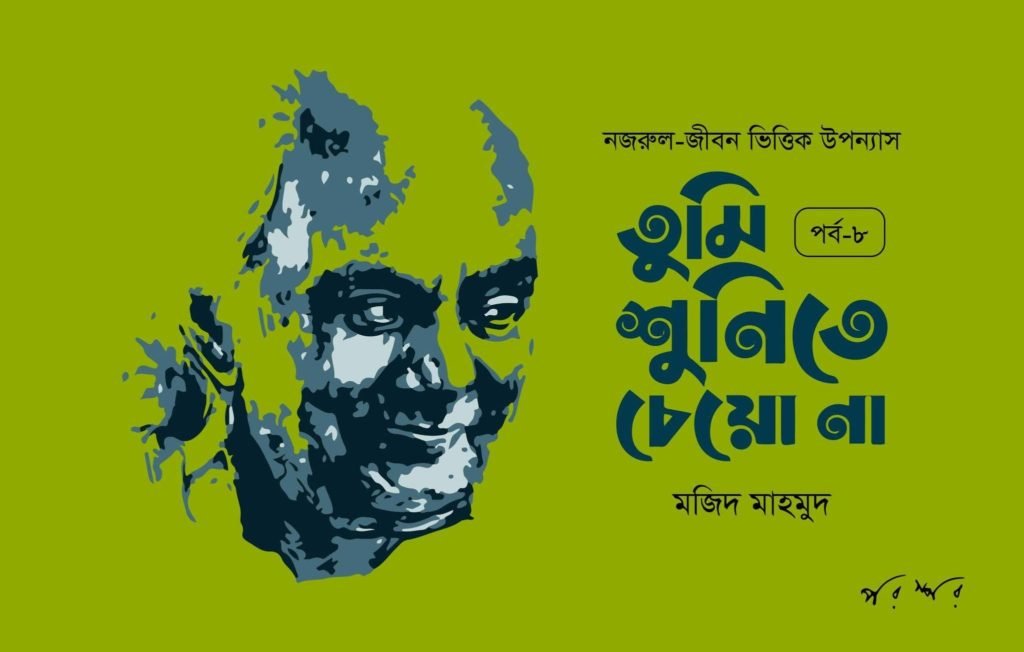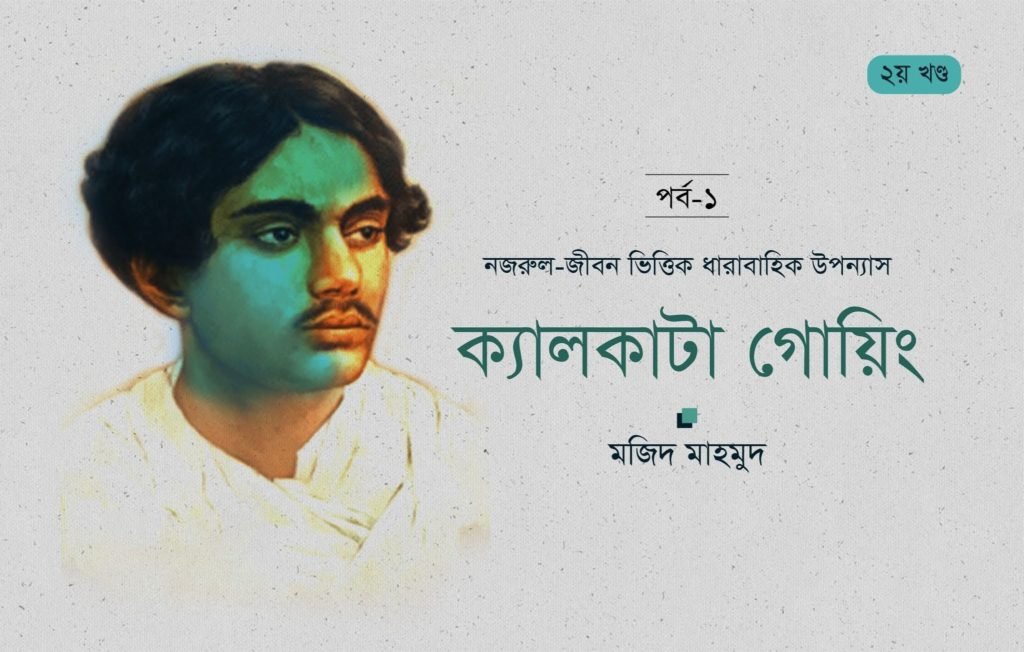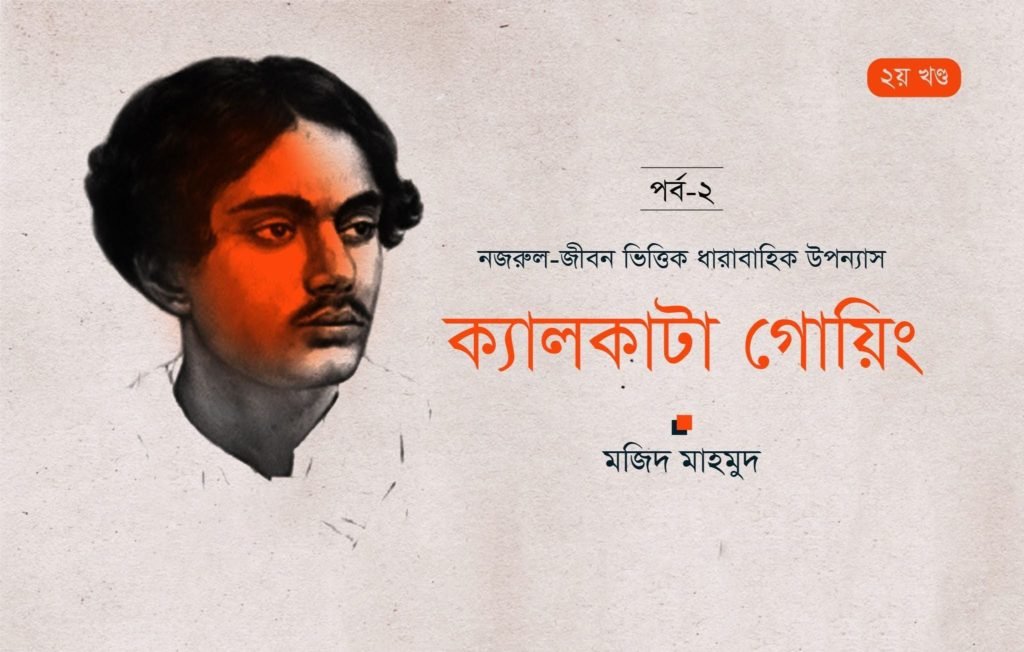পর্ব-৮
আজ ৮ জুন ১৯৫৩ সাল, আমি লন্ডনে এসে পৌঁছালাম। সুস্থ অবস্থায় লন্ডনে আসতে পারি নি। বেড়াতে আসারও সামর্থ্য ছিল না—লেখাপড়ার জন্য তো নয়ই। আমি যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছি, যাদের কর্মে ও দর্শনে আকৃষ্ট ছিলাম, তাদের অনেকে লন্ডনের স্কুলে পড়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ—আমার গুরু হলেও তাদেরও প্রধান পাঠ ছিল এই লন্ডনে। গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরু এই সব জাতীয় ব্যারিস্টার নেতাদেরও লন্ডনে আসতে হয়েছিল—তাদের কারখানার মাপে নিজেকে তৈরির জন্য। আমি যখন দীলিপের কাছে, হেমন্তের কাছে, সুভাষের কাছে লন্ডনের গল্প শুনতাম, তখন নিজেকে খুব বাইরের লোক মনে হতো। মনে হতো এই সব মানুষের ভিড়ে আমি কতই না বেমানান।
সবাই লক্ষ করেছে—কোনো আসরে আমি নিজের গানে, নিজের কথায়, নিজের হাসিতে মশগুল থেকেছি, অন্যকে ব্যস্ত রেখেছি। অন্য কারো কথা শোনার ফুরসত খুব কমই ছিল আমার, ইচ্ছেও ছিল না। গান ছাড়া কবিতা ছাড়া ওদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আমার আর কোনো উপায়ও ছিল না। গুরুর মতো বলতে ইচ্ছে করত—‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/ নইলে মোরা রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?’ নিজেকে রাজা মনে না করলে আমার মতো নিম্ন-শ্রেণির প্রজা ওদের মতো জমিদার-নন্দনদের সঙ্গে কিভাবে মিশত। আমার বন্ধুরা অধিকাংশ যুগপৎ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সঙ্গে যুক্ত থেকেও কিছুটা ব্রিটিশের স্বার্থ-রক্ষা করতে পেরেছিল। প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ দর্শন ও ব্রিটেনের ইশকুলে অধ্যায়ন—দেশটির প্রতি তাদের কিছুটা নমনীয় করে তুলেছিল। আমার ইংল্যান্ডের প্রত্যক্ষ কোনো স্মৃতি অভিজ্ঞতা না থাকায়, ইংরেজের বিরোধিতায় ভেজাল ছিল না। আর তার দাম ইংরেজ সরকারও দিয়েছিলেন ঠিক মতো, পর পর ছয়টি গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে, জেলে পুরে। একটু মজা করেই লিখেছিলাম, ‘বন্ধু! তোমরা দিলে না কো দাম,/ রাজ-সরকার রেখেছেন নাম!’
ইংরেজের প্রথম যুগে যে তিনজন বাঙালি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই সংস্কৃতির আত্তীকরণে কাজ করেছিলেন, এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারা দেশের মাটিতে শেষ ঠাঁই পান নি।
লন্ডনে পড়তে আসতে না পারায় আমার মধ্যে যে দুঃখবোধ ছিল না—তা নয়। প্রবোধ দিয়েছি—কোটি কোটি ভারতবাসীর কয়জনই বা লন্ডনে আসতে পেরেছিল। আমরা যে যুগে বাস করেছি—সেই যুগ লন্ডনের হয়ে ভারতীয়রাই তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক নীতিবোধ। কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ—সেটিও তাদের বাটখারাতেই মাপা হতো। তবু ভেতরে একটা গণ্ডগোল যে কোথাও হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। একটা প্রশ্ন আমার মনে সর্বদা নাড়া দিয়েছে—এই যে ইংল্যান্ড দেশীয় মানুষ আমাদের দীর্ঘদিন শাসন করছে, শোষণ করছে, ইংল্যান্ডের রানি ভারতেরও রানি, তবু আমরা দুই দেশের বাসিন্দা—এটার নামই হয়তো উপনিবেশ। একটি দ্বিধা আমার মনে সব সময় ছিল—ভারতবাসী ভারতে থেকে ইংরেজ জাতির উপরে যত না ক্ষিপ্ত হয়েছে, ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করতে এসে তারচেয়ে অনেকে বেশি ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে দেশে ফিরেছে। কী এমন ঘটেছে—যে কারণে তারা নিজ দেশে গিয়ে শাদা চামড়ার মানুষদের মেরে তাড়াতে চেয়েছে! এমনকি সরাসরি তাদের হত্যা করেছে! আঘাত করার জন্য গোপন দল গড়ে তুলেছে। অনুশীলন, যুগান্তরের মতো দল, ব্রিটিশের খাতায় যারা সন্ত্রাসী, তাদের অধিকাংশ মাস্টার মাইন্ডের জন্ম এই বিলাত শহরেই।
যারা বিলাত গিয়ে দেশে ফিরে বিলাত-বিরোধী হয়েছে, তাদের নিয়ে আমার কিছু সংশয় ছিল, মনে হতো তাদের দেশপ্রেমে কিছু ভেজাল মিশে থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা ইংরেজ-শাসন প্রলম্বিত হয়েছে। বিশেষ করে অরবিন্দসহ অনেকে তথাকথিত দেশদ্রোহী মামলায় শেষমেষ সাজার ভয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন দূরদেশে। হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্যটাও তো তারা স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করে দিলেন, হিন্দু-ভারতের একটা চরিত্র নির্মাণ করতে চাইলেন। তারা যাদের এ পথে নামিয়ে ছিলেন—তারা অনেকে ব্রিটিশের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে, জেলে পচে মরছে, গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তাদের অনেকের ঘর করা হয় নি, প্রিয়জনের মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নি। কত জীবন অকালে এই ভারত মাতার জন্য ঝরে গেছে, পথের ধুলায় তাদের নাম মুছে গেছে।
প্রথম যুগে যারা বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়েছিলেন, তারা রক্তে-মাংসে ভারতীয় হলেও মস্তিষ্কে কিছুটা ইংল্যান্ডীয় ছিল। কবিগুরুর বাবা ভারতীয় মহর্ষির আদলে নিজেকে নির্মাণ করাতে পারলেও, তার আগে ঠাকুর্দা লন্ডনে প্রিন্স খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনিই ভারতে প্রথম ইংরেজের ‘জাস্টিস অব দ্য পিস’—অন্তত সিপাহি-বিদ্রোহে ইংরেজের অশান্তির কারণ না হয়ে। রানি ভিক্টোরিয়া, প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পিল তাকে রাজকীয় সম্মান প্রদান করেছিলেন। পরম প্রভুর ইচ্ছে বোঝা দায়—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কবরও রয়েছে এই ইংল্যান্ড শহরে। লন্ডনে প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর উনত্রিশ দিন পরে ঠাকুর পরিবারের কাছে সেই খবর পৌঁছায়। তখন বোম্বে বা পুনে থেকে পানি-পথে এখানে আসতে কমবেশি একমাস সময় লাগত। ইংরেজের প্রথম যুগে যে তিনজন বাঙালি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই সংস্কৃতির আত্তীকরণে কাজ করেছিলেন, এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারা দেশের মাটিতে শেষ ঠাঁই পান নি। শেখ দীন মুহম্মদের হয়তো ফেরারও ইচ্ছে ছিল না, জাতধর্ম খুইয়ে মেম বিয়ে করে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহন, দ্বারকানাথের সে ইচ্ছে না থাকলেও শেষ বিচারে ফেরা হয় নি। তাদের বলতে হবে বিলাত-তীর্থের প্রথম শহিদ।
কবিগুরুর মতো আমিও বোম্বে থেকে ‘জল আজাদ’ জাহাজে লন্ডনে এসেছি, অবশ্য তাঁর জাহাজের নাম ছিল ‘পুনা’। মে মাসের দশ তারিখে রওনা দিয়ে জুন মাসের আট তারিখে পৌঁছেছি। জাহাজের গতি শত বছরে প্রায় একই আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় একশত আট বছর পরে আমার লন্ডনে আসতে একদিনও কম লাগে নি। তবে এখন বিকল্প উড়োপথে একদিনের লন্ডন থেকে কোলকাতায় পৌঁছানো সম্ভব। খরচ কিছুটা বেশি হওয়ায় আমাদের জলপথে আসতে হয়েছে। নিরাময় কমিটি নানা চেষ্টা করেও সাতাশ হাজার টাকার বেশি সংগ্রহ করতে পারে নি। পাঁচ জনের কয়েক মাসের ইউরোপ যাত্রার জন্য তখনকার দিনেও টাকাটি বেশ অপ্রতুল। রাহা-খরচ বাদেও পক্ষঘাতগ্রস্ত প্রমীলা ও আমার চিকিৎসার খরচও এর মধ্যে ধরা ছিল। লন্ডনের ‘নজরুল নিরাময় কমিটি’ কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
‘নিরাময় কমিটি’ বিদেশে আমার উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। হুমায়ূন কবির কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাওয়ার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা সহায়তার ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছে। হুমায়ূন বর্তমানে মৌলানার সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। মৌলানার মৃত্যুর পরে সে নিজেও শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছিল। হুমায়ূন কবিরের লন্ডনের ছাত্র-জীবনও খুব বর্ণাঢ্য ছিল। দেশবিভাগের পরের বছর জীবনানন্দ দাশ তার ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থটি হুমায়ূন কবিরকে উৎসর্গ করে। জীবনানন্দ দাশ আর আমি একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের জানাশোনা তেমন ছিল না। আমি অসুস্থ হওয়ার পরে সে আমার কবিতা নিয়ে বেশ কয়েকটি গদ্য রচনা করেছিল, সেটা না লিখলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। তার লেখার মূল সুর কাজীর কবিতায় ‘মহাকাব্যিক গভীর প্রসাদ নেই, প্রতিশ্রুতিও কম।’ এই অবিমৃশ্যকারিতা, দলবদ্ধ প্রচারণা, নিজেদের রুচিমাফিক পাঠক তৈরি—তিরিশের ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রবণতা। তবে আমার মতো সেও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে, সজনীকান্ত আমায় যেভাবে নাজেহাল করেছে, তাকেও কিছু কম করে নি। আমায় নিয়ে জীবন-বাবুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ লেখা ছাপার ফলে ‘স্বরাজ’ পত্রিকা তাকে চাকরিচ্যুত করে। আমি সুস্থ থাকলে এটি কখনো হতে দিতাম না।
কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তিন হাজার টাকা, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছয় হাজার তিনশ টাকা, অতুলচন্দ্র গুপ্তের ছাব্বিশ শ টাকা, বাকি বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা থেকে পাঁচশ টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া যায় । অতুলচন্দ্র সরকার টাঙ্গাইলের বিল্লাইক গ্রামের মানুষ। কোলকাতায় আইন ব্যবসায় প্রসার লাভ করেছিলেন, ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’র লেখক হিসাবেও তার সুনাম ছিল, মনটিও বড়।
ইংল্যান্ডে আমার সঙ্গী হয়েছে প্রমীলা, অনিরুদ্ধ, নজরুল নিরাময় সমিতির সহসম্পাদক ড. রফিকউদ্দীন আহমদ আর দেখভাল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক মিস ললিতা ঘোষ। সুবিধা হয়েছে ডা. অশোক বাগচী আমাদের সঙ্গে ভিয়েনা যাচ্ছে। অশোক ভিয়েনাতে উচ্চতর চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করছে। সে সঙ্গে থাকায় আমার পরিবার বেশ নিশ্চিন্ত। অশোক গানবাজনা ভালোবাসে, গান শুনে রাস্তায় থেমে পড়ে। ইতোমধ্যে বেশ কয়টি বইও লিখেছে। সুস্থ অবস্থায়ও সে আমায় চিনত। কোলকাতার অখিল মিত্র লেনে একবার সরাসরি গান শুনেছিল। তার ভাষ্যানুসারে, আমি সেখানে গেয়েছিলাম ‘বাগিচার বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস নে আজি দোল’, ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।’ অশোকের কথায়—‘গান শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এত অভিভূত যে, এত বড় একটা সেক্যুলার পারসোনালিটি কখনো দেখে নি।’… ‘যখন রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করি তখন অনিবার্যভাবে নজরুলের নামও চলে আসে।’
অশোক পাবনার বিখ্যাত বাগচী পরিবারের সন্তান। ড. বিধানচন্দ্র রায় তার ঠাকুর্দার ছাত্র, আবার আশোকের বাবাও বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে কিছুদিন পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিধানচন্দ্র রায় ও অশোক বাগচীর পরিবারের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। আবার মাতুলের দিক থেকে সে রংপুরের তুলসী লাহিড়ী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। তুলসী লাহিড়ীই তাকে বলেছিল, ‘অশোক, তুই ভিয়েনা যাচ্ছিস, তো নজরুলকে নিয়ে যা।’
তুলসী লাহিড়ী আমার সময়ে সংগীতে-নাটকে অন্যতম প্রধান প্রতিভা। শিল্পের টানে বংশমর্যাদা উপেক্ষা করে, ওকালতি ব্যবসার পসার ছেড়ে সংগীত ও নাটকে নিমজ্জিত হয়েছিল। জনগণের লেখক বলতে যা বোঝায় তুলসী ছিল তাই। তার ‘এল কাল পঞ্চাশের আকাল’ কিংবা ‘বাংলাদেশের কাঙ্গাল চাষী ভাই’ এখনো কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে পাওয়া যায়। কমলা ঝরিয়ার সাথে দ্বিতীয়বার ঘর বাঁধাও তুলসীর শ্রেণিপাতের প্রতি অনাস্থার প্রমাণ। জমিদারের ছেলে বাইজি বিয়ে করায় দুর্নাম সইতে হয়েছে অনেক। দুর্ভাগ্য এখন ওর নাম প্রায় অনুচ্চারিত। ওর অনেক গান আমার গানের সঙ্গে মিশে গেছে। কমলা এক সময়ে আমার গান গাইত, পরে তুলসীর গানই গেয়েছে।
কমলার ‘ঝরিয়া’ নাম আমারই দেয়া। সে সময়ে কমলা ভট্টাচার্য, কমলা দেবী, কমলা পট্টাধর, কমলা চট্টোপাধ্যায় নামে গানের আরো শিল্পী ছিল। বিহারের ঝরিয়া অঞ্চল থেকে এসেছিল বলে হিজমাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ডের গায়ে আমার পরামর্শে ঝরিয়া লাগানো হয়। এই পদবি তার পরিচয়ে সবার থেকে আলাদা করেছিল। তুলসীর সঙ্গে ওর জীবন বেশ সুখের ছিল, তুলসীকে ও সত্যিকারে ভালোবাসত, তুলসীও ওর জন্য ঘর ছেড়েছিল। তবে বাইজি বলে অনেকে ঘর ভাড়া দিতে চাইত না। তুলসী মারা গেলেও সে বাকি জীবন তুলসীর স্মৃতি ধরে ছিল।
আমাদের বহনকারী জাহাজ বোম্বে থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছাল ২৪ মে। জাহাজের সবাই জেনে গেছে, কাজী নজরুল ইসলাম এই জাহাজে লন্ডন যাচ্ছেন—চিকিৎসার জন্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক যেমন ছিল, বাংলাদেশেরও কয়েকজন যাত্রী এই জাহাজে লন্ডন যাচ্ছিল। সঙ্গে প্রভাত নামের এক যুবক লন্ডনে যাচ্ছে পড়াশোনার জন্য, ভালো গান গাইতে ও বাজাতে পারে। ড. অশোক বাগচীও ভালো গায়। পিয়ানো বাজিয়ে অনিরুদ্ধ কোলকাতার সুধীমহলে ইতোমধ্যে নাম করেছে। একই জাহাজে ভ্রমণ করছে মিসেস পিয়ার্সন নামে এক মহিলা, সেও খুব ভালো পিয়ানো বাজায়। প্রমীলাও গাইতে পারে, আমি শুধু নির্বাক শ্রোতা। শ্রোতা হলেও নিজের গান ভালোই বুঝতে পারি। সবাই মিলে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে আমার জন্মদিন পালন করল।
জাহাজের হলরুম ভর্তি যাত্রী আমার জন্মদিনের উৎসবে সমবেত হয়েছে। প্রতি বছর এই দিনে কিছু বন্ধু-বান্ধব, শিল্পী আমার ক্রিস্টোফার রোডের বাসায় হাজির থেকে ছোট আকারের অনুষ্ঠান করে, গান পরিবেশ করে। আমার গলায় ফুলের মালা দেয়। এখানে এই বিচ্ছিন্ন ‘জল আজাদ’ জাহাজে তার কোনোটারই কমতি ছিল না। নৈশ-ভোজের পরে কেক কাটা হলো, আমার গলায় পরানো হলো টাটকা ফুলের মালা। উপস্থিত অনেকে আমার গান পরিবেশন করল। বিশেষ করে ডাক্তার বাগচী আর প্রভাতের গায়কি আমায় মুগ্ধ করেছিল। তারা এই অনুষ্ঠান স্মরণীয় করে রাখতে বেশ কিছু গান রেকর্ড করল, ফটো তুলল। আমি মাঝে মাঝে দুই হাত দিয়ে তালির মতো বাজালাম, ঘাড় নাড়ালাম, মুখ দিয়ে অস্পষ্ট দুএকটি শব্দও করলাম। মিসেস পিয়ার্সনের নিখুঁত পিয়ানো বাজানো দেখে জাহাজের সবাই অবাক।
সে বাজাল, একটি পেগান লাভ সঙ ‘কাম টু মি হোয়ার দি মুন বীমস।’
এই গানের সুর নিয়ে আমি ‘দূর দ্বীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি’ গানটি লিখেছিলাম।
ডাক্তার বাগচী জানতে চাইল, ‘দিদি, আপনি এত ভালো পিয়ানো বাজানো শিখলেন কার কাছে?’
উনি বললেন, ‘আমি তো তালতলার মেয়ে রে।’
অনিরুদ্ধ পিয়ানোর সাথে গাইল, ‘হোম হোম সুইট সুইট হোম/ দেয়ার ইজ নো প্লেস লাইক হোম/ দেয়ার ইজ নো প্লেস লাইক হোম।’
‘নারী যদি ভালো না বেসে সেবা করে আমার, তবে সে-সেবা আমি নেব কেন?’
জাহাজ-যাত্রার আগে বোম্বেতে আমরা কয়েকদিন ছিলাম মেরিন ড্রাইভ সিগ্রিন হোটেলে। হোটেলের হলরুমে আমার সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পী, কবি সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। তাদের মধ্যে অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কেএস ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এস. আব্বাস মুকেশ, নৌশাদ আলী, যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমি, খৈয়াম, সাহির লুধিয়ানভি, মাজাজ মাখনভি, কাতিল সিপাহি, ফিরাক গোরখপুরীর কথা মনে আছে। সেখান কাইফি আজমি এবং সাহির লুধিয়ানভি আমাকে নিয়ে লেখা তাদের স্বরচিত কবিতা পড়েছিল; হেমন্ত গায়—‘ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি।’ এই অনুষ্ঠানের আয়োজকগণ আমার চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিক বেশ কয়েক হাজার টাকা চাঁদা তুলে একটি থলিতে করে আমার হাতে তুলে দেন।
আমি জাহাজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর দেখতে পাচ্ছি। মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর। মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রায় সমান বয়সী এর ইতিহাস। মহাবীর আলেকজান্ডার, রানি ক্লিওপেট্টা, সিজার ও তার সেনাপতি এন্টনিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এর ইতিহাস ও কিংবদন্তি। একই সঙ্গে পরিণত হয় ইউরোপ ও এশিয়ার সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্রে। এই শহরে পৃথিবীর অন্যতম আদি গ্রন্থাগার নিয়েও রয়েছে নানা কাহিনি।
রবীন্দ্রনাথ আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে নেমেছিলেন। এখানে জাহাজও পরিবর্তন করতে হয়, ভারত সাগর, আরব সাগর পার হয়ে এখন ভূমধ্যসাগর। নতুন মঙ্গোলিয়া জাহাজে যাওয়ার পর ‘স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। এখানকার এক একটা মাঝি স্যার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রিক, ইতালিয়ান, ফ্রেন্স, ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে।… আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধশালী মনে হলো। এখানে কত জাতের লোক আর কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই।’
আমার নির্বাক ইউরোপ যাত্রার প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে, আঠার বছর বয়সে তরুণ রবি ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। তখনো তিনি কৈশোরের গণ্ডি কেটে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বয়স অল্প হলেও তিনি তার পথের ধকল এবং ইউরোপ বাসের সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন—‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ ও ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’ গ্রন্থে। তাঁর বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল, ব্যারিস্টার হওয়া কিংবা মধ্যম ভ্রাতার মতো আইসিএস পরীক্ষায় বসা। তার কোনোটাই শেষ পর্যন্ত হয় নি। তবে দুবারের বিলাত যাত্রার অনুপুঙ্খ ইতিহাস তিনি রচনা করে গেছেন।
তার চুরাশি বছর আগে আরেকজন বাঙালি শেখ দীন মুহম্মদ প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন, ‘দ্য ট্রাভেলগ অব দীন মুহম্মদ।’ তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ইংরেজিতে বই লেখেন, তার জীবনে অভিজ্ঞতা লেখেন, ভারতীয় বিভিন্ন প্রযুক্তি তিনি সেখানে চালু করেন। তার পরিবার ছিল নবাবের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পলাশী ও বক্সারে নবাব পরাজিত হলে, তারা কোম্পানির বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে চলে আসে। রাজত্ব পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে শুরু করে তার নিজের জীবনের উত্থানপতন, এক ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমানো। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্মের বছরে দীন মুহম্মদ রচনা করেন, ‘দ্য ট্রাভেলগ অব দীন মুহম্মদ’। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর লন্ডন গমনের অর্ধশত বছর আগেই ইংরেজ জাতি এই বাঙালি দীন মুহম্মদের কাছে ভারতীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ঋণী। দীন মুহম্মদ বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা, কসমেটিক সার্জারি, স্ট্রিম বাথ ও শ্যাম্পু তৈরির প্রযুক্তি প্রবর্তন করেন। তার পরিবার নবাব বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়ায় এসব বিদ্যা তার আগে থেকে রপ্ত ছিল। প্রথম স্ত্রী জেন ডেইলির মৃত্যুর পর তিনি জেন জেনিফার নামে আরেকজন আইরিশ মহিলাকে বিয়ে করে বিলাতে স্থায়ী হন। তার প্রায় সত্তর বছর পরে বঙ্কিম ইংরেজিতে উপন্যাস লেখেন—‘রাজমোহানস ওয়াইফ’। দীন মুহম্মদ ও আমার পূর্বপুরুষ এসেছিল বিহারের পাটনা থেকে। সেদিক থেকে আমাদের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা ছিল। এটিই ছিল ইংরেজের রাজত্বের শুরুতে পদস্থ মুসলিম রাজ-কর্মচারীদের বাস্তুচ্যুতির ইতিহাসের অংশ।
ঘরকুনো রবি ইউরোপে যাওয়ার ব্যাপারে অন্তরের তাগিদ পান নি। পথের ধকলও তাকে কাবু করে ফেলেছিল। জাহাজে উঠে তিনি সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার বর্ণনায় উঠে এসেছে, ‘যন্ত্রণাশয্যায় অবচেতনপ্রায় হয়ে পড়ে আছি। কখনো কখনো ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সংগীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয় আমার এই সঙ্কীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।’ আমার পক্ষে এ সব বর্ণনা করা সহজ নয়।
তরুণ রবির ব্রাটনের স্কুলের সহপাঠীরা যে খুব সুবোধ ছিল এমন নয়। স্বজন-বর্জিত ঘরকুনো রবিকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছে। সহপাঠীরা এই ভারতীয় তরুণকে নাজেহাল করতে কখনো তার পকেটে কমলা, কখনো আপেল, এই জাতীয় পদার্থ চালান করে পালিয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথের ল্যাটিন শিক্ষক প্রমাণ করতে চাইতেন, ‘পৃথিবীতে একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হয়ে থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে এই ভাবের রূপান্তর ঘটে থাকে, কিন্তু হাওয়াটা একই।’ তাঁর আরেকজন শিক্ষক ‘মি. বার্কার’ সাহেব দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিলেন। বার্কারের স্ত্রী একটি কুকুর পুষতেন—‘স্ত্রীকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি কুকুরটিকে পীড়া দিতেন।’
লন্ডনের স্কট পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই পরিবারের তিনটি মেয়ে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তরুণ মন রোমান্টিকতার আনন্দ-অভিজ্ঞতায় ভরিয়ে তুলেছিল। তিনি এই পরিবারের গৃহকর্তা ও কর্ত্রীকে মি. কে. এবং মিসেস কে. বলে উল্লেখ করেছেন। মিসেস কে. তরুণ কবিকে স্নেহসুধা দান করেন, শৈশবে মাতৃহারা ও বিদেশে স্বজনবর্জিত কিশোর কবি সারা জীবন তার ভালোবাসা ভুলতে পারেন নি। তার দেশে ফেরার সময় মিসেস স্কট ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, ‘এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্প দিনের জন্য তুমি কেন আসিলে।’
আমি এর আগে কখনো য়ুরোপে যাই নি, শুধু য়ুরোপ নয়, ভারতবর্ষের বাইরে কোথায় যাওয়ার সুযোগ হয় নি। বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি গেছি, নৌশেরায় গেছি—সে তো তখন ভারতেরই অংশ। আমার মেসোপটমিয়া যাওয়া—জবানীকাররা গল্পের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। তবে এই সময়ে আমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি জোয়ানদের য়ুরোপের মাটিতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলাম। যদিও ব্যথার দান-এর গল্পগুলো আমি লিখছি তরুণ রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাওয়ার প্রায় চল্লিশ বছর পরে, তবু কাকতালীয়ভাবে আমারও তখন বয়স ছিল, য়ুরোপগামী তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো। অবিভক্ত ভারবর্ষের মধ্যে হলেও আমি তখন স্বদেশভূমি ছেড়ে করাচির বেঙ্গলি রেজিমেন্টে। নিজ দেশেও যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করা, আর বিদেশের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। নিজের দেশ যখন কেউ অপরিচিত করে দিতে চায়, তখনই তো যুদ্ধের প্রয়োজন হয়।
ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের ‘হেনা’ গল্পের নায়ক সোহরাব, ফ্রান্সের ভার্দুন ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করতে যায়। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা বলে অনেকে আমার নিজস্ব গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। এই যুদ্ধের ময়দানে এক ফরাসি বালিকার সাথে সোহরাব মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। ‘এই সিন্ধুপারের একটা অজানা বিদেশিনী ছোট্ট মেম আমায় খানিকটা আচার আর দুটো মাখন-মাখা রুটি দিয়েছিল। সেটা আর খাওয়াই হয় নি। এদেশের মেয়েরা আমাদের এত স্নেহের আর করুণার চক্ষে দেখে!… রুটি দুটো দেখছি শুকিয়ে দিব্যি রোস্ট হয়ে আছে! দেখা যাক, রুটি শক্ত না আমার দাঁত শক্ত! ওই খেতে হবে কিন্তু, পেটে যে আগুন জ্বলছে!—আচারটা কিন্তু বেড়ে তাজা আছে, দেখছি !’
গল্পের মেয়েটার বয়স তের-চৌদ্দ বছরের বেশি নয়, এ বয়সে আমাদের দেশে সন্তানের জননী কিংবা বউ হয়ে যায়। সে যখন সোহরাবের গলা ধরে চুমু খেয়ে বলে, ‘দাদা, এ-লড়াইতে কিন্তু শত্তুরকে খুব জোর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে,’ তখন আমার মুখে বেদনামাখা পবিত্র হাসি ফুটে ওঠে।
সোহরাব বলে ‘উঃ! এতটুকু অসাবধানতার জন্যে হাতের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেখছি একটা গুলিতে!… ব্যান্ডেজটা বেঁধে নিই নিজেই। নার্সগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি নে। নারী যদি ভালো না বেসে সেবা করে আমার, তবে সে-সেবা আমি নেব কেন?’
বিলাত-যাত্রার সময়ে জাহাজে একদিন ব্রেকফাস্টের সময়ে চাকুতে রবীন্দ্রনাথের হাত কেটে রক্তপাত হয়। তিনি রসিকতা করে বলেন, ‘অকাতরে রক্ত দান করতে না পারায় ভারত আজ স্বাধীন হচ্ছে না, অথচ রুটির টেবিলে অহেতুক এই রক্তপাতের কোনো সুফল নেই।’ ‘হেনা’র নায়ক সোহরাব রবীন্দ্রনাথের মতো লক্ষ করেন, ব্রিটিশ জাতিটার কাজে-কর্মে কায়দা-কানুনে কঠোর শৃঙ্খলা, তাই তারা আজ এত বড়।’ জার্মান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তারা ‘হিন্ডেনবার্গ লাইন’ পর্যন্ত চলে যায়।
সোহরাব বলে, ‘যাক, আমার “হ্যাভার স্যাক” থেকে একটু আচার বের করে খাওয়া যাক। সেই বিদেশিনী মেয়েটি আজ কত দূরে, কিন্তু তার ছোঁয়া যেন এখনো লেগে রয়েছে এই ফলের আচারে! দূর ছাই! যত সব বাজে কথা মনে হয় কেন? খামখা সাত ভূতের বেদনা এসে জানটা কচলে দিয়ে যায় !’
ব্রিটিশ রানি আমার সম্মানে না দিয়েছেন পার্টি, না প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এথলি দেখা করতে এসেছেন—খেতাব তো দূরের কথা।
সোহরাব বলে, ‘হেনা, আমি যাচ্ছি মুক্ত দেশের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যার ভিতরে আগুন, আমি চাই তার বাইরেও আগুন জ্বলুক! আর হয়তো আসব না। তবে আমার সম্বল কী? পাথেয় কই? আমি কী নিয়ে সেই অচিন দেশে থাকব?’ ‘আমি পিয়ানোতে “হোম হোম সুইট সইট হোম” গৎটা বাজিয়ে সুন্দর রূপে গাইলুম দেখে ফরাসিরা অবাক হয়ে গেছে, যেন আমরা মানুষই নই, ওদের মতো সূক্ষ্ম কাজ করা যেন আমাদের পক্ষে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! এ ভুল কিন্তু ভাঙাতেই হবে।’ ‘আবার সেই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই দুবছরে কত বেশি সুন্দর হয়ে গেছে সে! সেদিন সে সোজাসুজি বললে, যে, (যদি আমার আপত্তি না থাকে) সে আমায় তার সঙ্গীরূপে পেতে চায়! আমি বললুম, ‘না, তা হতেই পারে না!’ এক আইরিশ বালিকা শেখ দীন মুহম্মদের প্রেমে পড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ পরিবার বাঙালি হিন্দু মুসলিমের চেয়ে কম গোঁড়া নয়।
‘বিদেশিনীর নীল চোখ দুটো যে কী রকম জলে ভরে উঠেছিল, আর বুকটা তার কী রকম ফুলে ফুলে উঠেছিল, তা আমার মতো পাষাণকেও কাঁদিয়েছিল!’
আমার মতো আমার নায়ক সোহরাব সেদিন বলেছিল, ‘আমি বেওয়ারিশ মাল।’ অতএব খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললুম, ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়!’ তারপর তার ভাষায় ‘অডিএ’ (বিদায়) বলে সে যে সেই গিয়েছে, আর আসে নি! আমার শুধু মনে হচ্ছে, ‘সে চলে গেছে বলে কি গো/ স্মৃতিও হায় যায় ভোলা!/ আজও মনে হলে তার কথা/ মর্মে সে মোর দেয় দোলা।’
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ১৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সশস্ত্রবাহিনীতে যোগ দিয়ে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে। এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে গঠিত সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল। ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটেনের পক্ষে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে শুরু করে পূর্ব আফ্রিকা, ওসমানীয় সাম্রাজ্য ও চীনের মাটিতে যুদ্ধ করে। প্রায় ৯০,০০০ ভারতীয় সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। আমিও ছিলাম এই বাহিনীর অংশ। এই যুদ্ধে কিছু বাঙালি সৈন্য যে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতেও যোগ দিয়েছিল এবং কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল, সেই তথ্যটি আমার এই গল্প ছাড়া অন্যত্র খুব কমই উল্লেখ আছে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ফ্রান্সও ব্রিটেনের মতো জনবলের ঘাটতির সম্মুখীন হয় এবং উপনিবেশগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ফরাসি-শাসিত ভারতের গভর্নর আলফ্রেদ মাতিনো আহ্বান জানিয়েছিলেন, ‘ভারত নানাভাবে ফ্রান্সের নিকট ঋণী। এখন এই দুর্যোগের সময়ে ফ্রান্সের পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি ভারতীয়ের কর্তব্য…এই কঠিন সময়ে যারা ফ্রান্সের পাশে দাঁড়াবে ফ্রান্স তাদের কখনো ভুলবে না। ফ্রান্স তাদের সঙ্গে নিজ সন্তানের মতো আচরণ করবে। ফরাসি সেনাবাহিনিতে যোগ দিন!’ মাতিনোর বক্তব্য তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসকদের মানসিকতারই প্রতিচ্ছবি। ইউরোপের মাটিতে চলমান যুদ্ধে ভারতীয়দের কোনো জাতীয় স্বার্থ ছিল না। এমনকি এই যুদ্ধে ভারতবর্ষকে জড়িত করার আগে ভারতীয়দের কোনো মতামত নেয়ার প্রয়োজনীয়তাও ব্রিটিশ বা ফরাসিরা মনে করে নি। মিউস-আর্গন আক্রমণাভিযানে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে চন্দননগরের বাঙালি সৈন্যরাও অংশ নিয়েছিল। এর আগে ইউরোপে না এলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে এবং লেখক হিসাবে আমার মানস-ভ্রমণ সম্পন্ন করেছিলাম।
আমরা জাহাজ থেকে লিভারপুল বন্দরে নামলাম। লিভারপুল থেকে লন্ডনের দূরত্ব প্রায় দুশো মাইলের কাছাকাছি। এখানে থেকে ট্রেনে লন্ডন যেতে প্রায় ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। লিভারপুল ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের অংশ, অন্যতম প্রধান বন্দর। দাস আনা-নেয়ার জন্য আঠার শতকে এই বন্দর কুখ্যাত হয়ে আছে। লিভারপুল থেকে স্ট্রেটফোর্ড স্টেশনে নেমে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো লন্ডন ক্লিনিকে, সে-ভাবে আগে থেকে ব্যবস্থা করা ছিল। সেখানে একাধিক হাসপাতালের ডাক্তাররা বেশ কিছু দিন ধরে আমায় নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ২০ জুন লন্ডনের উপকণ্ঠ মিচাহামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি আমায় দেখেন। সেখানে সেন্ট টমাস হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান ড. উইলিয়ম সার্জান্ট নেতৃত্ব দেন, ২৩ জুন ভারতীয় হাইকমিশনের মেডিকেল পরামর্শক ডা. কর্নেল পাসরিচার কাছে রিপোর্ট করা হয়। ২২ জুন ডা. ই. এ. বেনেট তার পর্যবেক্ষণও হাইকমিশনের মেডিকেল পরামর্শককে জানান। পহেলা জুলাই নিউরোলজিস্ট রাসেল ব্রেইন তার রিপোর্ট দেন। ২২ আগস্ট একটি সম্মিলিত রিপোর্ট পেশ করা হয়। রাসেল ব্রেইন যে রিপোর্ট দেন, তার সারমর্ম ‘কবি দীর্ঘদিনের ডিমেনশিয়া অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ রোগে ভুগছেন এবং সেই সঙ্গে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন।’ এক্সরেতে দেখা যায়, ‘তার মস্তিষ্ক সংকুচিত’ হয়ে গেছে।
চিকিৎসা সম্পর্কে তাদের মতামত ছিল, আমি চিরদিনের জন্য সৃজনশীল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কোনো চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে অস্ত্রোপচার করলে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হতে পারে। পেশাব-পায়খানা নিজে নিজে করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রমীলা আমার অপারেশনে রাজি হয় নি। তার দ্বিধা ছিল, অপারেশনের ফলে আমার অবস্থা বর্তমানের চেয়েও খারাপ হয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে হাতে টাকা-পয়সাও শূন্যতে নেমে আসছিল। লন্ডন নিরাময় কমিটিও তেমন কিছু করতে পারে নি। তারা ফেরার জন্য চারটি বিমান টিকিটের ব্যবস্থা করে। তাতে অন্তত এক মাস ধরে কষ্টকর কয়েকটি মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে না।
এদিকে ডা. বাগচী আমায় ভিয়েনায় নিয়ে তার শিক্ষকদের কাছে দেখানোর ইচ্ছে পোষণ করে। এমনকি ভিয়েনায় যাওয়ার পথে জার্মানির বন স্টেশনে নেমে সেখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। অক্টোবরের সাত তারিখ থেকে সতের তারিখ পর্যন্ত জার্মানি ও ভিয়েনায় আমায় দেখানো হয়। ড. পি রোটজেন, ড. ক্লাউসবার্জার আমায় দেখে। ভিয়েনাতে ডা. হানস ডফের অধীনে ভর্তি করা হয়। মস্তিষ্কের এনজিও গ্রাম করা হয়। ড. হানস জানান, আমার মস্তিষ্কের সামনের এবং দুপাশের অংশ শুকিয়ে সংকুচিত হয়ে গেছে। তিনি এই রোগের নাম পিকস ডিজিজ বলে জানান। তিনিও লন্ডনের ডাক্তারদের মতো বলেন, এই রোগ নিরাময়ে কোনো চিকিৎসা নেই। পরে এই রোগের আরো নাম জানতে পেরেছি, জাপানি ডাক্তার কেঞ্জি এই রোগের নাম দিয়েছে, ‘ডিমেনশিয়া উইথ লিউলি বডিজ’।
তবে যে সব কারণে এই রোগ হতে পারে বলে এখানকার ডাক্তারা জানিয়েছিলেন—তার অন্যতম ম্যালেরিয়া। আমি জীবনে দুই দুইবার ভয়াবহ ম্যালেরিয়া রোগে ভুগেছি। শেষবার তো মনে হয়েছিল, আর বাঁচবই না। যেখান থেকেই হোক, শেষ পর্যন্ত বুঝেছি, আমার এই রোগের চিকিৎসা দুনিয়ার কোথাও সম্ভব নয়। এখানে এসে একটা লাভ হলো, এখানকার ডাক্তাররা প্রায় সকলে একমত রোগের শুরুতে ভুল চিকিৎসার ফলে রোগটি আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। আর শুরুর দিকে লুম্বিনী হাসপাতালের ডাক্তার আর বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া কেউ বলেন নি, আমার সিফিলিস হয়েছে। তাছাড়া আমি অসুস্থ হওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে যারা আমায় চিকিৎসা করেছে, সেই ড. বাগচী এবং ড. ডি.কে. রায়ও সে-কথা বলে নি। অবশ্য যারা বলেছিলেন, তাদেরও দোষ দেয়া যায় না—বলা যায় এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের সীমাবদ্ধতা।
লন্ডন ও ভিয়েনায় চিকিৎসার মাধ্যমে আমার প্রায় এক যুগের এক অজানা রোগের চিকিৎসার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটল। অর্থের অভাবে আমার সর্বোচ্চ চিকিৎসা হয় নি বলে আমার ভক্তকুল ও জাতির যে মনো-বেদনা ছিল—তারও অবসান হলো। যদিও রোগের বার বছর পরেও গরিব কবির চিকিৎসা অর্থের অভাবে কোনো রকম গরিবানা হালেই শেষ করতে হলো। আমরা এক সঙ্গে লন্ডনে পাঁচ জন এলেও এখানকার নিরাময় কমিটি চারটার বেশি বিমান টিকিট দিতে পারে নি। একজনকে অল্প দামের টিকিটে জল-জাহাজে দেশে ফিরতে হবে। সদ্য-স্বাধীন হওয়া পূর্ব পাকিস্তানের আমি জাতীয় কবি হতে পারব কি না, সেই বিতর্কে গোলাম মোস্তফাসহ অনেকে সরব থাকলেও আমার চিকিৎসার জন্য তাদের উদ্যোগ স্পষ্ট নয়। জাতীয় কবির চিকিৎসার গুরুভার এতই বেশি ছিল যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমার অগণিত বন্ধুবান্ধব ও ভক্তকুল, বিলাতের ভক্তকুল মিলেও তার সম্মানজনক সমাধান করতে পারে নি।
মাত্র বছর পাঁচেক আগে যে কবি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল, একের পর এক বই বাজেয়াপ্ত করে, পুলিশি হয়রানি করে, জেলে পুরে, গোয়েন্দা নজরদারিতে রেখে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষায় তটস্থ ছিল, সেই কবি আজ ইংল্যান্ডে এলেও—না আছে রাজকীয় সম্মান, না আছে অর্থব্যয়। ব্রিটিশ রানি আমার সম্মানে না দিয়েছেন পার্টি, না প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এথলি দেখা করতে এসেছেন—খেতাব তো দূরের কথা। ব্রিটিশবিরোধী সকল রাজনীতিক মুছে ফেলা গেলেও আমার গান কবিতায় যে সর্বনাশের চিহ্ন এঁকে দিয়েছি তার ক্ষত থেকে যাবে যুগের পর যুগ ব্রিটিশ জাতির ললাটে।
রেখে এলাম বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ-ভারতে ঘটে যাওয়া আমারই মতো এক অমীমাংসিত বোবা কান্নার ইতিহাস।
লন্ডন ও ভিয়েনায় এসে আমার বন্ধু নেতাজি সুভাষ বসুকে মনে পড়ছে। ভিয়েনাতে এখনো তার পরিবার রয়েছে। আমার মতো তাকেও দেখতে হয় নি খণ্ডিত ভারত, খণ্ডিত বাংলা। আমার অসুখের মতো এক রহস্যময় অন্তর্ধান তাকেও এই জাতীয় বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করার হাত থেকে রক্ষা করেছে। দীলিপকুমার রায়, হেমন্তকুমার সরকার তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—যারা খণ্ডিত বাংলা ও সন্ন্যাসধর্ম নিয়ে বেশ আছে। আমি কাজী নজরুল ইসলাম আর আপামর বাঙালির স্বপ্নের নেতা সুভাষ বসু—সেই স্বপ্নের দেশের খোঁজে অন্ধকারে এখনো লড়াই করে যাচ্ছি।
১৯৩৪ সালের কথা। তিনি তখন ইউরোপে। এখানকার এক প্রকাশক ওই সময়ে নেতাজিকে ‘দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল’ নামে একটা বই লেখার কাজ দেন। বইটি ব্রিটিশ সরকার ভারতে বিপণনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বইটি লেখার জন্য একজন সহকারীর প্রয়োজন হলো, যিনি ইংরেজি আর টাইপিং—দুটোই ভালো মতো জানবেন। ২৩ বছর বয়সী এমিলি শেঙ্কল এসেছিলেন ইন্টারভিউ দিতে। সুন্দরী অস্ট্রিয়ান ওই যুবতীকেই সহকারী হিসাবে কাজে নিয়োগ করলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তারপর ইতিহাস, দেশনেতা প্রেমে পড়ে গেলেন এই স্বর্ণকেশী ললনার, কিছুদিন প্রেম, তারপর গোপনে বিয়ে। জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে এভাবেই মিশে থাকল ঔপনিবেশিক ভারতের একটি আন্তর্জাতিক ইতিহাস। নিজ জাতের ব্যক্তিগত ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলো অন্য জাতের উত্তরাধিকার। আজ ব্রিটিশ নেই, কিন্তু চিন্তায় মননে, গভীর শুশ্রূষা ও ক্ষতে অক্ষয় হয়ে আছে সে-সব। মনে বড় সাধ ছিল ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের পোয়েন্টস কর্নারে যাব—আমার প্রিয় কবি শেলি কীটসের সমাধির ধূলা স্পর্শ করব—তা আর হলো না।
নিরাময়ের সম্ভাবনা না থাকায় এবং আসন্ন শীতের ভয়ে ছয় মাস পরে একই বছরে ১৪ ডিসেম্বর রোম থেকে আমরা কোলকাতায় ফিরে এলাম। রেখে এলাম বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ-ভারতে ঘটে যাওয়া আমারই মতো এক অমীমাংসিত বোবা কান্নার ইতিহাস। কবিগুরুর মতো বলতে ইচ্ছে করছে—‘এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস। ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না।’