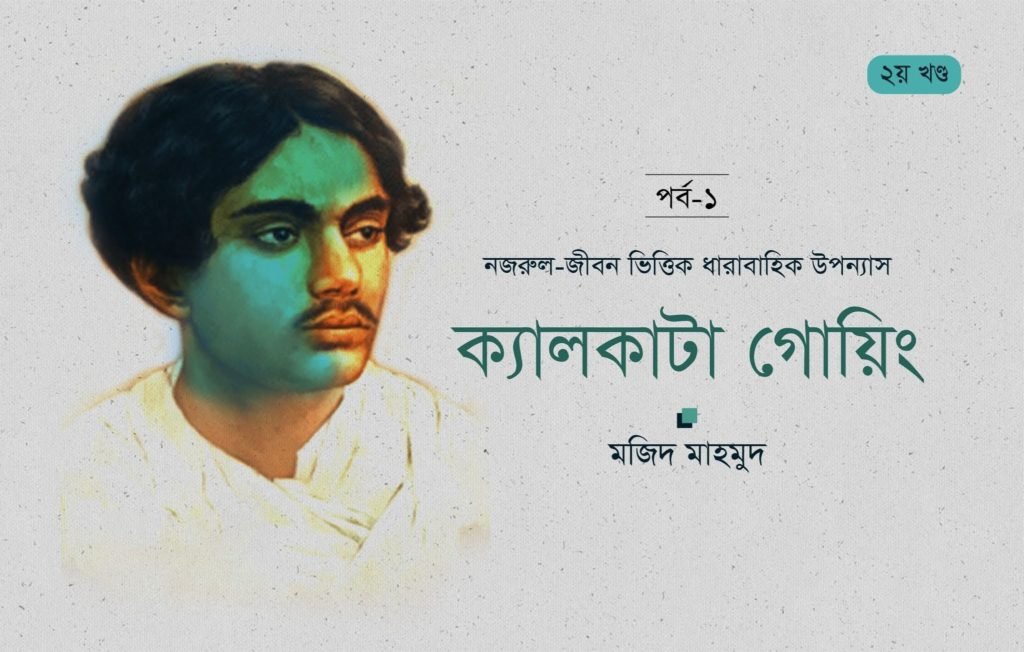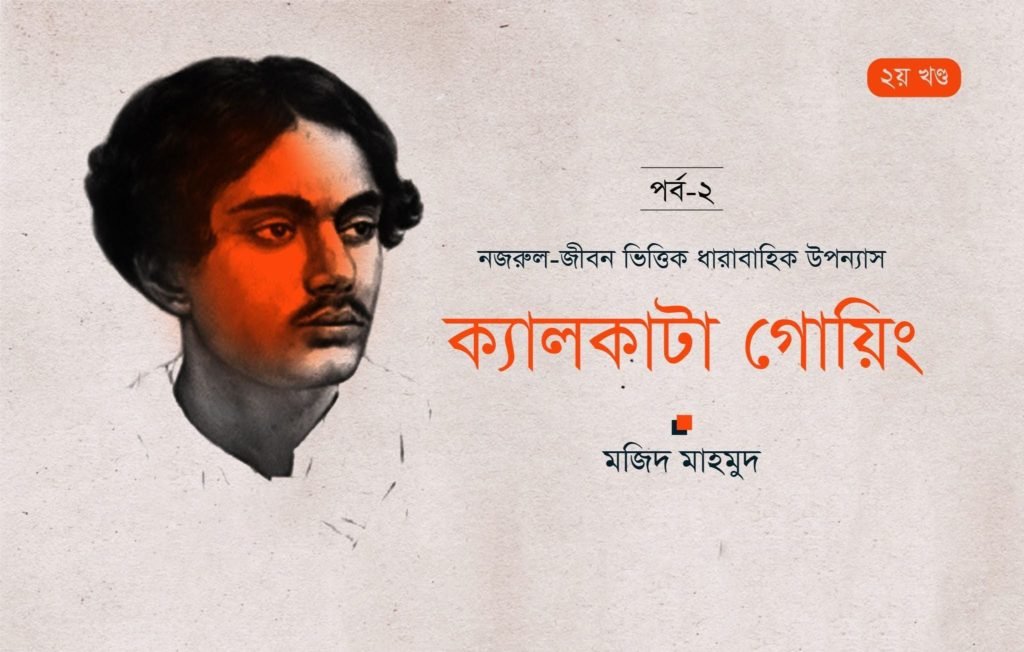পর্ব-৯
লন্ডন ও ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পরে আমার পরিবার নিশ্চিত যে, আমি আর কখনো কথা বলতে পারব না, গান কবিতা লিখতে পারব না, যতদিন বাঁচি এই পঙ্গুত্ব নিয়ে আমাকে থাকতে হবে। সবাই কিছুটা নির্ভার হয়ে সংসার-কর্মে মন দিতে শুরু করেছে। শাশুড়ি নেই, প্রমীলা পঙ্গুত্ব নিয়েই বেশ শক্তভাবে সংসারের হাল ধরেছে। সানি ও নিনি এখন অনেকটাই বড়। ওরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে। সানি আমার কবিতা আবৃত্তি করে বেশ প্রশংসা পাচ্ছে। নিনি গিটার বাজানো শিখছে, দুএকটি অনুষ্ঠানে বাজাচ্ছে, গানও গাইতে পারে, আমার সাহিত্য-কর্ম নিয়ে ওর রয়েছে আগ্রহ।
এত কিছুর পরেও আমার রোগটির সঠিক হদিশ পাওয়া গেল না। আমার জীবন ও কর্মের মতো এক অলৌকিক রহস্যঘেরা থেকে গেল। আমার নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার এক যুগ না ঘুরতেই আমার রোগ নিয়েও চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা, নিত্য-নতুন গল্পের ডালপালা মেলছে। অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই সামনে চশমা পরা কোনো মানুষ দেখলে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি, রেগে যাই। চশমা খুলে আমার সামনে আসতে হয়। কিছুদিন জানাশোনার পরে, যখন বুঝি লোকটি ক্ষতিকর নয়, তখন চশমাকেও মেনে নিই। ড. অশোক বাগচী চশমা পরে এলেও আমার মধ্যে তেমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। বুঝতে পেরেছিলাম সে আমার শত্রু নয়, মিত্র।
আমার রোগের কারণ আমি ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কেউ জানে না।
উত্তেজনার কারণ যে ভয় সে-কথা ডাক্তাররা বলে থাকে। একটা সাপও ভয় পেলে তেড়ে আসে। আমি বিলাত যাওয়ার আগেই মুর্শিদাবাদের সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসির ‘রঙ্গমঞ্চ’ পত্রিকায় লেখা হয়, ‘নজরুলের ওপর রেডিও স্টেশনে দৈহিক আঘাত ও কবিকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।’ পরবর্তীকালে ঢাকায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টে ঘাড়ে কঠিন আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়। সে-থেকে অনুমান করা যায়, সেদিনের আক্রমণকারীদের চোখে চশমা ছিল। ‘রঙ্গমঞ্চে’র খবরটি উনিশশ সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে। খবরটি ভিত্তিহীন হলে কেউ না কেউ এর প্রতিবাদ করত। সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসি উটকো লোক নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে অনেক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তার পুত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সম্প্রতি কথাসাহিত্যে নাম করতে শুরু করেছে। অনেকে বলবে, উৎখাত করার জন্য আঘাত করা হলে সেটি আমার জানার কথা। আঘাতে জ্ঞান হারালে সেই স্মৃতি মনে থাকার কথা নয়। আমার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র চলছিল রেডিও অফিসের ভেতরে। অনেকে চাচ্ছিল না, আমি রেডিওর এই চাকরিতে থাকি। এমন তো নয় এর আগে কেউ আমায় শারীরিকভাবে আঘাত করে নি। সে-সব আঘাতের জন্য নিশ্চয় আমি দায়ী ছিলাম না। গান শেখাতে গেছি যার মেয়েকে তার অভিযোগ নেই, অভিযোগ পাড়া-পড়শির। মানবেন্দ্র’র কথার ফেরদৌসির কথার ইঙ্গিত মেলে—
‘কবি একটা অবসেশনে ভুগছিলেন। বেশ বুঝতে পারছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে একটা যড়যন্ত্র চলছে। তার গতিকে স্তব্ধ করার চক্রান্ত। এ চক্রান্তের কি আজও শেষ আছে? যে গ্রামোফোন কোম্পানির কম্পোজার হিসাবে তিনি নিজেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, সেখানে তার রিহার্সালের জন্য আলাদা একটা রুমও জোটে নি। চিলেকোঠার একটা ছোট গুমোট ঘরে তাকে রিহার্সাল করতে হতো।’
একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সালের দিনগুলোতে আমার সৃষ্টিশীলতা কিছুটা কমে আসছিল। আমার কাছে এক মহারহস্য লোকের ইঙ্গিত এসে সব কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছিল।
নৃপেনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেদিন রেডিওতে উপস্থিত ছিল। সে-রাতের ঘটনার পরে সে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। এই হামলার ঘটনা চাউর হলে অনেকে তার কাছে বিষয়টি জানতে চেয়েছিল। বিশেষ করে নলিনীকান্ত পণ্ডিচেরি থেকে চিঠি লিখে জানতে চাইলে নৃপেনকৃষ্ণ এড়িয়ে যায়, বলে : ‘আমি এ সব জানি না।’ আমি ভাবি, এত বড় ঘটনা ঘটে থাকলে আমি নিশ্চয় পরে জানতে পারতাম। ডাক্তাররা আমার অসুখের যে ধরনের কারণ তদন্ত করেছে তার মধ্যে এই আঘাতের বিষয়টি প্রাধান্য পায় নি। সিফিলিস, নিউরো আলঝেমার, পিকস ডিজিজ, ডিমেনশিয়া উইথ লিউয়ি বডিজ, মস্তিষ্ক শুকিয়ে যাওয়া রোগের সাথে ভিয়েনার ডাক্তাররা বলেছে, ম্যালেরিয়া থেকেও এ ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে—সঙ্গে শারীরিক আঘাতের বিষয়টি যুক্ত হতে পারত। তবে আমার রোগের কারণ আমি ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কেউ জানে না।
তাহলে আমার রোগটা কী, সত্যিই কি আমি সচরাচর আর পাঁচজন মানুষের মতো রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, নাকি বন্ধু-বান্ধব পরিচিতদের সাক্ষ্য অনুসারে যোগভ্রষ্ট হয়েছি। ডাক্তাররা যেহেতু রোগটি সঠিকভাবে ধরতে পারে নি, চিকিৎসাও করতে পারে নি, তাহলে কি ডাক্তারদের দেয় নামের রোগগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব! কেউ যদি বলে, কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই রোগ হয়েছিল, তা মিথ্যাও হতে পারে, সত্যও হতে পারে। আমার রোগের জন্য যেমন এলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়েছিল, তেমন আয়ুর্বেদি, হোমিওপ্যাথি, ঝাড়-ফুঁক, মানত—ইসলামি মতে হিন্দু মতে—সবই করা হয়েছে। আমার নিরাময়ের ব্যাপারে বিশেষ কোনো প্যাথির দাবি আলাদাভাবে খাটে না, সব ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিতেই কিছু উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে কোনো চিকিৎসাই আমার উপরে আংশিকও কার্যকরী হয় নি—বাহ্যিক শরীরবৃত্তীয় ব্যাপারে কিছু কাজ করে থাকতে পারে। আবার অন্যভাবে বলা যায়, সত্যিই কি আমি অসুস্থ ছিলাম? মারাত্মক অসুস্থতা হওয়ার পরে কিভাবে প্রায় নিরোগ অবস্থায় চৌত্রিশ বছর বেঁচে থাকলাম! আমরা যে জগতে বসবাস করি সে-জগতে বুদ্ধির বাইরে প্রতিনিয়ত নানাবিধ রহস্যময় ঘটনা ঘটে চলেছে—যা বিশ্বাসের সাথে যুক্ত নয়।
আমি আসলে যে দশায় পরিণত হয়েছিলাম, সচরাচর তা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে।
আবার সংসারীদের মাঝে এ কথা বলা ঠিক হবে না, আমার যোগসাধনা, আধ্যাত্ম্য-সাধনা—এমন স্থলে পৌঁছেছিল, যার ফলে আমি চিরদিনের জন্য মহাস্থবির হয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার শরীরের মধ্যে কবর রচনা করেছিলাম। পৃথিবীতে আমার জন্য যে নির্ধারিত বয়স ছিল, সেই বয়স আমি পার করেছি—পৃথিবীর কোনো কর্মের সঙ্গে যুক্ত না থেকেই। আমি অতি অল্পদিনে আমার বরাদ্দকৃত সকল কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছি, ভবিষ্যতের জন্য কোনো কাজ বাকি নেই। মাত্র বিশ বছরে এত লেখা লিখেছি, এত কথা বলেছি, এত ঘুরে বেরিয়েছি, এত বন্ধু সঙ্গ করেছি যে, বাকি জীবনের জন্য কিছু করার ছিল না। আমার মহাস্থবির হওয়ার চৌত্রিশ বছরের শেষদিন পর্যন্ত আমি পুরোপুরি বুদ্ধিভ্রষ্ট ছিলাম, অচেতন ছিলাম, উদ্দীপনায় নাড়া দিই নি, এমন কথাও তো কেউ বলছে না, তাহলে জগতের আর সব মানসিক সমস্যার সঙ্গে আমার মানসিক সমস্যার মিল ছিল বলেও মনে হয় না। আমি আসলে যে দশায় পরিণত হয়েছিলাম, সচরাচর তা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। মানুষের জগৎ সকল কিছুকে যুক্তি দিয়ে বন্দি করতে চায়, শ্রেণিভুক্ত না করলে তার পক্ষে মুক্তির উপায় থাকে না।
অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আমার কিছু নতুন অভ্যাস তৈরি হয়েছিল, তার একটি কাগজ পড়া, কাগজ ছেঁড়া। আমার জন্য আলাদা একটি ইংরেজি কাগজ রাখা হতো, বাড়ির সবাই বাংলা কাগজ পড়ত। আমি কাগজটি পড়ার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ সামনে ধরে রাখতাম, অন্যরা ভাবত এটা নিছক আমার মানসিক বিচ্যুতির প্রবণতা, আমি কিছুই পড়ছি না, কিছুই দেখছি না, আর তাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে আমি কিছুক্ষণ পর কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। তারপর সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে বালিশের নিচে জমা করে রাখতাম। বাইরে যে সব কাগজের টুকরো পড়ে থাকত, এমনকি সিগারেটের মুথো, ভাঙা তৈজস—সংসারের সব ব্যবহার্য অবশিষ্ট আমার মতো মনে করে কুড়িয়ে আনতাম।
তখন আমরা থাকি হাজারীবাগের বাসায়। একবার একটি জ্বলন্ত সিগারেটের মুথো আমি বাইরে থেকে কুড়িয়ে এনে বালিশের নিচে রেখে দিলাম। তখন সানি ও নিনি নিয়মিত সিগারেট ধরেছে। আমার পানের নেশা থাকলেও সিগারেটের নেশা ছিল না, পছন্দও করতাম না। এ ধরনের পরিস্থিতি আমি সংসারীদের কখনো ফেলতে চাই নি, তবু সেদিনের ঘটনায় আমার পরিবার বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, তারা কেউ বুঝতে পারছিল না কিভাবে এটি হলো। জ্বলন্ত সিগারেটের মুথো বালিশের তুলোর স্পর্শ পেয়ে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ল—বালিশ থেকে বিছানায়, তোশকে চাদরে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সবাই দিবা নিদ্রায় মগ্ন। সানি ও নিনি বাইরে, উমা ও কল্যাণী তার ঘরে, প্রমীলাও নিথর তদ্রাচ্ছন্ন। আগুনের গন্ধে অকস্মাৎ সবার ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে এল কল্যাণী, ছুটে এল উমা, সাহু ও কাটিয়া, বিছনায় শুয়ে প্রমীলা চিৎকার করে উঠল—আগুন! আগুন! ওরা এসে দেখল, সব দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর আমি সেই আগুনের মাঝখানে নিরুদ্বেগ নিশ্চল বসে আছি। কোনো ভাবান্তর নেই, ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। আর মনে মনে উচ্চারণ করছি—
‘আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!..
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডি, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।’
কল্যাণী বলল, এই আগুনের মধ্যেও ‘অগ্নিবীণার কবি কিন্তু বসে আছেন আগুনের মাঝে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার উনার গায়ে একটা ছ্যাঁকাও লাগে নি। উনি যেভাবে নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন সেভাবেই বসে আছেন, আগুনে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।’ অথচ তারা কিভাবে নিশ্চিত হলো একটি জ্বলন্ত সিগারেটের মুথো থেকে এ আগুনের উৎপত্তি! সিগারেটের মুথো কি তারা খুঁজে পেয়েছিল। এরচে বেশিটা তো আমি কখনো দেখাতে চাই নি।
চাইলেই রাতারাতি পথ তৈরি সম্ভব নয়, পথের দিশা হয়তো রেখে যাওয়া যায়।
আমি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম, আমার পরিবারেও কেউ বিশ্বাস করে নি। এ অবস্থার শুরুর দিকে কিছুটা উন্মাদনা ছিল—এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার প্রাথমিক প্রকাশ। কল্যাণী বলেছিল, ‘বাবার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল, এ কথা আমি স্বীকার করি না।… আমাদের মাঝখানে—আমাদের একজন হয়ে তিনি থাকতেন। নাতি-নাতনিরা তাঁকে ঘিরে লুকোচুরি খেলত—তিনি তা হাসি মুখে উপভোগ করতেন। আবার বাচ্চারা কেউ কাঁদলে হুংকার ছেড়ে আমাদের ইঙ্গিতে তাকে কোলে নেবার নির্দেশ দিতেন।’
উমা আর কল্যাণীর বিয়ে হয়েছিল খুব কাছাকাছি সময়ে। সানি ও নিনির বয়সের পার্থক্যও বেশি নয়। উমা বর্ধমানের কাটোয়ার মুখার্জী পরিবারের মেয়ে। কলকাতার ‘লেডি ডাফরিন হাসপাতাল’ থেকে ট্রেনিং নিয়েছিল। সে এসেছিল আমার সেবার দায়িত্ব নিয়ে। তখন আমরা থাকতাম মানিকতলার বাসায়। উমা যেদিন প্রথম এসেছিল, তখনো পুত্রবধূ হয় নি, প্রমীলা তাকে বলল, ‘তুমি কি পারবে কবির সেবা করতে? ওই দেখো, উনি খবরের কাগজ ছিঁড়ছেন। উনি এখন শিশুর মতো।’
উমা বলল, ‘আমরা তো কলকাতার হাসপাতালে শিশু বিভাগে ডিউটি করেছি। কবি যদি শিশুর মতো হন, নিশ্চয়ই পারব।’ সে পেরেছিল।
সেবা ও স্নেহের পথে ক্রমে উমাই হয়ে উঠল আমার সেবা-যত্নে মমত্বের আধার। গোসল করানো, খাওয়ানো, দেখভাল করা, গল্প শোনানো—উমার হাতের স্পর্শে আমি শরীরে মনে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।
এর মধ্যে সব্যসাচী উমার প্রেমে পড়ে গেল। পড়ার কথা, ওর মতো লক্ষ্মী প্রতিম মেয়ে, দেখতে-শুনতেও ভালো। সব্যসাচীর ভাবনার মধ্যে আমার সেবা-যত্নের বিষয়টিও ছিল। কে আসবে বাইরে থেকে; কবি হিসাবে আমায় সম্মান করা, আর এক বুড়ো শিশুর বিছানা পরিষ্কার করা কখনো এক নয়। উমাও সব্যসাচীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সানিও দেখতে অনেকটা আমারই মতো, সৃষ্টিশীল রোমান্টিক, তার প্রেমে না পড়া কোনো মেয়ের জন্য অস্বাভাবিক। ভালোবাসলেও পরিণতি সহজ ছিল না। আমি তার বাবা, তার বিয়ের প্রায় তিন দশক আগে তার মাকে বিয়ে করেছিলাম, ধর্ম জাতি ও আইনের নানা নিষেধাজ্ঞা অতিক্রম করে, তার সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। চাইলেই রাতারাতি পথ তৈরি সম্ভব নয়, পথের দিশা হয়তো রেখে যাওয়া যায়, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মাথার মধ্যে যে পথের স্পষ্ট পদচ্ছাপ রয়ে গেছে—তা মানুষ কিভাবে অতিক্রম করবে।
ঈশ্বরের আলো বাতাস পানি খাদ্য সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে, হিন্দুর জন্য মুসলমানের জন্য আলাদা নয়। একই সূর্য, একই মলয় বায়ু, একই পানি, একই মাটি, জন্ম-মৃত্যু, ব্যথা-বেদনা, রক্তের রঙ—সব এক; তবু সমবর্ণ না হলে বিয়ে বৈধ নয়—এটি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলনের আনন্দ যদি এক হয়, হিন্দু নারী মুসলিম নারীর পক্ষে কি অন্য ধর্মের মানুষের দ্বারা গর্ভধারণ অসম্ভব, সন্তান পালন যদি সম্ভব না হতো, তাহলে মনে করা যেত অপ্রাকৃতিক। শাদা আর কালো, হিন্দু আর মুসলমানের পার্থক্য আছে। ধর্ম প্রাকৃতিক হলে নারী পুরুষের সম্পর্কও প্রাকৃতিক, কে কার সঙ্গে যাপন করবে সেটি তো একান্ত তার হওয়ার কথা, বিধাতার তো এখানে বাঁধা হওয়ার কথা নয়। স্রষ্টা চায় তার প্রকৃতির আবাদ, নারীর গর্ভে মানুষের সন্তান। কোনো নারী যদি মহাকালের মাত্র পঞ্চাশটি বছর গর্ভ ধারণে অস্বীকৃত হয়, ইস্রাফিলের শিংগার ফুৎকার তখন ব্যর্থ হয়ে যায়। শূদ্রানির গর্ভ প্রাচীন ব্রাহ্মণ বীর্য দানে কার্পণ্য করে নি কখনো। আমাদের নবীজীর একজন খ্রিষ্টান স্ত্রী ছিলেন, তার গর্ভে জন্মেছিলেন পুত্র ইব্রাহিম। প্রমীলার সঙ্গে আমার বিয়ে তো সেই আদি কিতাবের নিয়মেই হয়েছে। আমার পুত্ররাও আমারই মতো অন্য ধর্মের নারীর পাণি গ্রহণ করেছে। মধুসূদন নিজ ধর্ম ত্যাগ করলেও মোহিতলাল ‘শ্রী মধুসূদন’ লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছে—তিনি মূলত হিন্দুই ছিলেন। মধূসূদন হিন্দু নন কে বলতে পারে, নজরুল মুসলমান নন কে বলতে পারে—ধর্ম আমাদের বৈচিত্র্যের পরিচয়, প্রার্থনার ভাষা—যা কেবল প্রভুর জন্য, আর কেউ তা নির্দেশ করতে পারে না।
বিয়ে হলো বামুনের মেয়ের সঙ্গে মুসলিম ছেলের। হয়ে গেল উমা মুখার্জী থেকে উমা কাজী।
উমার জন্য তখন পাত্র খোঁজা চলছিল, মুখার্জী বাড়ির মেয়ে, সরকারি চাকুরে পাত্রও জোগাড় হয়ে গেছিল। উমা তবু সাহস সঞ্চার করে জানিয়ে দিল, ‘সব্যসাচীকে আমি ভালোবাসি। আমি তাকেই বিয়ে করব।’
তাকে বলা হলো, ‘মুসলিম বিয়ে করে কোনো দিন যদি দুঃখ পাও, তখন আমরা কিন্তু আর তোমাকে ফেরত নেব না।’
উমা বলেছিল, ‘দুঃখ করতে যদি নেমেই থাকি, দুঃখে পড়লেও কাউকে জানাব না।’
বিয়ে হলো বামুনের মেয়ের সঙ্গে মুসলিম ছেলের। হয়ে গেল উমা মুখার্জী থেকে উমা কাজী। তাকে বউমা হিসাবে পেয়ে আমি ও প্রমীলা বেশ খুশি। প্রমীলা ওকে মেয়ের মতো ভালোবাসত। চন্দনের সুগন্ধী সাবান ছাড়া আমি গোসল করতে চাইতাম না। উমা নিজে হাতে আমার দাড়ি কেটে, ছাপছুপ করে, চন্দন সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দিত। গোসলের পরে নীল রঙের শিশি থেকে সুগন্ধী মাখিয়ে দিত। কয়েক বছরের মধ্যে উমার কোলে এল মিষ্টি, খিলখিল আর বাবুল। ওরা সকলে অধিকাংশ সময় আমার কাছেই থাকত। ওদের সাথে আসন পেতে আমাকেও খাইয়ে দিত উমা।
এদিকে নিনি ও কল্যাণীর ঘরেও এসেছে অনির্বাণ, অরিন্দম, অনিন্দিতা।
কল্যাণীর সঙ্গেও অনিরুদ্ধের বিয়ে ছিল প্রেমের, মাত্র আঠার বছর বয়সে সে আমার পুত্রবধূ হয়ে এসেছিল। তার দু’বছর আগে রাঁচিতে বেড়াতে গিয়ে তাদের পরিচয়, মন দেয়া-নেয়া, তারপর বিয়ে। কল্যাণী আমায় প্রথম দেখেছিল আমার অসুস্থ হওয়ার অন্তত এক দশক পরে। ও কোনো দিনই বিশ্বাস করে নি, আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। আমাকে অনেকবার পরীক্ষা করান চেষ্টা করেছে, আমিও আনন্দ পেয়েছি, নিজেকে পুরোটা মেলে ধরতে চাই নি। একবারের কথা বলি, ও একবার আমার অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য খাতা নিয়ে এল। খাতা এগিয়ে দিল আমার দিকে। অনিরুদ্ধ একটি কলম আমার দিকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘বাবা, বাবা ও তোমার সই চাইছে।’
কল্যাণীর কথায়—‘বাবা কয়েকবার ওর আর আমার মুখের দিকে চাইলেন তারপর কলম ধরে খাতায় বড় বড় অক্ষরে লিখলেন আমার স্বামীর নাম। আমরা তো অবাক। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে আমার স্বামী বাবার বুকে আঙুল রেখে বললেন, ‘তোমার নাম লেখ, তোমার সই চাই।’
কয়েকবার বলতে কাজ হলো। বাবা খাতাতে গোটা গোটা করে লিখলেন, কাজী নজরুল ইস… না, পুরোটা নয়, শেষ দুটো অক্ষর লেখার সময়েই লেখাটা জড়িয়ে গেল।’ কেন লেখাটা জড়িয়ে গেল—সে-কথা আমি এখানে বলব না।
আরো অনেক কারণে ওরা বিশ্বাস করতে চাইত না আমার অসুস্থতার কথা। কল্যাণী পুত্রবধূ হয়ে যখন প্রথমে আমায় প্রণাম করতে এল তখন অনিরুদ্ধ বলল, ‘এই দেখো আমার বউ, তোমার মিনির বউ!’ দু’তিনবার বলতেই আমি হেসে ফেললাম।
হাজারীবাগে থাকতে আমাকে নিয়ে ওরা প্রতিদিন বিকালে হাঁটতে বেরোত, ওরা কেউ আমার সঙ্গে হেঁটে পারত না, আমি ঝড়ের বেগে কোনো দিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলতাম—‘আমি আপনার তালে নেচে যায়, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!’। সপ্তাহে একদিন আমায় নিয়ে ওরা গাড়িতে ঘুরতে যেত, গাড়ির প্রতি আমার ছিল আজন্ম আকর্ষণ, অসুস্থ হওয়ার পরেও তা বিন্দুমাত্র কমে নি। ফিরতে চাইলে আমি সব সময়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছি। আমি গাড়ি কিনেছিলাম বলে কত নিন্দে—আগের বছর যে গাড়ি কিনল, পরের বছরে তার নেই চিকিৎসার পয়সা। আরে বাবা, তা না-হলে আমি কেন নজরুল, আমি কেন দুখু মিয়া, তারাখ্যাপা।
এরপর কে আর বলবে নজরুল নির্বোধ নির্বাক ছিলেন।
কল্যাণী প্রতিদিনের একটি রুটিন প্রকাশ করে প্রমাণ করতে চেয়েছে, অসুস্থতার সময়েও আমি নিরুদ্বেগ সুস্থ মানুষের মতো কিভাবে জীবন-যাপন করেছি, তার ভাষ্য—‘মা রোজ সকাল আটটায় দুধ আর পাউরুটি মেখে ডাকতেন বাবাকে। ডাকটা ছিল, ‘কই এদিকে এসো, খেয়ে যাও।’ পাশের ছোট ঘরটায় থাকতেন বাবা। দুঘরের মাঝে ছিল পর্দার ব্যবধান। ডাক পড়লেই বাবা চলে আসতেন এ ঘরে। আসন পাতা দেখলে তবেই বসতেন খেতে, নচেৎ নয়। মা শুইয়ে শুইয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন বাবাকে। আমাদের বাড়ির দুই ভৃত্য কিশোর সাহু আর কাট্টু সিং স্নান-টান করিয়ে দিত। বেলা বারোটা বাজলেই বাবা উসখুস করতেন খাওয়ার জন্য। ঘন ঘন দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাতেন। খাওয়ার পর আমরা যদি বলতাম ‘বাবা শোন’ অমনি লক্ষ্মী ছেলের মতো উনি শুয়ে পড়তেন।
যদিও দুপুরে তিনি বড় একটা ঘুমাতেন না। সারা দুপুর পায়চারি করে বেড়াতেন বাড়িময়। বিকালে কেউ গান শুনাতে এলে উনি খুব খুশি হতেন। গানের সঙ্গে তাল দিতেও দেখেছি। গানের সঙ্গে তবলা বাজালে তো কথাই নেই, খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠতেন। দেশাত্মবোধক গান পছন্দ করতেন ভীষণভাবে। আর কেউ না এলে একা একা বসে থাকতেন কি পায়চারি করতেন গোটা বাড়ি। সদর দরজার কাছে, কখনো কি বাথরুমের কাছাকাছি চলে গেলে মা যদি বলতেন ‘এই ওদিকে যেও না।’ বাবা কখনই সেদিকে যেতেন না, ঘুরে চলে আসতেন নিজের ঘরে। সাড়ে আটটা কি ন’টার সময় রাত্রের খাওয়া খাইয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বাবা কিছুতেই ঘুমাতেন না। জেগে থাকতেন অনেক রাত পর্যন্ত। আর বাবাকে পাহারা দেয়ার জন্য মাকেও জেগে থাকতে হতো। তাই আমরা যখন সকাল সাড়ে ছটা, সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠতাম তখন দেখতাম বাবা-মা দু’জনেই ঘুমোচ্ছে।’ দেখ মেয়ের কাণ্ড! এরপরে কে আর বলবে নজরুল নির্বোধ নির্বাক ছিলেন।
একবার উমা তাঁর ছেলে আমার নাতি বাবুল কাজীকে শুইয়ে রেখে রান্না ঘরে গেছে, আর আমি বাবুলকে নিয়ে আমার ছেঁড়া কাগজের স্তূপের মধ্যে শুইয়ে রেখেছি। ওরা বাবুলকে দেখতে না পেয়ে হন্যে হয়ে খোঁজ করছে—এত ছোট মানুষ কোথায় গেল। ওদের অবস্থা দেখে আমি আনন্দে হাততালি দিচ্ছিলাম, ওরা আমার কাছে এসে দেখল—কাগজের গাদার মধ্যে বাবুলকে শুইয়ে রেখেছি। আমার নাতিদের সঙ্গে এই সব দুষ্টুমি দেখে ওরা অবাক।
আরেক বারের ঘটনা বলি—তখন নিনির ছেলে অনির্বাণ খুব ছোট। দোলনায় শুইয়ে থাকার বয়স। দোলনাটি প্রমীলার চৌকির কাছে ঝোলানো থাকত, যাতে সে ওর দেখাশোনা করতে পারে, কাঁদলে দোল দিতে পারে। একদিন প্রমীলা ঘুমিয়ে পড়েছে, এরমধ্যে অনির্বাণ জেগে কেঁদে উঠল। আমি তখন ওদের ঘরে ছিলাম। অনির্বাণের কান্না শুনে এক ধরনের আওয়াজ করে প্রমীলার ঘুম ভাঙালাম। প্রমীলা বুঝতে পারল, সেও দুষ্টুমি করে হাতের ইশারায় অনির্বাণকে আমায় কোলে নিতে বলল। এর মধ্যে কল্যাণী ও অনিরুদ্ধ এসে হাজির। ওদেরও মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি। অনিরুদ্ধ ওর মাকে বলল, বাবাকে বল অনির্বাণকে দোলনা থেকে নিয়ে তোমার কোলে দিতে।
প্রমীলা ভয় পেয়ে বলল, ‘না না, বাচ্চা ছেলে যদি ফেলে দেন উনি।’
ওরা বলল, ‘আমরা তো পাশে থাকব। কিছু হলে ধরে নেব।’
ওরা বারবার অনুরোধ করতে আমি এক হাত দিয়ে অনির্বাণকে ধরে ওর দাদির কোলে দিলাম।
এই ছিল মূলত আমার অসুস্থ সংসার জীবনের খুঁটিনাটি। এর মধ্যে আমার জন্মভূমি চুরুলিয়ায় যাওয়ার সুযোগ ঘটল। প্রায় তিন যুগ আগে মায়ের প্রতি অভিমান করে মা ও মাতৃভূমি ছেড়েছিলাম—আমার সৃজনময় সুস্থ জীবনে আর কখনো সেখানে ফেরা হয় নি। মায়ের মৃত্যু প্রায় তিন দশক পার হয়ে গেছে, সহোদররা মারা গেছে। সমবয়সী বন্ধু-স্বজনদের দুএকজন এখনো বেঁচে আছে। মায়ের প্রতি জন্মস্থানের প্রতি আমি খুব সুবিচার করি নি, তবু এই দুরন্ত অবাধ্য সন্তানের নামে তার চিরদুখিনী মা, দুখিনী গ্রাম—চিরন্তন দুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে বাংলার সকল গ্রামে জেগে আছে।
আমার জন্মের দিনে উঠেছিল ‘ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর, উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহদ্বার’।
চুরুলিয়া আসার কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছে—সেই প্রয়োজনে আসা। এই তথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছেন আমার বন্ধু নাট্যকার মন্মথ রায়। মন্মথ রায়ের পরিবারের স্থায়ী নিবাস পশ্চিম দিনাজপুরের বালুঘাটে হলেও বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে ওর জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করে বালুর ঘাটে ফিরে ওকালতির পাশাপাশি নাট্য রচনায় বেশ নাম করেছে। এই তথ্যচিত্র নিয়ে মন্মথের ভাষ্য—‘বাংলার এই কবি দুলালের মহিমাময় পুণ্যজীবনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারই হ’ল আমার জীবনের মহাব্রত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজক রূপে আমার রচিত ও পরিচালিত তথ্যচিত্র ‘বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম’ কবির উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য।’
আমায় প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা মন্মথ বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে—‘বিদ্রোহী কবিতা লিখে কাজী নজরুল ইসলাম তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। একদিন তার কথা উঠতেই পবিত্র বললেন, ‘ও কাজীটার কথা বলছিস? তা ওটাকে আনব একদিন।’
আমি তো হাঁ!
বড় বেশি কথা বলতেন পবিত্র। কিন্তু সত্যি-সত্যিই তিনি অবাক করে দিলেন কাজী নজরুলকে একদিন আমাদের মেসে এনে। একটা শিহরন খেলে গেল আমার মনে। এই সেই কাজী নজরুল? আর পবিত্র তাঁর এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু? পূজারির মনোভাব নিয়ে সেদিন তাঁদের সামনে রেখেছিলাম চায়ের বাটি খাবারের থালা।’
আমার সাথে প্রমীলাকেও নেয়া হলো। প্রমীলা যেখানেই যেত পূর্ণাঙ্গ খাট বিছানাসহ যেত। বিয়ের পরে তার শ্বশুরবাড়ি দেখার সৌভাগ্য হয় নি। এই তার প্রথম শ্বশুরবাড়ির দেশে আসা, স্বামীর জন্মস্থানে আসা। শ্বশুর-শাশুড়ি না থাকলেও তার খাতির যত্ন কম হলো না। ঠিক নববধূর মতো গাড়ি থেকে নেমে জনতার পালকিতে চড়ে সে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াল। সে যে চুরুলিয়ার দুখুমিয়ার বউ। একটি শাদা পাঞ্জাবি, একটি শাদা ধুতি কুচি দিয়ে পরে আমি বরের বেশে পরিস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ন নজর রাখতে থাকলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমার হারানো শৈশব খুঁজে ফিরলাম। পুরনো বন্ধুবান্ধব, কোলকাতা থেকে আগত শৈলজা, অচিন্ত্য, নিতাই ঘটকসহ বিশিষ্টজন, এলাকার শিশু যুবা নারী পুরুষ আমাদের সংবর্ধনা জানাল। ফুলের মালা দিয়ে বরণ করল। চুরুলিয়া নবকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে লোকে লোকারণ্য। জ্যৈষ্ঠের রাঢ় অঞ্চলের গরম বাতাসে অনেকে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। প্রবল বাতাসে খেজুর আর দেবদারু গাছের পাতায় প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। ‘শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণিবায়/ জল তরঙ্গে ঝিল্মিল্ ঝিল্মিল্ ঢেউ তুলে সে যায়।’
আমার জন্মের দিনে উঠেছিল ‘ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর, উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহদ্বার’। জন্মের পরে তিনদিন নাকি কোনো সাড়াশব্দ কান্নাকাটি করি নি। সবাই তো ভেবেছিল এ ছেলে বাঁচবে না। গ্রামের এক সাধু পুরুষ জন্মের পরে আমাকে দেখেই বলেছিলেন—এ মহাপুরুষ হবে। ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিলাম, মা পেরে উঠতেন না, বাবা পাশা খেলায় ব্যস্ত, তারপর একদিন গেলেন মরে। সংসারে প্রচণ্ড অভাব, বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ মাদরাসায় যুক্ত থেকেছি কিছু উপার্জনের আশায়। আজ এখানে এসে কেবল মাকে মনে পড়ছে। দুখিনী মা আমার। মায়ের সাথে আমার আচরণ সংগত ছিল না। অনেকে আমায় দোষারোপ করেছে, গবেষকরা কারণ খুঁজতে চেয়েছে। মায়ের জন্য আমার আহাজারি কখনো বন্ধ হয় নি। অনেক মা নিয়ে আমি কথা বলেছি, কবিতা লিখেছি, আনেক মাকে বই উৎসর্গ করেছি। কিন্তু নিজের মায়ের ভালোবাসা নিয়ে লিখেছি ‘শায়ক-বেঁধা পাখী’—সেদিন কি আর আমি জানতাম একদিন এই কবিতার মতো আমায় এখানে ফিরে আসতে হবে, মা যেন কেঁদে কেঁদে বলছে—
‘হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মানিক!
দেখেই তোরে চিনেছি, আয়, বক্ষে ধরি খানিক!
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চিরকালের মা কি?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী!
কেমন ক’রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি।
এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই তো আমার ন’সরে অতিথ্ অতীত কালের কেহ,
বারে বারে নাম হারায়ে এসেছিস এই গেহ,
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য’দিন আছে বাকী!
প্রাণের আড়াল ক’রতে পারে সৃজন দিনের মা কি?
হারিয়ে যাওয়া? ওরে পাগল, সে তো চোখের ফাঁকি!’
চুরুলিয়া থেকে ফিরে এলাম। প্রমীলা নিজে নিজে কোথাও যেতে না পারলেও, উঠে বসতে না পারলেও এই শয্যাশায়ী শ্বশুরবাড়ি যাত্রা তার জীবনে একটি ঘটনা হয়ে থাকল। বিয়ের পর থেকেই তার শখ ছিল একবার চুরুলিয়া যাওয়ার। সে এখন খুব খুশি—এই যাত্রা কেবল তার জন্য নিছক শ্বশুরালয় গমন ছিল না, মৃত্যুর পরে তার চির আবাসের জায়গাটিও সে এই সুযোগে দেখে আসতে চেয়েছিল। আগেই নির্ধারিত করা হয়েছে কোথায় প্রমীলা ও আমার কবর দেয়া হবে। এখন আমরা দুজন মিলেই মূলত একজনে পরিণত হয়েছি, আমার দেহ সুস্থ আছে, চলাফেরা করতে পারি, ভীষণ জোরে হাঁটতে পারি, শরীরের চঞ্চলতা একটুও কমে নি। অন্য দিকে প্রমীলার মানসিক শক্তি, বুদ্ধির তেজদীপ্ততা, পারিবারিক সামর্থ্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু তার শরীর অচল, তার শরীর সে নিজে নিজে কোথাও বহন করে নিয়ে যেতে পারে না। চুরুলিয়া থেকে ফিরে এসে সে আরো নির্ভার হয়েছে।
কবিগুরুর চেয়ে আমার গানের সংখ্যা বেশি।
চুরুলিয়া থেকে ফিরে আসার পর ১৯৬০ সালে ভারত সরকার আমায় ‘পদ্মভূষণ’ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছে। গোলাকার একটি মেডেল, বার্নিসড ব্রোঞ্জের মধ্যে একটি পদ্ম, চারটি সোনালি রঙের পাপড়ি, ফুলের উপরে ও নিচে ‘পদ্মভূষণ’ কথাটি রুপালি গিল্টিতে খোদাই করা—আমার গলায় শোভা পাচ্ছে। আমার কাছে যদিও এসব এখন বান্দরের গলায় মুক্তোর মালার মতো—যার কাছে এখন মুক্তোর চেয়ে বাদামের দাম বেশি। যে হারিয়ে ফেলেছে পৃথিবীর বস্তুময় পার্থক্য, সব ধরনের মুখাপেক্ষিতার বাইরে তার অবস্থান। এখনো আমার বই পুস্তুক নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, পুরনো বইয়ের সংস্করণ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখা নিয়ে নতুন নতুন বই বেরুচ্ছে। গত বছরেও সম্পূর্ণ নতুন কবিতা নিয়ে বের হলো ‘নতুন সওগাত’ কাব্যগ্রন্থ। আমার অসুস্থতার পরে রেডিওতে আমার গান বাজানো কমে গিয়েছিল, সম্প্রতি তার পরিবর্তন হচ্ছে, আগে আমার গান বাজানো হতো আধুনিক গানের অনুষ্ঠানে, এখন ‘নজরুল গীতি’ বলে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছে, ফলে নতুন নতুন শিল্পীদের আবির্ভাব হচ্ছে, আমার গান আলাদাভাবে সংগ্রহের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। এতদিন সবাই জানত আমার গানের সংখ্যা এক দেড় হাজারের বেশি হবে না, তরুণ শিল্পী ও গবেষকদের চেষ্টায় ইতোমধ্যে তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সবাই বলছে, কবিগুরুর চেয়ে আমার গানের সংখ্যা বেশি, সংখ্যা শিল্প-উৎকর্ষের মাপকাঠি নয়।
কিছুদিন হলো প্রমীলার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কত আর সম্ভব, একা শয্যাশায়ী শরীরে আমার মতো একজন বৃদ্ধ শিশুকে সামলানো, জীবনের দুই দশক না যেতেই দুই পুত্রের মৃত্যু, মায়ের নিরুদ্দেশ, আমার অসুস্থতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা, পুত্রদের অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ—যদিও এসব আজ সে পেছনে ফেলে এসেছে, তবু বিগত জীবনে তার কষ্টের ইতিহাস শরীরে ছাপ রেখে গেছে। গভীর রাতে সবাই যখন সুপ্তির কোলে নিমগ্ন, চরাচরে যখন কেউ জেগে নেই, তবু প্রমীলা জেগে আছে, একা একা লুডু খেলছে, একা একা খেলছে চাইনিজ চেকার। অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আমায় পাহারা দিচ্ছে। কারণ রাতে আমি একটানা ঘুমাতাম না, অল্পতেই ঘুম ভেঙে যেত, ঘুম ভাঙলে এদিক-ওদিক চলে যেতে পারি—এই ভয়ে প্রমীলা জেগে থাকে। ঘর থেকে বাইরে যেতে গেলেই প্রমীলা বলে ওঠে—‘এদিকে এসো—বাইরে যেয়ো না। শোন, শুয়ে পড়ো।’ প্রমীলাকে না নিয়ে অসুস্থ জীবনে আমি এক পাও যেতাম না। আমরা দুই আহত পাখি, নিঠুর ব্যাধের তিরে আহত হয়ে পৃথিবীর ঝিলাম নদীর তীরে পড়েছিলাম। আজ তিরিশ জুন উনিশশ বাষট্টি সালের পড়ন্ত বিকালে মন্মথ দত্ত রোডের ভাড়াবাড়ি থেকে এক হংসমিথুন তার জোড়া হারাল।
‘বাহুর ডোরে বেঁধে আজো ঘুমের ঘোরে যেন
ঝড়ের বন-লতার মত লুটিয়ে কাঁদ কেন।
বনের কপোত কপোতাক্ষীর তীরে
পাখায় পাখায় বাঁধা ছিলাম নীড়ে।’
আমার নির্বাক জীবনের অনুভূতি প্রকাশের বিড়ম্বনা আর নিজে নিতে চাই না। কল্যাণীর এক অনুভূতির কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই—‘মা মারা যাবার পর যখন ভাশুর বাবাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেল, তখন যাবার সময় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বাবা ও মা এক ঘরে থাকতেন। ভাশুর যখন বললেন, ‘বাবা, চলো যাই। তিনি কিছুতেই নড়ছিলেন না। বোধ হয় ভাবছিলেন—আমার সঙ্গে চিরদিন যে থাকত—সে কোথায় গেল।’ অবশেষে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি দু’পা এগুলেন বটে কিন্তু বারবার পিছনে ফিরে শূন্য চৌকির উপরে কাকে যেন খুঁজছিলেন। সে দৃশ্য দেখে চোখের জল সেদিন রোধ করতে পারি নি।’ আমি তখনো মনে মনে গাইছিলাম—
‘খেলা শেষ হলো, শেষ হয় নাই বেলা
কাঁদিও না, কাঁদিও না
তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা॥’