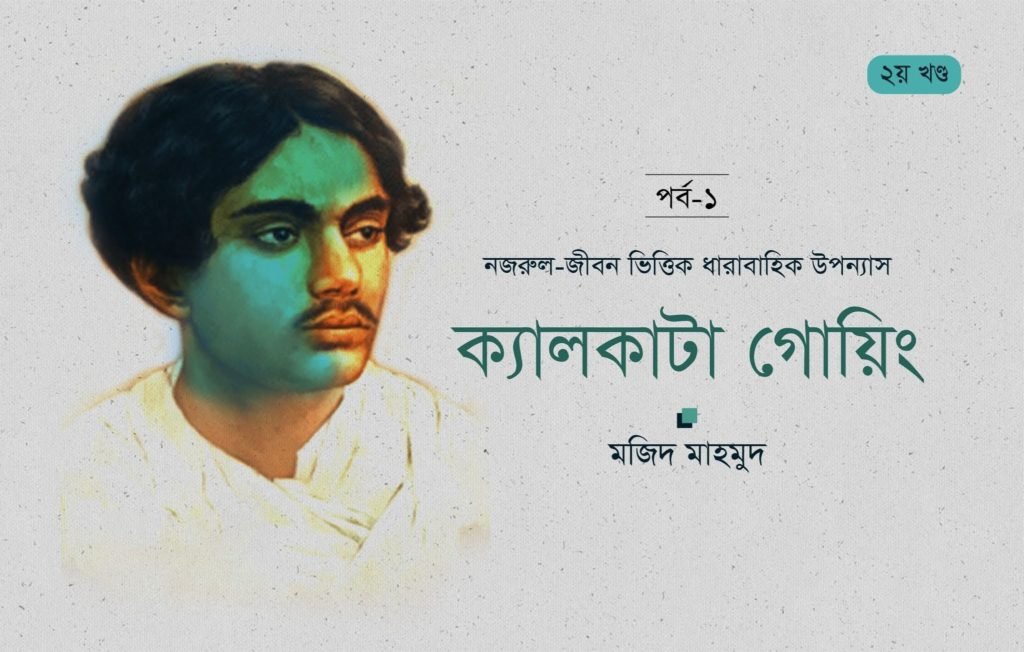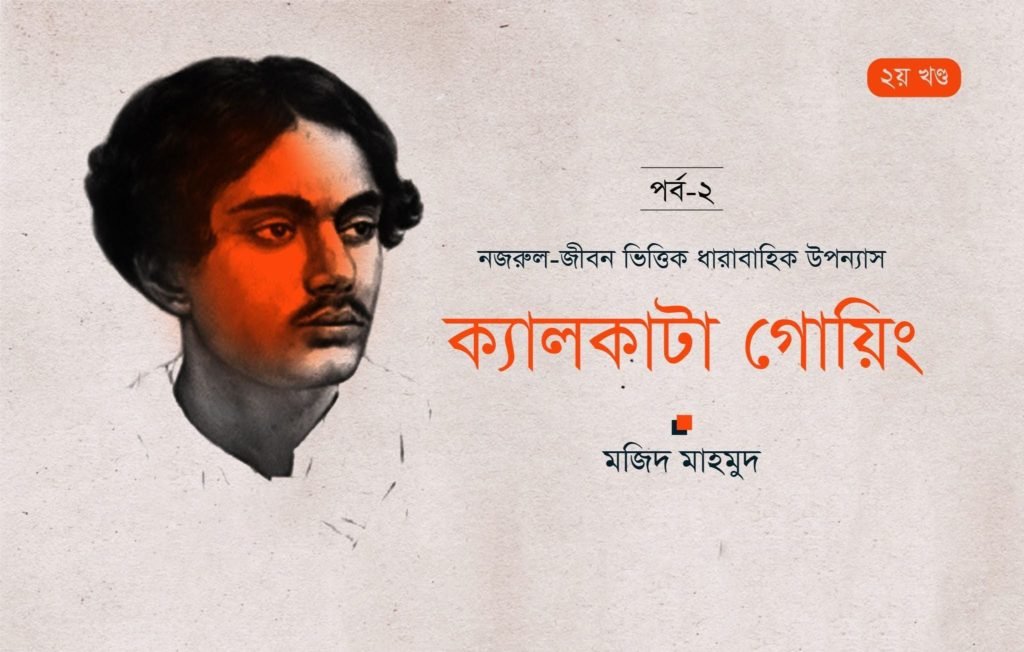পর্ব-১০
এটি ছিল আমার নির্বাক জীবনে কোলকাতা পর্বের শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অর্ধশত বছর আগে অখণ্ড বাংলার রাজধানীতে আমার কর্মময় জীবনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল—মাত্র দুই দশকের মধ্যে এক অজানা কারণে সেই উত্তুঙ্গ সৃষ্টিশীলতা নির্বাপিত হয়ে গেলেও প্রাণবায়ু এখনো ক্ষীণ উজ্জীবিত। আমার সত্তরতম জন্মবার্ষিকীর উৎসবকে কেন্দ্র করে এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রবীন্দ্রসদনে আমার সংবর্ধনার আয়োজন করেছে।
প্রমীলা মারা যাওয়ার পরে আমি ক্রিস্টোফার রোডে সব্যসাচীর বাসায় উঠে এসেছি। এটি আমার জীবনে যুগপৎ আনন্দের ও বেদনার ঘটনা। জীবনে একটি সময় বই বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও নিজের কোনো বাড়ি কেনার কথা ভাবি নি। গাড়ি কিনেছি, দুহাতে টাকা উড়িয়েছি—তারপর একদিন পথের নিঃস্ব। মাত্র বিশ বছরের মধ্যে তিরিশটিরও বেশি স্থানে বাসা বদল করতে হয়েছে, কখনো অভাবের তাড়নায় কখনো স্বভাবের তাড়নায়। আমার বাড়ি কেনা নিয়ে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের ভাষ্য—আমি অসুস্থ হওয়ার পরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখনো আমি কখনো কখনো দুএকজনকে চিনতে পারতাম। মঈনুদ্দীনকে দেখে সানি বলল, ‘বাবা, দেখুন কে এসেছে।’
আমার আগে দিল্লিতে এক কবি ছিলেন গালিব—তার সঙ্গে আমার জীবনের ছিল এক অদ্ভুত মিল।
আমি মাথা থেকে চাদর খুলে ফেললাম। তারপর তার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালাম। মুখ-চোখ হাসিতে ভরে গেল। সেই আগের হাসি।
বললাম, ‘কে মঈনুদ্দীন না?’
সে বলল, ‘হাঁ চিনতে পেরেছেন?’
এ-কথার আর জবাব দিলাম না। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলাম। সে ওখানে বসেই সানির সাথে গল্প করতে লাগল। কথায় কথায় সানিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এ বাড়ির ভাড়া কত?’
সানি বলল, ‘পঞ্চাশ টাকা।’
মঈনুদ্দীন দুঃখ করতে লাগল। বলল, ‘কতদিন থেকে অনর্থক এই ভাড়া গুনতে হচ্ছে। যখন অবস্থা একটা ভালোর দিকে ছিল, কিছু কিছু টাকা বেশ আসছিল, তখন তোমার বাবাকে বলেছিলাম, পার্ক সার্কাসের দিকে একটা বাড়ি কিনতে, তা-না করে তিনি কিনলেন গাড়ি। এখন গাড়িও গেল বাড়িও হলো না।’
আমি মুখের চাদর ফেলে দিলাম। তার মুখের দিকে দুএক সেকেন্ড তাকালাম। তারপর ওকে দিলাম জোরে এক ধাক্কা। বললাম, ‘যা তুই ঘর থেকে বেরিয়ে যা।’
তখনো আমার অহং মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে আসত। আমার কাজের সমালোচনা করলে আমি ভীষণ বিরক্ত হতাম। ভাবি, তারা তাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে আমায় চিনতেই পারে নি। কারণ আমি তো বিদ্রোহী কবি নজরুল :
‘আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা, করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।’
আমার আগে দিল্লিতে এক কবি ছিলেন গালিব—তার সঙ্গে আমার জীবনের ছিল এক অদ্ভুত মিল। মোগল ইংরেজের যুগসন্ধিক্ষণে তার জন্ম—আমার জন্মের একশ বছর আগে। তিনশ বছরের মোগল সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাসের সাক্ষী তিনি—আমিও দুশো বছরের ইংরেজ সাম্রাজ্য পতনের নীরব সাক্ষী। চার বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃব্যর আশ্রয়ে চলে আসতে বাধ্য হন গালিব। তার বিরুদ্ধেও ধর্ম না-মানার অভিযোগ উঠেছে, মহাবিদ্রোহের পরে ইংরেজ সেনারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, সম্রাটের পক্ষ নেয়ায় তার হতে পারত ফাঁসি। কর্নেল ব্রাউন সাহেব জানতে চেয়েছিল, ‘গালিব, আপনি কি মুসলমান?’ গালিবের উত্তর, ‘আধা মুসলমান।’ কারণ হিসাবে বলেছিলেন, ‘তিনি মদ্য পান করেন, কিন্তু শুয়োর খান না।’ জীবন ধারণের জন্য করেন নি কারো চাকরি, হাতে পয়সা এলে উড়িয়েছেন দেদার। পঞ্চাশ বছর দিল্লিতে বসবাস করছিলেন, পেয়েছিলেন মোগল সম্রাটের সান্নিধ্য, কিন্তু নিজের বসবাসের জন্যে কেনেন নি বাড়ি, থেকেছেন সারাজীবন ভাড়া। বই পড়েছেন—তাও ধার। শেষ জীবনে আমারই মতো রিক্ত, ভগ্ন-স্বাস্থ্য, ডায়াবেটিস, দেনার দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আদালতের সমন। পরপর সাত সন্তানের মৃত্যুর পরে পোষ্য নেয়া ভাতিজারও তেইশ বছর বয়সে মৃত্যু। তিনি আজ উর্দু কবিতার শুধু মুকুটবিহীন সম্রাট নন, দুঃখের রাজ্যেরও রাজাধিরাজ। একশ বছর আগে কোলকাতা এসেছিলেন—নিজের ভাগ্যের উন্নয়নে, দু’বছর ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের শিকা ছেঁড়ে নি। কোলকাতা বসবাসের চিহ্ন হয়ে ‘মির্জা গালিব স্ট্রিট’ এখনো ঘোষণা করছে—‘তোমার দরজার সামনেই ঘর বানিয়ে নিয়েছি আমি/ এবারও কি বলবে আমার ঘরের ঠিকানা জানো না তুমি!’ ঠিক লিখে রেখে গেছেন আমারই ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা—‘কেন বেঁচে আছ গালিব—এ প্রশ্ন অবুঝের/ আমার ভাগ্যে লেখা মৃত্যুর বাসনা নিয়ে আরো কিছু দিন বেঁচে থাকা।’ নজরুল এখনো বেঁচে আছে এই প্রশ্ন যারা করে তাদের বলতে চাই—আমি তো সে-কবেই জন্মে গেছি মরে।
ক্রিস্টোফার রোডের বাসাটি খুব ছোট্ট—দোতলায় উঠতে বাম পাশে ড্রইং ড্রাইনিং বাদে দুই কামরার বাড়ি। সুখের খবর এই বাসাটি সব্যসাচীর নিজের কেনা, আর বেদনার—এই জন্য যে এই নির্বাক বার্ধক্যে আমার আরেক সন্তান অনিরুদ্ধের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং প্রিয়তমা স্ত্রী প্রমীলার স্পর্শহীন চারি দেয়াল। এখানে আসার পরে আমায় দেখা-শোনা করার জন্য দুলাল শেখ নামে এক যুবককে নিয়োগ দিয়েছে সানি। ওর বাড়ি বর্ধমানের কয়াথা গ্রামে। এখানে আমার প্রাত্যহিক রুটিন নিয়ে দুলাল শেখের স্মৃতি চারণ এমন :
‘উমা কাজীর তত্ত্বাবধানে কাজে যোগ দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই, কবির সুবিধা-অসুবিধার দেখভাল এবং বিশেষভাবে তাঁকে খাওয়ানোর কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল দুলাল। যদিও খাওয়ানোর কাজ উমাই করে। প্রমীলা আর উমা ছাড়া আমি অন্য কারো হাতে খেতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি না। সকালে উমার গুলে দেওয়া হরলিক্স এবং একটু বেলা হলে ভেজা চিঁড়ে কলা মাখিয়ে চামচ দিয়ে খাওয়ানো হতো আমাকে। ডায়াবেটিস থাকায় চিনি দেওয়া হতো না। দুপুরে ভাতের সঙ্গে ডাল চটকে স্টু-র মতো করতে হতো। সঙ্গে হালকা মাছের ঝোল। বিকেলে চায়ে ভেজানো বিস্কুট কিংবা দুধ-পাউরুটি। এ সবই দুলালের স্মৃতিচারণে উঠে আসা। খাওয়ার বিষয়ে আমি আপত্তি করতাম না। খাওয়ার আর ইচ্ছা না থাকলে, অনিচ্ছাটা মুখভঙ্গিতেই প্রকাশ করতাম। দুপুরে কিছুটা ঘুমোতাম। কোনো কোনো সময় বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে টলোটলো পায়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াতাম। বিভোর হয়ে বাইরের সব কিছু দেখতাম। এখনো আমি হাঁটাচলা ভালোই করতে পারি।
দুলাল শেখের স্মৃতিচারণের সূত্রেই জানা যায়, আলিপুর হাসপাতালের চিকিৎসক অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় আসতেন স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য। গুণগ্রাহী বিশিষ্ট মানুষজনও আসতেন সময়ে সময়ে। গানও শোনানো হতো। তবে, পছন্দের গান না হলে, বা বেসুরে গাইলেই আমি খানিক উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। তখন পাল্টাতে হতো গান। পছন্দের গানে নিজের হাঁটুতে হাতের টোকা মেরে তাল দিতাম। যাঁরা সে-সময় আসত আমার কাছে, তাঁরা দুলালের হাতে দু-এক টাকাও দিয়ে যেত। মাঝে মাঝে চুরুলিয়া থেকে এই বাড়িতে আসত ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী মোজাহার হোসেন। তাঁর সঙ্গী হিসাবে খুড়তুতো ভাই হাঁদু কাজীও আসত। তাঁরা আসলে এই বাড়িতেই থাকত।’ দুলাল আমার সাথে আমার সেবা করার জন্য ঢাকায়ও গিয়েছিল। কিন্তু আমার মৃত্যুর সময়ে কাছে থাকতে পারে নি। বিয়ে করার জন্য কোলকাতায় ফিরে সংসার জীবনে আটকে পড়ে।
এ সময়ে প্রতি বছর আমার জন্মদিনে পুরনো শিল্পীর সঙ্গে নতুন শিল্পীরা গান শোনাতে আসত, তাদের মধ্যে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ওকে আমি সুস্থ কালেই দেখেছি, ওর কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিল আমার বন্ধু, মেহেদী হাসান ও জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে সে গান শিখেছিল। আমি শিশু মানবেন্দ্রের নাম দিয়েছিলাম ‘ঘিয়ে কড়ি’—সারাক্ষণ রত্নেশ্বরের পাশে ঘুরঘুর করত। খুব ফর্সা টুকটুকে ছিল। আমার কাছে ও গান শেখার মতো যথেষ্ট বড় ছিল না। তবু, ‘সখী সাজায়ে রাখল পুষ্পবাসর’ এবং ‘হে মধাব হে মধাব।’ গান দুটি আমার কাছে তালিম নিয়েছিল।
মানবেন্দ্রর গান শেখা মূলত বিমান মুখোপাধ্যায়ের কাছে। বিমান আমার কাছে গান না শিখলেও সঠিক নিয়মে গাওয়ার জন্য মান্যতা পেয়েছিল, আর প্রথম দিকে আমার গানের সংগ্রাহক হিসাবে তার নাম হয়েছিল। বিমান এবং মানবেন্দ্র একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। বিমানের স্মৃতি কথায়—‘গ্রামোফোন কোম্পানির সন্তোষ সেনগুপ্ত মশাইয়ের কথা মতো এক সকালে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, “আপনি মশাই নজরুলগীতি শেখাবেন!” আসুন আসুন বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রথম দর্শনের প্রতিক্রিয়া যত দিন বাঁচব মনে রাখব।’ বিমানবাবুর ছোটখাটো চেহারা দেখে মানবেন্দ্রর মনে হয়েছিল, এই ছেলেটা আবার কী গান শেখাবে? সবার ধারণা ছিল নজরুলের গান শেখানোর জন্য শারীরিক বলেরও প্রয়োজন হয়।
এমনকি আঙুরবালাকে বিমান কিছু গান শিখিয়েছিল। এখানেও তার মজার স্মৃতি রয়েছে—‘এক দিন গান শেখাচ্ছি আঙুরবালাকে, ‘তব চরণপ্রাান্তে’। সংগীতসম্রাজ্ঞী বলে উঠলেন, ‘মাস্টার, তুমি ফাঁকিবাজ। তোমার কাছে শিখব না। তোমার যদি ধৈর্য না থাকে তবে তুমি শেখাচ্ছ কেন? আমার গলার সম্পূর্ণ কাজটা না দেখেই তুমি বলে দিলে, হয়েছে?’ ‘স্বীকার করলাম অন্যায় হয়েছে।’ আঙুরবালা বললেন, ‘শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি, আমার যৌবনের গলা এখন আর নেই। থাকলে দেখিয়ে দিতাম তুমি কত বড় ওস্তাদ হয়েছ! জমিরুদ্দীন খান সাহেব করোগেটের শেডের ওপরে একটা ছড়ি টেনে কড়কড় আওয়াজ করে বলতেন, এ রকম স্বর বের করো। আমি সেই ‘দানা’ সুর বের করতাম।’
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে বিমান দিদিভাই ডাকত। একদিন সন্ধ্যার স্বামী শ্যামল গুপ্ত বিমানকে বলল, ‘তোর দিদিভাই তোকে ডেকেছে। নজরুলের গান শিখবে। আজও আমার মনে হয়, আমি ‘ওগো মোর গীতিময়’-এর গায়িকার সামনে বসে আছি। সন্ধ্যা বলেছিলেন, ‘আমি স্বরলিপি ও রেকর্ড ব্যবহার করি না। আমাকে খুব ধৈর্য ধরে একখানি করে গান শেখাতে হবে।’ আমার দশটা গান তুলে ওর কাছে রেকর্ড করল সন্ধ্যা।
আমি অসুস্থ হওয়ার পরে আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে এক রহস্যময় কারণে যোগাযোগ কমে গিয়েছিল।
সত্তরতম জন্ম দিনের বছর দুই আগেও এক জন্মদিনে আমায় আনা হয়েছিল রবীন্দ্র-সদনে। তার স্মৃতি নিয়ে মানবেন্দ্র বলল, ‘আমি রবীন্দ্রসদনের মাঠে আম্রকাননে গেয়েছিলাম—‘তরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী।’ খুব দরদ দিয়ে গেয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা এক্সপ্রেশন লক্ষ করেছিলাম কবির চোখে মুখে। দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ছিল জল। মনে হচ্ছিল এবার জেগে উঠবেন ওই নীরব যোগী।’
মানবেন্দ্র নূরুল ইসলাম মোল্লাকে গল্পচ্ছলে বলল, ‘জানো, আর একটি স্মৃতি বড় উদ্বেল করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের টিভি একটি তথ্যচিত্র তুলে ধরেছিলেন কবিকে নিয়ে। সেদিন ওর সামনে ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে গান করেছিলাম আমি ‘কুহু কুহু কোয়েলিয়া’। ওহ, কবির কী অদ্ভুত ভাবাবেগ! উনি বারবার ঘাড় দোলাচ্ছিলেন। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে হাত দেখাচ্ছিলেন হারমোনিয়ামের দিকে। ওর হাতে কিছু বইপত্তর দেয়া হচ্ছিল, উনি তা পাশে সরিয়ে রাখছিলেন। মনে হলো ওঁর গান উনি চিনতে পেরেছেন, ওঁর স্মৃতিতে ফিরে এসেছে, কিন্তু উনি কথা বলতে পারছেন না। গান শেষ করার পর আমার বুকে জমাট কান্না, কবির চোখেও জল। এ স্মৃতি আমি ভুলতে পারব না।’
মানবেন্দ্র বলল, আজ তোমরা ভাবতেও পারবা না ‘এককালে নজরুলের গান গাইতে গিয়ে টিটকারি বিক্ষোভ হঠকারিতার মুখোমুখি হয়েছি। চন্দনগর ফাংশন করতে গিয়ে তো আমার কপালে ইটের টুকরো জুটেছিল। কিন্তু আমার জিদ কমে নি। নজরুল গীতির নামকরা শিল্পীরা তখন নজরুলের গান ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যের গান গাইছিলেন। কেউ বোম্বে গিয়ে ফিল্মের সুরকার হচ্ছিলেন। আর ষাটের দশকে আমি আধুনিক গানের পপুলার শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক ছেড়ে নজরুল গীতি গাইছিলাম। লোকে ভেবেছিল আমি পাগল। না খেয়ে মরব। কিন্তু আমি জানতাম, আমার অদ্ভুত প্রত্যয় জন্মেছিল, নজরুল গীতি পপুলার হবেই। সে সময় নজরুল গীতিকে জনপ্রিয় করার জন্য পপুলার শিল্পী দিয়ে নজরুল গীতি গাওয়ানো হতো—আর এখন জনপ্রিয় শিল্পীদের নিজেদের অস্তিত্ব, আইডেন্টেটি রক্ষার জন্যই নজরুল গীতি গাইতে হচ্ছে।’
ধীরেন্দ্র মিত্র বলল, ‘আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে কবির বাসগৃহে গিয়েছিলাম। কবির সামনে গিয়ে বসে আছি। কাজীদা আড়চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে আবার হারমোনিয়ামের দিকে চোখ ফেললেন। আমি পরপর কবির রচিত ও সুরারোপিত চারটি গান গেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শৈলেন রায়ের একটা গান ধরলাম। হঠাৎ কবির দিকে চাইতে দেখি তিনি মোটা মোটা চোখে আমার দিকে তার বিরক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই গানটি অসমাপ্ত রেখে কাজীদার অন্য একটি গান ধরলাম। আমি যে কটা গান গেয়েছিলাম কাজীদা সব কটিতেই দুহাতে তালি বাজিয়ে তাল দিচ্ছিলেন এবং সেই তাল কখনো বেতাল বা বেসুরো মনে হয়নি।’
বিমলাভূষণও সায় দিল, ‘কবির জন্মদিনে ওর সামনে যখন ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে গাইলাম ‘ফলের জলসায় নীরব কেন কবি, সেদিনও বাকহারা কবির মুখে অদ্ভুত এক্সপ্রেশন লক্ষ করার মতো। ওঁর দুচোখ বেয়ে তখন লবাণাক্ত অশ্রুর ঢল নামছে। সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন ছোট ভাই প্রভাতভূষণ, কবির পাশে ওর বন্ধু মঈনুদ্দীন হুসায়ন ও উমা কাজী।’
সুপ্রভা সরকারও এসেছিলেন ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে। সে গাইল—‘অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী।’ এছাড়া ‘আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ’, ‘চৈতালী চাঁদনি রাতে’ গান দুটিও গাইল। এ দুটি গান যে আমি পছন্দ করতাম সুপ্রভা তা জানত। ও বলেছে—‘অন্য গান গাইতে শুরু করলেই নজরুলের লালা পড়া বন্ধ হয়ে যেত এবং ট্যাপট্যাপ শব্দ করতেন। বুঝে নিতাম নজরুল উক্ত গান দুটি গাইতে বলেছেন। উক্ত গান দুটির যে কোনো একটি গাইতে শুরু করলেই তিনি চুপ হয়ে যেতেন।’
সুপ্রভা সরকারকে নিয়ে একবার বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। উনচল্লিশ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বেতারের উদ্বোধনে আমার সঙ্গে অণিমা দাশগুপ্ত, শৈল দেবী, দেবাশীষ দাসগুপ্তা, চিত্রা রায় ও সুপ্রভা ঢাকায় গেছিল। রাতে স্টিমারে সুপ্রভা বেঁকে বসল সে কিছু খাবে না। স্টিমারের কর্মীরা সবার জন্য সানকিতে ভাত সবজি ও ইলিশ মাছের তরকারি পরিবেশন করেছিল। সুপ্রভার আপত্তি এই স্টিমারের পরিচালক থেকে শুরু করে সকলেই মুসলমান। ফলে এখানে খেলে তার জাত থাকবে না, পাপিষ্ঠ হবে।
আমি তাকে গিয়ে বললাম, ‘কেন রে বুড়ি খাবি না কেন?’ আমি সুপ্রভাকে বুড়ি ডাকতাম।
সুুপ্রভা বলল, ‘ওরা সব মুসলমান। আমি মুসলমানের হাতে খাব না।’
আমি হাসতে হাসেত বললাম, ‘আমিও তো মুসলমান।’
সুপ্রভা বলল, ‘আপনি মিথ্যা বলছেন, আপনি কিসের জন্য মুসলমান হতে যাবেন।’
বললাম, ‘কেন রে আমারে দেখে কি তোর মুসলমান মনে হয় না?’
ও বলল, ‘না।’
আমি বললাম, ‘দ্যাখ বুড়ি শিল্পীর কোনো জাত হয় না।’
সেদিন আমার কথায় দ্বিমত না করে সুপ্রভা মুসলমানের হাতে খেয়েছিল। পরবর্তী জীবনেও আর এ ধরনের জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে কথা বলে নি।
ছেষষ্টি সালে ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে কিংবা রবীন্দ্র সরণির অনুষ্ঠানে সরযুবাল এসেছিল কি না আমার স্মরণে নেই। তবে সে সব্যসাচীর সঙ্গে আমায় দেখতে এসেছিল, গান শুনিয়ে গেছে। ওর ভাষ্যানুসারে, ‘কাজীদা ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে সেই জীবন্ত চোখ দিয়ে চেয়ে রইলাম। মুখের ভাষা বন্ধ হলেও তার চোখের ভাষা অক্ষুণ্ন ছিল। আমি তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করলাম, বললাম, দাদা, আমি সরযু—আমি এসেছি, আমায় আদর করবেন না? দেখলাম কাজীদার ঠোঁট কেবল নড়ছে—কী যেন বলতে চাইলেন, কী এক অব্যক্ত বেদনা তার চোখে মুখে। আমি কেঁদে ফেললাম।’
তবে বাষট্টির পরে ফিরোজা বেগম, কমল দাশগুপ্ত, আব্বাসউদ্দীন—এরা কেউ এসব অনুষ্ঠানে তেমন উপস্থিত থাকতে পারেন নি। আমি অসুস্থ হওয়ার পরে আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে এক রহস্যময় কারণে যোগাযোগ কমে গিয়েছিল, কিন্তু আজ আমার এই প্রিয় বন্ধু অকালে লোকান্তরিত, চাইলেও তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। ফিরোজা বেগম ষাটের দশকের মাঝামাঝি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে যায়, আব্বাসউদ্দীন তারও আগে। নতুন দিনের শিল্পীদের মধ্যে মানবেন্দ্রর মতো ফিরোজা বেগমও আমার গান গেয়ে কিছুটা নাম করেছিল। ফিরোজা বেশির ভাগ গান কমল দাশগুপ্তের সুরে গাইত। কমল দাশ আমার অনুমোদনক্রমে বেশ কিছু গানের সুর করেছিল। এ সময়ে মহাজাতি সদনে তিন দিনব্যাপী নজরুল জন্মজয়ন্তীর উৎসবের আয়োজন করা হয়। ফিরোজা বেগম এতে বেশ ভূমিকা রেখেছিল। এখানে সন্ধ্যা, হেমন্ত, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপ্যাধ্যায়সহ আধুনিক ও রবীন্দ্র সংগীতের নামি লিল্পীরাও উপস্থিত ছিল।
এক জন্মদিনে আঙুরবালা চোখের জল মুছতে মুছতে গাইল—‘ওগো পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল’। শিল্পী বীরেন্দ্র চন্দ্র গাইল—‘ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি’। সুপ্রভা সরকার—‘অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে’। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়—‘ওরে নীল যমুনার জল’, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—‘কে গো আমার সাঁঝ গগনে’, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়—‘দিতে এলে ফুল হে প্রিয় আজি সমাধিতে মোর’, ধীরেন বসু ‘শূন্য এ বুকে পাখি মোর’। সেদিন রবীন্দ্রসদনে আমার গানে গানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।
আমি যাদের গুরু ছিলাম—তাদের প্রেমিক ছিলাম না।
ধীরেন দাস ও বীরেন্দ্র ভদ্রও এ সময়ে নিয়মিত আসত। একবার ধীরেন ও বীরেন্দ্র আমায় দেখতে এল। ধীরেন গান গাইল। গান শুনে আমি হাততালি দিলাম। মুখ দিয়ে কিছু বলতে চাইলাম। আমার এই না বলতে পারায় বীরেন্দ্র কেঁদে ফেলল। এক সময় ধীরেন দাস ও আমার বাসা ছিল হরিঘোষ স্ট্রিট ঠিক সামনা সামনি। আমরা প্রায় এক পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। একবার খুব মজার কাণ্ড হয়েছিল। একবার ধীরেনের ছোট্ট মেয়ে আমার বাসা থেকে ফিরে গিয়ে ওর বাবাকে বলল, ‘বাবা, ভারি মজা হয়েছে।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কী মা?’ মেয়ে বলল, জ্যাঠামশাই শাড়ি পরে মেয়েছেলে সেজে রান্নাঘরে রান্না করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জ্যাঠামশাই এ কী? জ্যাঠামশাই বললেন, ‘কী করব মা—তোর জ্যাঠাইমার সঙ্গে মায়ের (আমার শাশুড়ির) রাগারাগি হয়েছে—তাই আমিই তোর জ্যাঠিমার কাজ করছি।’ আমার এ অবস্থা দেখে ধীরেনের মেয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। সে ছুটে ছুটে সারা পাড়ায় বান্ধবীদের এ কথা বলে বেড়াল। এই পাড়াতে প্রথম যখন বাসা ভাড়া নিই তখন অনেকে জাতপাতের কারণে অখুশি হয়েছিল, পরে আমাকে ছাড়া তাদের চলতই না।
এ সময়ে আমার বিভিন্ন জন্মদিনে কাননবালা, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, দীপালি নাগসহ অনেকেই এসেছে, আমায় গান শুনিয়েছে। কাননদেবীর পক্ষে খুব বেশি সম্ভব হতো না। গান সে ভালোই গাইত—‘ছন্দে ছন্দে দুলিয়া নন্দে আমি বনফুল গো’ ‘আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই’—গান দুটি গেয়ে খুব নাম করেছিল। তবে সে চলচ্চিত্রের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম দিককার অনেক ছবির কাহিনি ও গান রচনায় আমার ভূমিকা ছিল। কানন এখানে নায়িকা হিসাবে এসেছিল। আমার ও জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে গান শিখত। কানন লিখেছে—‘মাঝে মাঝে মনে হয় কবি কি সত্যিই নীরব? নাকি আপন ধ্যানের জগতে সমাহিত বলেই বাইরের জগতের কোনো কোলাহল তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারছে না? এককালে দেখা মাত্রই আনন্দে যার মন ভরে উঠত আজ তাঁকে নীরব প্রণাম জানিয়ে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। জন্মদিনে কবিকে ঘিরে সকল উৎসব সভা যখন তাঁরই গানে, কথায় সুরে ঝলমল করে ওঠে, কবিরই ভাষায় তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ‘ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?’
কাননকে নিয়ে একটি বাজে কৌতুক চালু করেছিল ঈর্ষাকাতররা—বলত, ‘ও নজরুলকে পাচ্ছ না! তাহলে দেখ কানন দেবীর ঘরে আছে।’ কাননের ঘরে অবশ্য অনেকেরই মন পড়ে থাকত। আমি যাদের শিক্ষক ছিলাম, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক গুরু শিষ্যের। রানু সোম, নোটন মৈত্র, কাননদেবীর মতো বহু সুন্দরী বুদ্ধিদীপ্ত নারীগণ আমার কাছে গান শিখেছে, তাদের সাথে আমার অতিরিক্ত সম্পর্ক থাকলে তা নার্গিসের মতো, ফজিলাতুন্নেসার মতো, জাহানারার মতো গোপন থাকত না, আমি যাদের গুরু ছিলাম—তাদের প্রেমিক ছিলাম না। সত্যিকার অর্থে আমি ওই সময়ে কেবল ফজিলাতুন্নেসারই প্রেমে পড়েছিলাম, আর কারো নয়। কবি হিসাবে আমার সম্পর্কের উপলব্ধি মাত্রা সর্বত্র প্রকাশ করেছি। প্রকাশে অক্ষমদের ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।
এ সময় আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল ড. ডি. কে. রায়। আমার এক জন্মদিনে সব্যসাচীর আমন্ত্রণে ক্রিস্টোফার রোডের বাসায় এসেছিল। এর কয়েক বছর পর উনসত্তর সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার তাকে আমার চিকিৎসার ভার দেয়। ড. রায় প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। দর্শনার্থীদের চাপ সহ্য হচ্ছিল না। গান বাজনা শুনতে আমার ভালো লেগেছে, লোকজনের কোলাহল সর্বদা ছিল কাঙ্ক্ষিত, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সীমিত পর্যায়ে নিজের গান শুনে প্রফুল্ল হয়েছি, কিন্তু অতিরিক্ত চাপ অপরিচিত লোকজন সহ্য করতে পারি নি। ডাক্তারদেরও ভাষ্য তা-ই, অশোক বাগচী, ডি. কে. রায়, পরবর্তী পর্যায়ে অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ও আমায় দেখত; তারাও বলেছে, শুরুতে আমি ডাক্তারদেরও সন্দেহ করতাম। কিছুদিন গেলে সে সমস্যা দূর হতো, প্রেসার মাপার জন্য নিজেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, শুতে বললে শুয়ে পড়েছি, চোখের চাহনিতে স্বাগত জানিয়েছি। আমি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকায় গেলে ডাক্তার হিসাবে ডি. কে. রায় এবং অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় সঙ্গে যায়। অঞ্জলি নিজেও খুব ভালো গাইত। গানের প্রতি ভালোবাসাই ওকে আমার কোলকাতা জীবনের শেষ পর্বে কাছে নিয়ে এসেছিল। সব্যসাচীর অগ্নিবীণা আবৃত্তি সংগঠনেও ও সক্রিয় ছিল। একদিকে পুরনো ধারার আবৃত্তিকারদের পাশাপাশি নতুন ধারার বাচিকশিল্পীরা আমার কবিতা আবৃত্তি করছে, সব্যসাচী নিজেই একটি ধারার প্রবর্তন করেছে। বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে রাতারাতি নাম করেছে, প্রচুর ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। পুরনো দিনের জলদ্গম্ভির শম্ভুমিত্র যেমন ছিল, তেমনি আজকের জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ও সব্যসাচীর অনুরক্ত হয়ে এ দলে ভিড়ে গিয়েছিল, ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে সেও আসত, ওর বাবা কালীকানন্দও ভালো আবৃত্তি করত।
উনিশশ আটষট্টি সালে একই বছরে আমার জন্মভূমি চুরুলিয়ায় ও ঢাকায় নজরুল একাডেমি নামে দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আমার রচনা ও জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন, গবেষণা ও প্রকাশ করা। একই সঙ্গে বাণী ও সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রমিতকরণ, প্রকাশ ও রেকর্ডিং, অনুবাদ ও গবেষণা করা। চুরুলিয়ায় আমার আদি নিবাসের স্থলে একাডেমির ভবন উঠেছে। স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে নজরুল মুসলিম হাই স্কুলের গোড়া পত্তন করা হয়। অনেকের আপত্তির মুখে পরে মুসলিম শব্দটি বাতিল করা হয়েছে। তারা বলেছে, নজরুলের মতো একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির নামে কোনো কিছু শুধু ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। তবু আদি কাল থেকে খ্রিষ্টান স্কুল, বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু কলেজ, মুসলিম মাদরাসা হয়ে আসছে—এসব হয়তো সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ টিকে থাকার লড়াইয়ের অংশ।
আজ আমার সত্তরতম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রথম সংবর্ধনা জানাচ্ছে। জন্মদিনের কয়েক দিন আগে থেকে আমার শরীর ভালো যাচ্ছিল না, মেজাজ খিটখিটে ছিল। সবার সন্দেহ ছিল শেষ পর্যন্ত আমি উপস্থিত হতে পারব তো রবীন্দ্রসদনে। বিষয়টি আমার পারিবারিক ও সরকারি ডাক্তার ডি. কে. রায়কে সব্যসাচী অবহিত করে। আমার স্বাস্থ্যগত যে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যাতে তাৎক্ষণিক সামাল দেয়া যায়, সে-জন্য ডাক্তারকেও সঙ্গে নেয়া হলো। সেখানে অগণিত জনসাধারণ আমাকে এক নজর দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এই জন্মবার্ষিকী স্মরণযোগ্য করে রাখতে রাজ্য-সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। আমার বসবাসের জন্য সরকারি জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজন বেশ সুচারু ছিল, ভুল ধরার সুযোগ ছিল না। এখানেই অঞ্জলির সঙ্গে পরিচয় হলো, সানি নিনি বলল, ‘বাবা, অঞ্জলি তোমার গান করে।’ ওই দিন সন্ধ্যাতে সে সানির বাসার অনুষ্ঠানে গেয়েছে।
তবে আমায় নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, আমার পক্ষে পুরো সময় অনুষ্ঠান স্থলে থাকা সম্ভব হয় নি। মঞ্চের উপরে আমার সঙ্গে শৈলজা ও বামফ্রন্ট সরকারের কর্তাব্যক্তিরা আসন নিয়েছিল। নিচে শিল্পীরা গান গাইছিল। সমবেতভাবে শিল্পীরা ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গান শুরু করলে আমার মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, আমিও মঞ্চ থেকে নিচে নেমে শিল্পীদের সঙ্গে অংশ নিতে চেষ্টা করি। যেহেতু আমি কথা বলতে পারি না, আমার বুদ্ধি যেহেতু যৌক্তিক রীতি মেনে চলে না, সেহেতু তারা ধরে নিয়েছিল, আমার চাঞ্চল্যের কারণ অন্য কিছু। তাই তাড়াহুড়ো করে আমায় মঞ্চ থেকে নামিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে।
সকাল আটটা না বাজতেই পুরো রাস্তা অনুরাগীদের দখলে চলে গেছে। সবার হাতে পুষ্পস্তবক, শেফালি গাঁদার মালা।
এর পরের বছরটা ছিল কোলকাতায় আমার শেষ জন্মদিন, আমার বাস্তুচ্যুতির বছর। প্রায় তেইশ বছর আগে বাংলা তথা ভারত বিভাগের যে ক্ষত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, আমিও সর্বশেষ তার চূড়ান্ত শিকার হলাম। দেশ ভাগ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং পারিবারিক ও জাতীয় বিপর্যয়ের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। একটি মহাবিস্ফোরণের ধাক্কায় পৃথিবীটা যেমন আজও ঘুরে চলেছে, ঠিক সাতচল্লিশে উপমহাদেশে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছিল তার ধাক্কায় এখন নতুন নতুন দেশ প্রদেশের সৃষ্টি হচ্ছে, রেখে যাচ্ছে অমোচনীয় ক্ষত। যে পূর্ব-বাংলা একদিন তার নিজের ভাষার বন্ধন ত্যাগ করে ধর্মীয় তমুদ্দুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার মাইল দূরের ভিনভাষী পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, আজ তার বন্ধন ছিন্নের শেষ ধাপে উপনীত হয়েছে।
সেই গিঁট ছেঁড়ার প্রাক-মুহূর্তের জন্মদিনের কথাও বলতে চাই, এন্টালি ক্রিস্টোফার রোডে, আমার তৃতীয় পুত্র—জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্রের নিজস্ব আলয়ে এবং কোলকাতা পর্বের শেষ জন্মদিনের আগে, ১১ জ্যেষ্ঠ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৭০ খ্রিষ্টীয় সাল। জ্যৈষ্ঠ মাসের এই সময়টা সকালের দিকে সচরাচর বৃষ্টি হয় না, তবু আজ ভোর থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাতে বেশ কিছুটা বৃষ্টি ও ঝড় হয়েছে, ভোরের দিকেও হালকা দু’এক পশলা বারিপাত হয়েছে। রাস্তার খানাখন্দে কিছুটা পানি জমে থাকলেও লোক চলাচলে বাধা হচ্ছে না। এলাকার যুব সমাজ ও কোলকাতা পৌর কর্পোরেশনের লোকজন রাতে ক্রিস্টোফার রোডের প্রবেশ পথে তৈরি করেছে নজরুল জন্মজয়ন্তীর বিশাল তোরণ। লালসালু কাপড়ে মোড়া তোরণটি বিদ্রোহীর রং নিয়ে ক্রিস্টোফার সাহেবের দম্ভে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে।
দুপাশের সারি সারি সি.আই.টি. প্রকল্পের ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটিতে তৈরি করা হয়েছে বিশাল মঞ্চ। স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মীরা নিজেরাই সোৎসাহে করছে সকল কাজ। কেউ সামনে চেয়ার বসাচ্ছে, কেউ চাঁদোয়া টানানোর কাজে সহায়তা করছে, কেউ খুঁটি পুঁতছে, এ যে নজরুল-জয়ন্তী—তারুণ্যের প্রতীক, এরা যে শ্রমিক-রাজ কায়েম করতে চায়—‘ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল!/ ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।’—এই মঞ্চে হবে মূল অনুষ্ঠান। মঞ্চের কাছেই সব্যসাচীর বাসা, আমার বর্তমান আবাসস্থল।
সকাল আটটা না বাজতেই পুরো রাস্তা অনুরাগীদের দখলে চলে গেছে। সবার হাতে পুষ্পস্তবক, শেফালি গাঁদার মালা। ফুল-বিক্রেতা শিশু কিশোররা হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, যাদের হাতে ফুল দেখতে পাচ্ছে না—তাদের কাছে ছুটে যাচ্ছে, কাছাকাছি তাদের পেয়ে ভালো হয়েছে, যারা আনতে পারে নি, পথে পড়ে নি—তারা বেশ স্বস্তিতে আছে, কবির কাছে যাবে—কিছু একটা অর্ঘ্য দিয়েই না তার ভালোবাসার কথা জানাতে হবে।
এর মধ্যে পাকিস্তান হাই কমিশনার এসে পড়েছে কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। চেয়ার বিছানো অল্প পরিসরের পথ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল সে। দুকামরার ছোট ফ্ল্যাট, পরিপাটি করে আজ সাজানো হয়েছে, অপেক্ষাকৃত বড় কামরাটিতে একটি খাটে বিছানা পাতা আছে কবির জন্য। চারিদিক থেকে অনেকগুলো চেয়ার দেয়া হয়েছে, অতিথিদের বসার জন্য। দেয়াল জুড়ে রঙিন কাগজের আলপনা, জায়গায় জায়গায় তাজা ফুলের স্তবক। আজ এ বাড়িটি বাঙালির তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে।
পাঞ্জাবি আর কালো পাড়ে ধুতি পরে আমি বিছানায় বসে আছি, অন্যদের চোখে সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্তি। আমায় দেখে অপরিচিত জনের বোঝার উপায় নেই—আমি কোনো দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছি। বিশেষ করে আমার দীর্ঘ চোখের চাহনিতে কেউ ধরতে পারত না। আমি যেখানে বসেছি—তার বাম পাশে জানালার উপরে প্রমীলার একটি পোর্ট্রেট রয়েছে। আমি মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি, চেনা চেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে—‘আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন আমি খুঁজে ফিরি আপনায়।’
পাকিস্তানের বাঙালি হাই কমিশনার ফুল দিয়ে তার প্রাণের শ্রদ্ধা জানাল, তারপর একে একে অন্যরা, অল্প ক্ষণে ফুলে ফুলে পুরো ঘর ছেয়ে গেল। ছোট ঘর, ছোট্ট বাড়ি দাঁড়ানোর জায়গা নেই। সিঁড়ির নিচ থেকে ক্রিস্টোফার রোড বিশাল কিউয়ের সৃষ্টি হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, এ যে ভালোবাসা—এখানে জোর করা সাজে না।
প্রথমে কল্যাণী তারপর অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ‘ঝরা ফুল দ’লে কে অতিথি’ এবং ‘ফুলের জলসায় নীরব কেন’ গান দিয়ে ঘরোয়া অনুষ্ঠান শুরু করল। গান শেষে হাই কমিশনার বলল, ‘কবি নজরুল আমাদের জীবনে প্রাণের স্পন্দন। আজ এখানে, এপার-বাংলায় যেমন আমরা তার জন্মোৎসব করছি, তেমনি ওপার বাংলাতেও হচ্ছে তাঁর জন্মদিনের উৎসব। তিনি তো শুধু এখানকার নন, উভয় বাংলারই প্রাণ-পুরুষ।’
তার কথা বলার পরে মানবেন্দ্র গাইল, ‘কত কথা ছিল বলিবার’ ধীরেন বসু গাইল ‘জনম জনম গেল আসা পথ চাহি।’ এদিকে নিচের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন কোলকাতার মেয়র প্রশান্তকুমার বসু। আমায় মঞ্চে নেয়ার চেষ্টা করল, আমার ইচ্ছে হলো না। আমি ইতোমধ্যে বিরক্ত হতে শুরু করেছি, কিছুটা ক্লান্ত। এত মানুষের চাপ আমি এখন সইতে পারি না। মেয়রমশাই নিচের আনুষ্ঠানিকতা সেরে উপরে উঠে এল। আমায় ধুতি, মানপত্র ও পুষ্পস্তবক উপহার দিল। মন্মথ রায় এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, ‘কি আমায় চিনতে পারছ, আমি মন্মথ।’
রবীন্দ্রসদনের ফটোগ্রাফার বিশুনন্দী ছবি তুলছে, আকাশবাণীর তরফদার বাবু রেকর্ড করছে। অভিনেত্রী চন্দ্রবতী, পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার সহধর্মিণী যমুনা বড়ুয়া সোফায় বসে আছে। আমি একাগ্র চিত্তে পদ্মফলের পাতা ছিঁড়ছি। চন্দ্রবতী বলল, ‘কত কালের কথা, তবু মনে হয় সেদিনের কথা। কাজীদার কাছে গান শিখতাম, ওর সুর, ওর কথা—সেদিন কি জানতাম তিনি এত বড় মানুষ।’
‘তিনি কখনো বড় মানুষ হয়ে আসেন নি আমাদের সামনে, আমাদের হয়ে আমাদের সাথে মিশেছেন।’ বলল যমুনা বড়ুয়া।
কাঠিয়া চৌবাচ্চার উপর বসে ভিড় নিরীক্ষণ করছে, দুলাল শেখ উমার কাছাকাছি থাকছে, কখন কোন হুকুম হয়। বিকালে আবার রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠান আছে। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ ও বউমারা যাবে। ইতোমধ্যে বারোটা বেজে গেছে, আমার দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে। ডায়াবেটিস থাকায় কম মিস্টিযুক্ত একটা রসগোল্লা খেয়েছি। কিন্তু এখনো বাইরের ভিড় কমে নি। সবাই কবিকে একবার সচোক্ষে দেখতে চায়। যুবক বৃদ্ধ দলে দলে আসছে। মায়েদের হাত ধরে শিশুরাও আসছে, কেউ ‘লিচুচোর’ কেউ ‘খাঁদু দাদু’ কবিতার কথা বলছে। আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ কাগজ বের হয়েছে, একটির নাম ‘কবিকণ্ঠ’ হকারের হাতে হাতে ঘুরছে, কেউ কেউ কিনছে।
রাত এগারটায় আঙুরবালা গাইল—‘আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়।’
বারাসাত থেকে এক বৃদ্ধ এসেছে, হাতে গাঁদাফুলের মালা, আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, লাইনের পেছনে পড়েছিল। তার পক্ষে আর এ বেলায় আমাকে দেখা হলো না। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিতে বাসার দরজা বন্ধ করা হয়েছে। মাইকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, কবির স্বাস্থ্যেও কথা বিবেচনা করে আপনারা একটিু ধৈর্য ধারণ করবেন। আবার বিকাল তিনটা থেকে আপনারা কবিকে দেখতে পাবেন। কেউ বজবজ থেকে এসেছে, কেউ হুগলি, মেদিনীপুরেরও দুএকজন আছে। দর্শনার্থীদের ভিড়ে আমি মেদিনীপুরের আজহারউদ্দীনকে মনে মনে খুঁজলাম, সে আমায় নিয়ে একটা বই লিখেছে, সুস্থ অবস্থায় ওর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। আজহারের আগে আমার বন্ধু কাজী আবদুল ওদুদ আমার প্রতিভার মূল্যায়ন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিল। তাঁর মূল্যায়নের আবেগহীনতা ও রবীন্দ্র মাপের খাটো হওয়ায় অনেকে তাকে দুষে থাকে, কিন্তু প্রথম যুগে যারা আমায় নিজে কাজ করেছিলেন, তাদের অবদান ছোট করে দেখার উপায় নেই, এত বড় পণ্ডিত তখন কজনই-বা ছিল। বঙ্গীয় মুুসলিম সাহিত্য সমিতির কলেজ স্ট্রিট অফিসে সে আমার আগেই থাকতে শুরু করেছিল। আজ আমি খুব শোকাভিভূত মাত্র কয়েকদিন আগেই আমার এই জ্ঞানী বন্ধু প্রয়াত হয়েছেন।
বিকালের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত দশটা বেজে গেল। অনেকে ফুল শুকিয়ে যাওয়ার ভয়ে ছিল, দূর থেকে যারা এসেছিল তারা ফেরার গাড়ি পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। অনেকে প্রণাম করার সুযোগ পাচ্ছে, অনেককে দ্রুত জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। যুথিকা রায় প্রণাম করল, আমি মাথা চাপড়ে দিলাম, সবাই মজা পেল। আঙুর বালা সোফায় বসে সানি নিনির সঙ্গে গল্প করছে। তার স্মৃতিতে তিরিশ বছর আগের চিৎপুর রোডের বিষ্ণুভবন—গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ড রুম। কাজীদার সুর, কাজীদার কথা—‘তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি।’ বলছে, ‘এখন কাজীদার সামনে গেলেই কষ্ট হয়।’ যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু বলল, ‘তাও উনি এখনো আমাদের মাঝে আছেন, এটিই ভগবানের আশীর্বাদ।’
বিকেলের অনুষ্ঠানে সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। উপরে আমায় দেখতে এসে বলল, ‘কী রে কেমন আছিস?’ আমি ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। কিছু বলতে গিয়েও বললাম না—‘সেদিন পুকুরে ডুবে মারা গেলেই তো ভালো হতো—বাঁচাতে গেলি কেন?’ সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ড. অজিতকুমার ঘোষ। অনেক রাত হয়ে গেছে, তবু দর্শকদের অনুরোধ থামছে না। রাত এগারটায় আঙুরবালা গাইল—‘আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়।’ তার আগে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জপমালা ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী কাজী, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় গাইল। ধীরেন বসু গাইল, ‘নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা’—এক সময় এটি আব্বাসউদ্দীন গাইত। আব্বাস মারা গেছে, অনেক দিন হলো, বছর দশেকের কম নয়; কে. মল্লিকও মারা গেছে একই বছরে—এই দুই গুণী শিল্পী ছাড়া আমার সংগীত প্রতিভার একটি দিগন্ত অন্ধকারে থেকে যেত। সংগীতে ভারতে মুসলমানদের অবদান উজ্জ্বল হলেও আমার হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডের যুগে ছিল বিরল। অনুষ্ঠানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত কিছু বলার সুযোগ পেল, বিশ্বনাথ দে সানি নিনির সঙ্গে দেখভাল করে কাটাল।
শৈলজানন্দ আমাদের শৈশবের স্মৃতিচারণ করল। ‘ছোট বেলার বন্ধুর সামনে দাঁড়ালে আজ চিনতে পর্যন্ত পারে না।’ ও যতিনের কথা বলল, লেডি ডাক্তার অরুণা ঘোষের কথা বলল, বলল সাপুড়ে ইয়াছিনের বউ শিবানীর কথা। বলল, ‘নজরুল নৌশেরা থেকে চিঠি লিখেছে, তুমি যদি থাকতে কত ভালো হতো।’ আমি যেতে পারি নি, নজরুল গিয়েছে, আমি এখনো স্বপ্ন দেখি করাচি, নৌশেরা, আমার সেই দুঃখ কখনো ঘুচার নয়।
অনেক রাত, সবাই যার যার মতো ঘরে ফিরে গেছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফুলের পাপড়ি, ধুলায় মলিন কবিকণ্ঠের ছেঁড়া পাতা, পৌর কর্পোরেশনের আধভাঙা মঞ্চ, দড়ি-দড়া, ক্রিস্টোফার রোডের তোরণ বাকি-রাত একা একা জেগে রইল, কয়েকটি বেওয়ারিশ কুকুর দল বেঁধে ক্রিস্টোফার রোডের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সারারাত ছুটাছুটি করছে, সারাদিনের ক্লান্তিতে যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে; আমার চোখে ঘুম নেই, একদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছি—দেয়ালে প্রমীলার মতো ছবি হয়ে। দুই ছবিতে কথা বলতে বলতে চোখ দুটি ভিজে এল—কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এল—
‘মুসাফির! মোছ রে আঁখিজল ফিরে চল আপনারে নিয়া। আপনি ফুটেছিল ফুল গিয়াছে আপনি ঝরিয়া।’