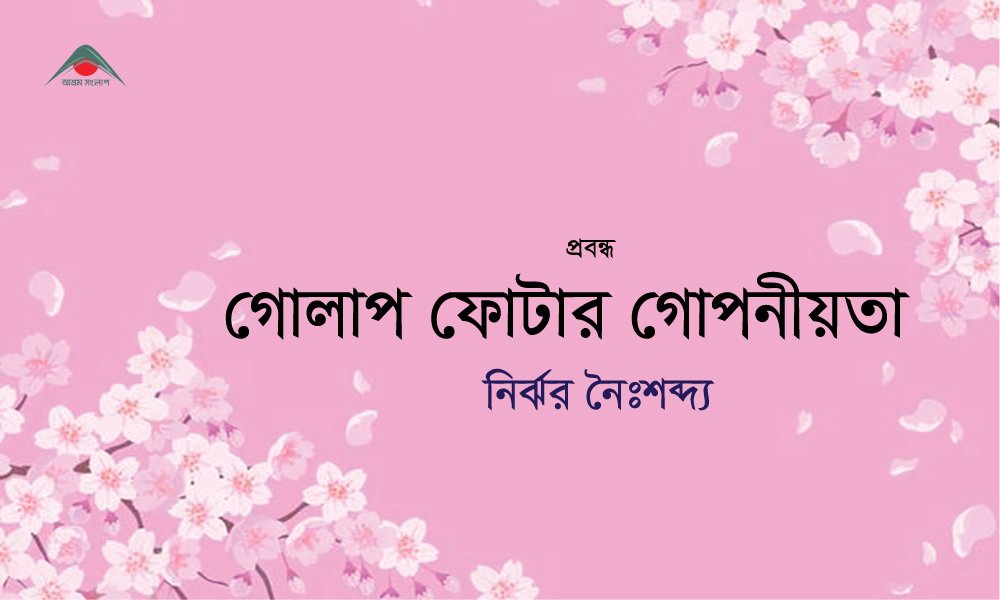প্রাসঙ্গিক কথা : ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হল এবং এ নিয়ে আনন্দ যেমন আছে, তেমন আছে মায়া কান্না। মায়া কান্না মূলত দেখানো হয় জাতীয়তাবাদের কথা বলে। আর সে জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের কালো অধ্যায় রচিত করেছে বহু আগে। অর্থাৎ যাকে জাতীয়তাবাদ বলা হচ্ছে তা সত্যিকার অর্থে হিন্দুত্ববাদ। তবে এ কথাও ইতিহাসে প্রমাণিত জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে এ দেশে শুরু হয়েছে সন্ত্রাসবাদ।১ কেননা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাথে আমাদের জাতীয়তাবোদের অনেক পার্থক্য রয়েছে। আবার জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে মনে করেন, ‘জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ধারার মধ্য দিয়ে পরিচালিত সাম্প্রদায়িকতার অতিরিক্ত কিছু নয়।’২ বাংলাভাগের পক্ষে এ দেশের অর্থাৎ আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ সমর্থন জানিয়েছে এবং এ সিদ্ধান্তে অটল আছে ও থাকবে।
‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রদায়গত আলোচনার উদ্দেশ্য হল, জাতীয় স্বাধীনতার ধারায় মুসলমানের অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা; এ যুক্তিকেই পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই কথা প্রমান করতে যে, মুসলমানেরা কখনই সত্যিকার জাতীয় নাগরিক হতে পারবে না।’৩ জাতীয়তাবাদের এসব আলোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক কেননা, বর্তমানে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদকে বেশ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে সত্যিকারের ইতিহাসকে আড়াল করা হচ্ছে। কেননা, ‘ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার কোনো ভূমিকাই ছিল না’৪ জাতীয়তাবাদীদের।
আমরা বরাবরের মতোই বিশ্বাস করি কলকাতার ভদ্রলোকেরা এ দেশের নিম্নবর্গের হিন্দুদের বিপদগামী করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। তার সাথে ঐতিহাসিকেরাও বেশ রঙ লাগিয়ে ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, ‘তাদেরকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী করে তোলার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যে-প্রয়াস তখন হয়েছিল. . . যেসব মাপকাঠিতে মুসলমানকে কাছে টানার চেষ্টা হয়েছে, তার অনেকগুলি ছিল ভ্রান্ত।’৫
এর আড়ালে আমাদের অবিভক্ত ভারতের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে এবং তাকে বিভক্তের জন্য মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে দায়ী করা হয়। প্রকৃত অর্থে এর কি আদৌ কোনো সত্যতা আছে, না এমন অভিযোগের পিছনে রয়েছে হীন মানসিকতা? তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু দেখার বিষয় কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব এর জন্য দায়ী, আর কোন জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন থেকে নিজেদের বাঁচাতে এবং স্বাধীনতার পথে হাটতে বাধ্য করেছিল কারা। এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে গত শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় শাসন কাঠামোকে এক অদ্ভুত উপায়ে বিন্যস্ত করার প্রতিক্রিয়ায় দৈনিক অমৃত বাজার ২০ আগস্ট, ১৯৩২ সংখ্যায় একটি উপকথা ছেপেছিল, যাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বাংলার ভবিষ্যতের, তা তুলে ধরতে চাই। উপকথাটি এরকম :
এক কৃষকের একটা ভেড়া বাড়ির আঙিনায় রাখা লম্বা মুখওয়ালা ধান ভর্তি একটি মাটির কলসির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু এর পর ভেড়াটি তার মাথা আর বের করতে পারছিল না। এ ঘটনায় পরিবারের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফলে গ্রামের মাতব্বরকে ডেকে পাঠানো হয়. . . মাতব্বর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হয়; ‘সামান্য এই বিষয়ে তোমরা আমার সাহায্য কামনা করেছ? আমি মারা গেলে তোমরা কী করবে? একটা তলোয়ার এনে দাও।’ অতঃপর তলোয়ারের এক আঘাতে ভেড়াটির মাথা তার দেহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন করে দিল। মাতব্বরের বুদ্ধির প্রখরতা লক্ষ্য করে গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু চালাক ধরনের এক যুবক কথার মধ্যে কথা বলল : ‘কিন্তু কলসির মধ্যে ভেড়ার মাথা এখনো রয়ে গেল।’ মাতব্বর লোকটি তার দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : ‘বোকা কোথাকার। এ ঘটনায় তুমি হতবুদ্ধি হতে পারো, কিন্তু আমার বুদ্ধি লোপ পায়নি।’ অতঃপর সে একটুকরো পাথরের আঘাতে কলসিটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। কলসির মধ্যে যে ধান ছিল তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল আর ভেড়ার মাথাটা বেরিয়ে আসল। কৃষক পরিবারের সবাই সঙ্কট থেকে মুক্ত হল। তারা সবাই বুঝতে পারল যে, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য মাতব্বর যদি না আসত তাহলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত. . . ।৬
আমরা জানি ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। যেমন, হামলা-মামলা, হত্যা ও গুম করে রীতিমত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়কে নানাভাবে মুসলামনদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া, শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে রাখা ছিল অন্যতম। তার উপর মিথ্যা অপপ্রচার ছিল একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা। আর অপপ্রচারের কারণেই আমরা নিয়মিতভাবে শোনতে বাধ্য হচ্ছিলাম মুসলামনরা পড়াশোনায় অনাগ্রহী ও বাস্তববাদী না হওয়ায় তারা অনগ্রসর এবং হিন্দু সম্প্রদায় আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পড়াশোনা করায় বেশ অগ্রসর। কিন্তু আমরা জানি মুসলমানরা মধ্যযুগে এ দেশে আসার পর এ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অথচ সেগুলিকে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই না দিয়ে সবাইকে অন্ধকারে রাখার সব ষড়যন্ত্রই হয়েছে। আর তিতুমীরের উত্তরসূরীরা নিজেদের বার বার ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং বিশেষ করে ‘পশ্চিম বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে অবশ্য মুসলমানেরা কুড়ি দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বেশ ভাল অবস্থায় আসে’।৭ আর সে সময়েও স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা সাধারণভাবে সারা বাঙলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে।৮
কলকাতা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী হিসাবে পথ চলা শুরু করে এবং তার সংস্কৃতিও ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত; অথচ প্রকৃত বাংলা ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন, কিন্তু আসামের সে রকম কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়।৯
আমাদের এ বিষযটিও আমলে নিতে হবে যে ‘১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হবার কারণে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা পেয়েছে।’১০ কেননা, এই ভঙ্গের মধ্যদিয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিল ও নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হবার পথ খুঁজে পেয়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলেও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে অস্বীকার করার উপায় নাই। আর একে অস্বীকার করার মানেই হলো স্বাধীন বাংলাদেশেরও বিরোধীতা করা।
২
বঙ্গভঙ্গ : ইতহাসে ১৯০৫ সালকে প্রথম বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪৭ সালকে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল ১৮২৬-১৮৭৪ সালে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাগ করার পরিকল্পনা করা হয়।১১ অতএব স্বাভাবিকভাবে ১৯০৫ সালের ভাগকে দ্বিতীয়বার ভাগ বলতে হবে। তবে আক্ষরিক অর্থে ১৯০৫ সালের পূর্বে বঙ্গভঙ্গ হয়নি কিন্তু ১৮৬৬ সালে (কোনো কোনো মতে ১৮৯৬ সালে প্রথম পরিকল্পনায় আনা হয় বঙ্গভঙ্গের।১২) উড়িষ্যা দূর্ভিক্ষের কারণে ব্রিটিশ শাসকদের মাথায় এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসে।১৩
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বঙ্গভঙ্গ হবার আগে যে প্রস্তাব দেয়া হয় এতে পূর্ববঙ্গের ষোলজন হিন্দু ও মুসলিম জমিদার একত্রিত হয়ে ‘২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আহবান জানান ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জকেও পূর্ববাংলার সাথে সংযুক্ত করতে।’১৪ এটি কি প্রমাণ করে না এ বঙ্গের বঞ্চিত মানুষ শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল?
বঙ্গভঙ্গ না হলে কি হত : হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দিন দিন যে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল এবং হিন্দুদের মধ্যে গায়ে পড়ে ঝগড়া করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল নিয়মিতভাবে। কিন্তু এ দাঙ্গায় মুসলমানরা হয়তো কোনো কোনো এলাকায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উত্তর ভারত যেমন কাশ্মীর অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত হবার পরও ভারতীয় হিন্দুদের হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থাকায় নিয়মিতভাবে অনেক ভয়ানক আক্রমণের শিকার হয়েছিল বিদ্রোহী ও ভারতীয় আইন শৃঙ্খলাবাহিনী দ্বারা।১৫
এ দূরত্বের জন্য বারবার হিন্দুদের দায়ী করা হয়। হিন্দুদের হীন দৃষ্টির কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছিল না। এমন প্রেক্ষাপটে ‘চট্রগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ডব্লিউ. ডি. ওল্ডহাম ১৮৬৯ সালেই বঙ্গীয় সরকারের মূখ্য সচিবের কাছে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব ভারতের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দুদের হুমকিমূলক রাজনৈতিক অবস্থান অনেকাংশে খর্ব হবে।’১৬ এখানে স্পষ্টত বুঝা যায় হিন্দুরা শোষণ করে মুসলামনদের পিছিয়ে রাখত এবং এই শোষণের হাত বাঁচার তাগিদেই মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েছে।
বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের দূরভিসন্ধি : আমাদের বলা হল অবিভক্ত বাংলার আয়তন ও জনসংখ্যা এত বেশি যা একজন গভর্ণর দিয়ে শাসন করা সম্ভব নয়। এখানকার জনসংখ্যা ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার প্রায় সাতগুন।১৭ তাছাড়া পূর্ববাংলা শিক্ষা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর।১৮ তাই একে এগিয়ে নিতে হলে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ আবশ্যক। ইতিহাসে এভাবে যখন লিপিবদ্ধ থাকে তখন আমাদের খুশি হবার কারণ ছাড়া অন্য কিছুই নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য ভিন্ন! কেননা এর পিছনে তাঁদের রাজনৈতিক কুটকৌশল কাজ করছিল।’১৯
আমরা যদি ইতিহাসে চোখ রাখি দেখতে পাই ১৯০৫ সালের পূর্বে বাংলা হিন্দু মুসলামনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু ১৯০৫ সালে বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই শুরু হয় নানামুখী ষড়যন্ত্র। আর সে ষড়যন্ত্রের ফসল হল দাঙ্গা। কেননা, ‘ঔপনিবেশিক শাসনকার্য নির্বিঘ্ন করার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়- হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার স্বতন্ত্র্যকে বিরোধে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।’২০
লর্ড কার্জন-ই মূলত বাংলাকে বিভক্ত করার পরামর্শ দিয়ে ব্রিটিশ রাজদরবারে যে আহবান জানায় তার ফলে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ সালে প্রজ্ঞাপণ জারির মাধ্যমে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়।২১ কিন্তু বেটেনের ‘ভাগ কর এবং শাসন কর’ নীতির কথাকে এড়িয়ে যাই। প্রকৃতপক্ষে এ ‘ভাগ কর এবং শাসন কর’ নীতির কারণেই লর্ড কার্জন এমন চিন্তায় মাথায় আনেন। কেননা সে সময়ে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। আর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মূলত এই বাংলা থেকেই বেশি পরিচালিত হত। পাশাপাশি এ. কে. ফজলুল হক, আবুল হাশিম, মাওলানা আকরাম খাঁ পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের হয়ে যেভাবে অগ্রসর হয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষকে অগ্রসর করছিলেন তা ব্রিটিশদের মাথায় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া ভাইসরয় মনে করেন যে, ‘খেলাফাত আন্দোলনের পর মুলমানদের শান্ত করার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি।’২২
এমতাবস্থায় ‘ভাগ কর এবং শাসন কর’ নীতি অবলম্বন করে স্থায়ী সমস্যা তৈরি ছিল ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য। আর ‘ভাগ কর এবং শাসন কর’ নীতির সূদূর প্রসারী যে বিভেদ তৈরি হবে তা একেবারে স্পষ্ট হয় রোয়েদাদ নামক সম্প্রদায় ভিত্তিক আসন বিন্যাসের মাধ্যমে। লর্ড জেটল্যান্ডের লিখিত পত্রে এমন পরিকল্পনার কথা ওঠে আসে। তার মতে, ‘এই রোয়েদাদ ক্রমাগতভাবে সাম্প্রদায়িক তিক্ততাকে বাড়িয়ে দিবে. . . এবং এই রোয়েদাদ ক্রমাগত আন্দোলনের পথকে সুগম করবে এবং নিশ্চিতভাবে নাশকতামূলক আন্দোলনে প্রভূত শক্তি যোগাবে।’২৩ কিন্তু এতে কলকাতার বাবু তথা ভদ্রলোকেরা কেন ক্ষেপে উঠলেন তাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। মূলত অবিভক্ত বাংলায় কলকাতার ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকের ও ব্রিটিশ আনুগত্যশীল জমিদারদের শাসনে পিষ্ট ছিল পূর্ববাংলা। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের চাকুরি পাবার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হত। এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলা প্রশাসনিকভাবে আলাদা হলে জমিদাররা তাদের জমিদারীতে নিয়ন্ত্রন হারাবে আংশিক এবং মুসলামানরা লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলার মুসলমানরা সরকারী বিভিন্ন কাজে চাকুরী লাভের সুযোগ পাবে এবং তারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার কারণে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে পারবে। অতএব কলকাতার ভদ্রলোকেরা ও জমিদাররা কর্তৃত্ব হারানোর বিরহে দাঙ্গা বাঁধিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলার আহ্বান জানায়।
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় পূর্ববাংলার বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠী এ বিভক্তের বিরুদ্ধে তেমন কোন আন্দোলন বা প্রতিরোধ বা অহসযোগ তৈরি করেনি। কেননা মোঘল শাসন আমলে মুসলমানদের অধীনে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা সম্মানের সাথে বসবাস করার অধিকার পেয়েছিল, সে ইতিহাস তারা ভুলে যায়নি।
আর মুসলামনরা ব্রিটিশ কুটকৌশল ধরতে না পারলেও নিজেদের স্বার্থে এ বিভক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। কেননা, শিক্ষায়, অর্থনৈতিকভাবে ও বাণিজ্যের দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরে তারা বঞ্চণার শিকার ও অনগ্রসর। সুতরাং এ সুযোগে নিজেদের ভাগ্যে পরিবর্তন করা সম্ভব বলে তার একে ধরে রাখার আন্দোলনে নিয়োজিত করেছিল।
কিন্তু ব্রিটিশরা ও কলকাতার ভদ্রলোকেরা এবং জমিদারদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের কারণে স্থায়ী দাঙ্গা দেখা দেয়। তবে ইতিহাসে এ প্রসঙ্গটি বরাবরই মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণা খেয়াল করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ফলে ‘মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই বঙ্গদেশের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখতে পান।’২৪
ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষজন সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছে তাও বিবেচনায় আনা আবশ্যক। ‘ব্রিটিশ প্রশাসকেরা বুঝতে পারে যে মূলত ভারত হল সস্পূর্ণ পৃথক শ্রেণি, জাতি ও সম্প্রদায়ের সমষ্টি- এদের মধ্যে আছে স্বার্থের ভিন্নতা ও বংশগত আবেগ, যার কারণে তারা যুগের পর যুগ ধরে যৌথভাবে কোনো কাজ করতে পারে না বা স্থানীয় পর্যায়ে কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্যে উপনীত হতে পারে না।’২৫
তবে ব্রিটিশ ‘মূলনীতিবাদী’দের ভারত সম্পর্কে ধারণা ছিল, ইনডেনের মতে:
অদ্ভুত ও পরস্পরবিরোধী এক মিশ্র সমাজের প্রতি ভারত আস্থাবান- ঐ সমাজে ভারতীয়দের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জাতি, গ্রাম, ভাষাগত অঞ্চল, ধর্ম ও যৌথ পরিবারের মতো সামাজিক গ্রুপগুলোর জন্য। কারণ, ভারতে ‘ব্যক্তিগত’ বলে কিছু নেই- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে ভারতীয়রা অসৎ কাজ বলে মনে করে।২৬
৩
বাংলা বিভক্তিতে হিন্দু ভদ্রলোকদের আশঙ্কার কারণ : অবিভক্ত ভারতের সাথে একীভূত হয়ে থাকলে নানামূখী ষড়যন্ত্র ও চাপে আমরা চিরদিনের মতোই দাসত্বের শিকলে বন্দি থাকতাম। তবে বঙ্গভঙ্গ আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ শিখিয়েছে এবং এ স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতীয়দের নানা আশঙ্কায় ফেলে দেয়। ফলে তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আর অনেকগুলো আশঙ্কার মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ছিল, পূর্ব বঙ্গকে আলাদা করে দিলে পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের অনেক অঞ্চলও প্রভাবিত হয়ে স্বাতন্ত্র্যবোধে জাগ্রত হতে পারে। ’৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রভাবিত করেছেও কোনো কোনো অঞ্চলকে। যেমন, ভাষা আন্দোলনের সময় ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ভাষার অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেছে। আর এসব বিবেচনায়ও ছিল। তাই পূর্ববঙ্গকে মেনে নিলে মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের উত্থানে প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে অন্য অঞ্চলগুলো আলাদা হতে চাইবে। এই আশঙ্কার কারণেই বিরোধীতা।
একই আশঙ্কা থেকে ভারত ফারাক্কা বাঁধও নির্মাণ করে। জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ফারাক্কা পরিকল্পনায় ষড়যন্ত্রের সব ব্যবস্থা করা ছিল তা আহমদ ছফা এক প্রবন্ধে ইতিহাসভিত্তিক ও ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থের কথা তুলে ধরেন। তাঁর মতে :
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় বাঁধটি নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত নিলেন অনেকে মনে করেন তাতে ভারতের হিন্দি বলয়ের শাসকগোষ্ঠীর একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। বর্তমানে ভারতের (গত শতাব্দীর শেষ দশককে বুঝানো হয়েছে) রাষ্ট্রের জোড়াগুলো কাঁপছে। কাশ্মীরিরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে। পাঞ্জাবি শিখরা বিক্ষুদ্ধ এবং পশ্চিম বাংলা হল ভারতের ফেডারেল কাঠামোর দূর্বলতম অংশ। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে পশ্চিম বাংলা ভিন্ন চিন্তা করতে পারে। সে কথা আগাম চিন্তা করে গঙ্গা নদীর ওপর একচ্ছত্র অধিকার অর্জন করতে চায় ভারত।২৭
বঙ্গভঙ্গের কারণে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চমার্গীয় হিন্দুরা যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল তার পিছনে সর্ব ভারতীয় হিন্দুদের সমর্থনেরও কারণ রয়েছে আর কারণসমূহ কখনো আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় না এবং এমনকি যাতে সেসব বিষয় যাতে দিনের আলোতে না আসে তার চেষ্টাও নিয়মিতভাবে করা হয়েছে এবং হচ্ছে।
পলাশী যুদ্ধের বিজয় ভারত উপমহাদেশে শুধু উপনিবেশ স্থাপনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। এ যুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তি সমূহ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে-সকল উপনিবেশ স্থাপন করেছে তার সঙ্গে পলাশী যুদ্ধের একটা গভীর সংযোগ রয়েছে। বস্তুত প্রাচ্যদেশীয় রাজ্যগুলোতে পশ্চিমা দেশমূহের উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পলাশীর বিজয়কে গণ্য করা যায়।২৮
বাংলাদেশের মানুষ যে আন্দোলন শুরু করেছিল তার দেখাদেখি আসাম এবং দ্রাবিড় অঞ্চলগুলোতেও ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ যখন স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করে, এরপর ভারতের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসনের সংগ্রাম জাগিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভারতের অবহেলিত অঞ্চল এবং নির্যাতত জনগোষ্ঠীর মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়ে ভারত রাষ্ট্রের মূল কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে লড়াই শুরু করেছে এবং সে লড়াই অদ্যাবধি অব্যাহত গতিতে চলছে।২৯
স্বদেশী আন্দোলনের নামে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা ভারতীয় (এখানে মনে রাখতে হবে ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতীয় বলতে আমরা উচ্চমার্গীয় হিন্দুদের বিবেচনায় রাখব) শিল্পকে প্রসারিত করার পথকে আরো নিখুঁত রাখতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসনের বিরোধীতা করেছিল। আর তাদের এই ঐক্যবদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের আড়ালে সব কিছুকে নিজেদের কুক্ষিগত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।৩০
এর মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে যদি সত্যি তাই হত তবে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে কেন বিদেশী পণ্যবর্জনের আহ্বান ছিল? এর মূল কারণ দু’টি। এক, বিদেশী শক্তিকে চাপ দেয়া যাতে তারা অনতিবিলম্বে বিভক্ত বাংলাকে এক করে দেন। দুই, এ সুযোগে নিজেদের পণ্যের বাজারকে আরো সম্প্রসারিত করা। এছাড়াও পণ্যের ঘাটতিতে বাজার উর্ধ্বমুখী হলে পূর্ববাংলার দরিদ্র মানুষেরা অসহনীয় জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে একীভুত হবার তাগিদ অনুভব করবে। তেমনি এক প্রমাণ মেলে Shri Gurunathrao Patak এর সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাতে। এ সভায় বক্তারা বলেন : everyone should vow not to use foreign cloth, except in unavoidable circumstances, in order to encourage Indian artisans, trade in Indian goods and production of indigenous goods.৩১ এর মানে এই নয় আমরা বিদেশী পণ্যকে স্বাগত জানায়েছি। আসলে বিদেশী পণ্য বর্জনে স্বদেশী আন্দোলনকরীরা যদি সত্যিকার অর্থে দেশের ভালোবাসায় করতেন তবে তাকে সমর্থন করা যেত। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ তাদের একক আদিপত্যকে ছিন্ন করে আমরা নতুনভাবে জেগে উঠি তা তারা চায়নি।
বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের সন্দেহের কারণ : বঙ্গভঙ্গের সময় পশ্চিবঙ্গের ভদ্রলোকেরা ভাষার প্রতি দরদ দেখিয়েছে। বাংলাকে ভাগ না করতে ও আসামকে বাংলার সাথে সংযুক্ত না করতে যুক্তিও উপস্থাপন করে। যুক্তিতে বলেন, ‘বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের দু’টি ভূখণ্ডে বিভক্ত করা যৌক্তিক নয়। তাছাড়া আসামের ভাষা যেহেতু বাংলা নয় তাই আসাম পূর্ব বাংলার সাথে যুক্ত হলে বাংলা দ্বারা আসামের ভাষা ও সংস্কৃতি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।’৩২
কিন্তু বাংলাকে পশ্চিম বঙ্গের ভদ্র মানুষেরা কখনো সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রীয় ভাষা করতে চাননি। ‘বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসনামলে প্রকাশিত তার ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা নামক বইয়ে বলেন, ‘ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিত হিন্দি।’৩৩
আমরা এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেলাতেও দেখি যিনি বিশ্বাস করেন ভাষা একটি জাতির পরিচয় হতে পারে না। উল্লেখ্য তাঁর ‘নেশন কী’ প্রবন্ধে তিনি দাবী করেন ‘ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, একথাও ঠিক নয়।’৩৪ অধিকিন্তু তিনি আরো মনে করেন :
‘নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর-একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পরের সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা- যে অখণ্ড উত্তারাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা।’৩৫
রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য যেমন আশা জাগায় তেমনি হতাশও করে। কেননা, এক সাথে থাকার ইচ্ছা সবারই থাকে। কিন্তু একসাথে থাকতে হলে অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া প্রয়োজন। কিন্তু তথাকথিত ভদ্র হিন্দুরা কেবল আধিপত্যবাদী হয়ে দাসত্বের শিকলে বন্দি রেখে মুসলমানদের সাথে থাকতে চেয়েছে। তাই বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানরা আর্শীবাদ হিসাবেই দেখেছে। উল্লেখিত প্রবন্ধের অন্য অংশে তিনি এটিও বলেছেন, ‘এই নেশন-সকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে- এক আইন, এক প্রভু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।’৩৬ আর মোঘল বিজয়ের পর ‘বিজয়ী মুসলমান শক্তিকে এই দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ বিদেশী জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।’৩৭ আর এমন চিন্তা থেকেই বরাবরই মুসলামনদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করেছিল উচ্ছমার্গীয় হিন্দুরা। উল্লেখিত বিষয় বিবেচনায় নিলে বুঝা যায় ষড়যন্ত্র যেখানে বিদ্যমান সেখানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান হাস্যকর।
৪
ঐক্যবদ্ধ ভারতে বাঙালি মুসলমানেরা কী স্বাধীনতা উপভোগে করতে পারতো?: ভারতকে রাষ্ট্র বলা যায় কিনা এ নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। আবার কেউ কেউ ভারত রাষ্ট্রকে সত্যিকারের অর্থে রাষ্ট্র বলা যায়, না বৃহতাকারের কোনো উপনিবেশিক শক্তি বলা যায় তা ভাববার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি ভারতীয় পণ্ডিত শিবনারায়ণ রায়ের মূল্যায়নকে। তাঁর মতে, ‘মারাঠী জাতি আছে, উড়িয়া জাতি আছে, বাঙালী জাতি আছে, গুজরাটি জাতি আছে, তামিল জাতি আছে, কিন্তু ভারতীয় জাতি বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। ভারতীয় জাতিয়তার কনসেপ্টটি উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া।৩৮
একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে বহু জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠী ও ভাষাভাষী মানুষ থাকে। কিন্তু সেটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হতে হলে কিছু শর্ত অবশ্যই মানতে হবে। আর এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা বলেন :
আমার বিশ্বাস, যে কোনো ঐক্য চিন্তার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল পরষ্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা। যে সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বাস এবং আস্থার ভাব স্থায়ী হয় সে কাজগুলোকে হতে হবে শর্তমুক্ত, স্বতস্ফূর্ত এবং পারষ্পরিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বর্তমানে দুই বাঙালার মধ্যে সম্পর্কটা সেরকম অনাবিল সম্পর্ক নয়।৩৯
এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় যে অবিশ্বাস দুই বাংলার মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তার শতভাগ দায়ী পশ্চিম বাংলার ভদ্র হিন্দুরা। কেননা তারা আমাদেরকে সাথে রাখতে চায় কেবল তাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ ও নিজেদের জমিদারিকে টিকিয়ে রাখতে। কেবল এখানে তারা ক্ষান্ত থাকত বলে মনে হয় না। তাই বঙ্গভঙ্গের সময়ও যেমনটি চেয়েছিল রাজ্য হিসাবে পূর্ববঙ্গ দূর্বল থাকুক, যাতে তাঁরা একে বাজারে পরিণত করতে পারেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশকেও দমানোর প্রয়াস চলিয়ে যাচ্ছে। এই বাংলার সংস্কৃতি জরাগ্রস্ত হোক, যাতে তাঁরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যেতে পারেন। আর আগ্রাসন দিন দিন এত ভয়াবহ হতে শুরু করেছে যে তাদের নাটক ছবি দেখে সংসার ভাঙ্গার যে হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যেভাবে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে, তা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতি রাষ্ট্রের জন্য সরাসরি হুমকি। আর আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য এ দেশের ‘গণবিরোধী এবং নষ্ট চরিত্রের লোকদের সম্মান-শিরোপা দিয়ে সীমান্তের এ পাড়ে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে।’৪০ যার একটি নমুনা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে পদ্মভূষণ পুরষ্কারে ভূষিত করা।
বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও আমরা দেখি বর্ণবাদ ও গোত্রকে ভারতের তথাকথিত ভদ্রসমাজ কিভাবে জিইয়ে রেখেছে এবং নিম্ন বর্ণীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানদের দমিয়ে রাখার হীন প্রয়াস চালিয়েছিল। যেমন ১৯২৮ সালে Bengal Tenancy Amendment Act of 1928 নামে একটি বিল পাশ করালে ‘হিন্দু নেতারা বিশেষ করে জমিদারেরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তাদের এই বিরোধিতার কারণ মুসলমানরা কিছু নিশ্চিত মৌলিক অধিকার পেয়েছিল এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে’৪১ তা থেকে বঞ্চিত করা।
বঙ্গভঙ্গের কারণে ভারতীয় রাজনীতির পুরো মানচিত্রই ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। এর ফলে আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গে ভদ্র লোকেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে কংগ্রেস প্রায়ই বাংলার মুসলিমদের অবজ্ঞা করত। কিন্তু মুসলমানরা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমের নিজেদের আত্ম মর্যাদা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৯ সালে ভারতীয় কংগ্রেস হতে মাওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে মুসলামনদের একটি অংশ বেরিয়ে আসে।৪২ এতে বেশ হতাশ হয়ে কংগ্রেস নেতা জে. এন. সেন গুপ্ত বলেন, ‘. . . আজ হতে কংগ্রেস কেবল মুসলমানদের আত্মবিশ্বাসই হারালো না তারা কিছু সাধারণ প্রজাও হারালো।’৪৩ এখানে বেশ লক্ষণীয় মুসলামনদের নিজেদের স্বার্থে প্রজার বাহিরে অন্যকিছু ভাবতে পারেনি। এ বিষয়গুলি বিবেচনায় আনলে বুঝতে অসুবিধা হয় না ধীরে ধীরে মুসলমানরা কেন পৃথক জাতি রাষ্ট্রের দিকে আন্দোলনকে নিয়ে গেল।
আবারো আরেকবার ফিরে তাকাই বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরপরই হিন্দু তথাকথিত সভ্য-তথাকথিত ভদ্রদের প্রতিক্রিয়া। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হল মাঠে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় কাসিমবাজারের জমিদার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেন, ‘নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। হিন্দুরা স্বদেশেই আক্রান্ত হবে। এর সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভীত এবং স্বজাতীয়দের ভবিষ্যতের চিন্তায় মুহ্যমান।’৪৪ নন্দীর এই প্রতিক্রিয়াও সাম্প্রদায়িক ছিল। এভাবে প্রত্যেক হিন্দুই সংঘবদ্ধভাবে মুলমানদের প্রতিহতের মনোভাব নিয়েই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।
কেবল এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও হত। কলকাতার ভদ্রলোকেরা এ দেশের মুসলমানদের নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মতো অস্পৃর্শ মনে করত। এ প্রসঙ্গটি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন দেখছেন এভাবে:
হিন্দুদিগের স্পর্শদোষ বড়ই মারাত্মক। অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত, এমন কি শিক্ষিত হিন্দুও মুসলমানদিগকে স্পর্শ করা অপবিত্রজনক মনে করেন। মুসলমান জাতি যে কিসে অস্পৃশ্য এ কথা আমরা চিন্তার করিয়া উঠিতে পারি না। এরূপ ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত হইবার কারণ- মুসলমানের আচার ব্যবহার, শাস্ত্রবিধির অনভিজ্ঞতা। মুসলমান শাস্ত্রবিধিতে অন্তরশুচি ও বহিঃসুচির সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সে সব অনেক হিন্দুই অনুসন্ধান না করিয়া মুসলমান জাতির প্রতি অকারণ কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে।৪৫
হিন্দুদের এই কালো মনোভাবটি এবনে গোলাম সামাদের লেখাতেও বেশ স্পষ্ট। তার মতে, ‘হিন্দুরা মনে করে যে, মুসলমান হলো যবন, স্লেচ্ছ, অশুচি। তাদের এই ঘৃণাই এই উপমহাদেশের মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছে পৃথক রাষ্ট্র গড়তে।’৪৬ এরপর তিনি বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এম এন রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :
‘মানুষ নিয়েই রাষ্ট্র। মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। কেননা, ভারতের বেশির ভাগ মানুষ এখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেনি। মুসলমানদের তারা এখনো ভাবছে যবন ,স্লেচ্ছ, অশুচি। এই মনোভাব কোনভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার সৃষ্টি করতে পারে না। রায়ের কথা বিশেষভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে বাবরি মসজিদ ভাঙেনি, ভেঙেছে স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ দল কংগ্রেসের শাসনামলে।’৪৭
বঙ্গভঙ্গ রহিত হবার পর কলকাতার ভদ্রলোকেরা আবার পুরোনো চরিত্রে ফিরে গেলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ‘১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যশোহরের মুসলমান ও নমঃশূদ্র বর্গাদারদের উচ্চ শ্রেণির হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করে- অধিকতর ভালো পারিশ্রমিক না পেলে তারা এসব জমিদারদের জমি চাষ করতে অস্বীকার করে।’৪৮ এই আন্দোলনকে কি কোনভাবেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা যায়, না এটি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর সচেতনতা।
এমনকি গ্রামীণ বাঙালার বিভিন্ন আশ্রমে প্রচলিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী খ্যাতনামা গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও বর্ণ প্রথার পক্ষে যুক্তি দেখান যে, ‘বর্ণ প্রথা প্রাচীন পদ্ধতিতে সমাজন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন যে, অস্পৃশ্য ও নীচু শ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করা বর্ণাশ্রম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল না।’৪৯ ‘বরং তা ছিল ঐ পদ্ধতির বিকৃতি এবং মুসলিম আক্রমণের পরই তা হিন্দু মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।’১৩ অথচ মুসলিম সমাজ হিন্দু বর্ণবাদকে অনেকটা প্রশমিত করে আদর্শ স্থাপন করে এবং নির্যাতিত হিন্দুদের মুক্তির কাণ্ডারি হিসাবে ভূমিকা পালন করে। সতীশচন্দ্রের এমন মনোভাব বা মিথ্যা প্রচারণা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদকে উস্কে দেয়। তাছাড়া তার এমন হীন বক্তব্যের বিরুদ্ধে গান্ধীকেও কখনো শোনা যায়নি প্রতিবাদ করতে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।
বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশদের দীর্ঘকালের পরিকল্পনা ছিল যাতে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ভুলে হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা গড়ে তোলে এবং পরস্পর হানাহানিতে নিয়োজিত থাকে। এর মধ্য দিয়ে তারা ভারত শাসন করতে পারবে। এর কুটকৌশল হিসাবে বঙ্গভঙ্গ করে এবং তাদের ফাঁদে হিন্দুরা পা দিয়ে চিরদিনের মতো হিন্দু-মুসলমান বিভাজিত সম্পর্ক তৈরি করল। যদি সত্যি ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উদ্দেশ্য হত তবে বঙ্গভঙ্গ রদের পরও হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের আক্রমণ ও হামলা করেছে তা সত্যি অবিশ্বাস্য। ফলে, দেখি, ‘১৯২৬ সালের কোলকাতা দাঙ্গার উপর লিখিত এবং অসহযোগ, খেলাফাত আন্দোলন ও দাশ চুক্তির ব্যর্থতার স্পষ্টভাবে প্রভাবিত ঐ প্রবন্ধে (শরৎচন্দ্রের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা) সাহসের সাথে ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানরা শুধু পৃথক নয়, মৌলিকভাবে তারা অসমান, আর মিলন হয় সমানে মানে’।৫০
৫
দাঙ্গা ও দাঙ্গার কারণ: বঙ্গভঙ্গকে রহিত করার জন্য ‘দাঙ্গা’ নামক একটি শব্দকে বেশ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেমনি বর্তমান সময়ে বিরোধী মতকে দমাতে ‘জঙ্গি’ নামক অবান্তর কথা বলে জনগণকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে নিয়মিত। দাঙ্গা কি? এ প্রসঙ্গে জন আর ম্যাকলেইন বলেন :
The term ‘Communalism’…means the tendency of people to perceive their interests as identical with those of their religious group, the tendency to re-gard the values and activities of members of the other religious groups as alien or antagonistic, the tendency of religion to determine political affilia-tion, the tendency of group conflict to occur between members of different religious communities.৫১
এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের আগে অবশ্যই দেখা দরকার ১৯০৫ সালের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল। বঙ্গভঙ্গের আগে খুব কমই হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ছিল । অথবা ছিল না বললেই ভালো। এ প্রসঙ্গে এক ইংরেজ দাবী করেন : There were reports of stray incidents regarding cow-slaughter, religious and social festivals, representa-tion on consultative and legislative organisations, education and government em-ployment but they remained only small frictions but never caused any great commu-nal disharmony. এখানে সুস্পষ্ট দেখা যায় যে বিরোধ তা বঙ্গবভঙ্গের পর দেখা দেয় । এখানে খতিয়ে দেখা দরকার কেন এ বিরোধ বঙ্গভঙ্গের পর দেখা দিল এবং কারা এর মূল নায়ক।
বঙ্গভঙ্গের পর বাংলায় দাঙ্গা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, ‘সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল।৫২ আর ১৯০৬ সালের গোড়ার দিকেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে থাকে।’৫৩
ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতাকে মুসলমানদের একক ফসল হিসাবেই দেখানোর প্রয়াস চালিয়েছে বহু সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদ এবং সে চেষ্টা আজও চলছে। বিশেষ করে ‘বাঙালার ক্ষেত্রে সবাই এ ধারণাকে একটা সাধারণ সত্য বলে গ্রহণ করেন যে, বাঙালার মুসলমানেরা সহজভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং তাদের উচ্চ শ্রেণির নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে সহজে সংগঠিত করতে পারে।’৫৪
এসব যুক্তির যথার্থতা থাকুক বা না থাকুক, তা এমন ধারণা প্রদান করে যে, বাঙালায় সাম্প্রদায়িকতা হল মুসলমানদের একটা বিষয়। এর ফলে ঐতিহাসিকেরা এই ধারণা করেন যে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সমান্তরালভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ঘটেনি বা ঘটলেও তা এমন সীমিত ও ছোট গণ্ডির মধ্যে ছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়াসের বিরোধ সৃষ্টিতে তা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।৫৫ ‘এই ধারণার ফলে ভয়ঙ্করভাবে ত্রুটিপূর্ণ সেই ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয় যে, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানেরা সহজভাবে ‘সাম্প্রদায়িক’।”৫৬
হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের পর গরু কোরবানী দেয়া ও মসজিদের সামনে পূঁজা দেয়াকে কেন্দ্র করেই দাঙ্গা শুরু হত। অথচ ইতিহাস বলছে গরু কোরবানী দেয়া নিয়ে অতীতে কারো মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না। হঠাৎ এ ধরনের বিষয় সৃষ্টি কেন হল। ঐতিহাসিক বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ এখানে প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে :
হিন্দু মুসলমানের একতা একটা কঠিন ব্যাপার। হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর কোনও বিবাদ নাই। দুই জাতিই উদার। এতকাল ইহারা পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছি-কই দাঙ্গার কথা তো শুনি নাই। মাঝে যে হয় সে কুচক্রীর কুপরামরর্শ।. . . আর মুসলমান আমলে তো এ সম্বন্ধে দাঙ্গা শুনি নাই।৫৭
আর মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা মনে করেন, ‘গোহত্যার প্রশ্নটি অবশ্য বঙ্গদেশে চরমপন্থী হিন্দুদের প্রতিরোধী মনোভাবের জন্যই বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে।৫৮ কিন্তু প্রাচীনকালে হিন্দুরাও যে গরু জবাই করত তার প্রমাণও মেলে ইতিহাসে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ গোলাম হোসেন বলেন :
হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রধান কারণ- মুসলমানদিগের গো-হত্য প্রথা।. . . আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে গোহত্যা প্রচলিত ছিল। তবে তাহা সাধারণ খাদ্যের মধ্যে গণ্য ছিল কিনা, এ কথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। উহা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের যে অঙ্গ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।৫৯
কিন্তু বর্তমান ইতিহাস বলছে, বাঙালার ভিন্ন ধরনের অনুপম জাতিভেদ কাঠামোর কারণেই মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে ঘটেছে’।৬০ তাছাড়া আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা শুরুতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েনি বরং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচ্চ শ্রেণির হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়েছেন।
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা : এটি সবার জানা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ জোরালো আন্দোলন করেছেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে। কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ তোষণে ব্যস্ত এবং সারা জীবন বলা যায় রাজনীতির বাহিরে ছিলেন, তিনি হঠাৎ করে এমন ভূমিকায় কেন এলেন?
আমরা জানি ‘রাখী বন্ধন’ নামে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আড়ালে শক্তিশালী হিন্দুত্ববাদী ঐক্য গড়ে তোলা ও মুসলমানদের স্বাধীনতার চেতনাকে দুর্বল করার প্রয়াসে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে জাতীয় বেদনার দিন কিন্তু জাতীয়তা বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন? মুসলমানরা কি এ ভঙ্গের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল? যদি না বলে সবার বেদনার দিন বলার মানে কি? তবে কি তিনি পূর্ব বঙ্গের মানুষদের মানুষের পর্যায়ে ভাবতে পারেননি?
রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের সাথে যে বৈরি আচরণ করতেন তাও কারো অজানা নয়। গান্ধীর এ বৈরি আচরণ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় বলেন :
গান্ধী এইভাবে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ ঐক্যে মৌলিক বিভেদ সৃষ্টি করেন এবং শ্রমিক কৃষকের সকল গণসংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সচেতনভাবেই সাম্প্রদায়িক বিরোধীরূপ অস্ত্রটিকে সাম্রাজ্যাবাদের হাতে তুলিয়া দেন।৬১
১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার ঘোষণা এলে রবীন্দ্রনাথ পাল্টা ঘোষণা দিয়ে ‘রাখী বন্ধনে’র আহবান জানান এবং সেদিন একটি শোভাযাত্রা করেন তাঁর নেতৃত্বে তাতে ‘বন্দে মাতেরাম’ ধ্বনিতে গঙ্গা স্নানে শুদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করেন।৬২ ‘বন্দে মাতেরাম’ একটি সাম্প্রদায়িক চেতনার নাম।
মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তি স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেননা, বঙ্গভঙ্গের ফলে রবীন্দ্রনাথের তিনটি বিশাল জমিদারি পূর্ববঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। আর পশ্চিমবঙ্গে থাকা দুটি জমিদারি পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে ছোট জমিদারির চেয়েও ছোট তাই জমিদারির স্বার্থে তাঁকে আন্দোলনের বিকল্প ছিল না। যদি তা না হত কেন বঙ্গভঙ্গের আগে এ বঙ্গের মানুষজন অবহেলায় থাকার পরও একবারের জন্যও তাদের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আহবান জানালেন না?
অর্থনৈতিক দূরাবস্থা: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববাংলা মুসলিম অধ্যুষিত হবার কারণে অর্থনৈতিকভাবে বেশ দূরাবস্থার মধ্যে ছিল। এর মধ্যে চট্রগ্রামের অবস্থা ছিল আরো করুণ। যদিও চট্রগ্রামে সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করে একে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কাজে লাগানো সম্ভব ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। এবং বাংলাভাগ হবার পর চট্রগ্রামের সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ও সে অঞ্চলের অর্থনেতিক দূরাবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কলকাতা সমুদ্র বন্দর চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সংযোগ রেল থেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত করে।৬৩ মুসলমানরা যে নিজেদের কারণে পিছিয়ে পড়েনি এবং তাদের প্রতি পদে কিভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে তাও ঐতিহাসিকভাবে আজ প্রমাণিত। আমরা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব শিক্ষিত হবার পরও কিভাবে মুসলমানরা চাকুরি পেতে ব্যর্থ হয়। আর চাকুরি দাতা ছিল ব্রিটিশরা।
১৮৫৮-১৮৮১ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকোত্তর ১৭২০ জনের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ৩৮জন। ১৮৭১ সালে বঙ্গদেশে ২১১১টি গেজেটেড পদে কর্মরতদের মধ্যে মাত্র ৯২জন ছিলেন মুসলমান। এই পদগুলোতে ৬৮১জন ছিলেন হিন্দু বাকিরা ইউরোপীয়। এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গের ১৪টি জেলায় জনসংখ্যার ৬৫.৮৫ শতাংশ এবং স্বাক্ষর জনগোষ্ঠীর ৪১.১৩ শতাংশ ছিলেন মুসলমান। কিন্তু সরকারী চাকুরি মাত্র ১৫.৫ শতাংশ ছিল মুসলমানদের দখলে।৬৪
উল্লেখিত পরিসংখ্যানে এটি স্পষ্ট শিক্ষিত হবার পরও চাকুরি মিলত না মুসলমানদের। যেমনটি হয়েছিল ড. এনামুল হকের বেলায়। তিনি ব্রিটিশ সরকারের আমলে পিএইচডি করার পরও দীর্ঘ কাল চাকুরি না পেয়ে মক্তবে চাকুরি করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি সেখানে কর্মরত হন। আর এসব ক্ষেত্রে কেবল ব্রিটিশ শাসকারাই দায়ী নয়, এ দেশের হিন্দু জমিদাররাও দায়ী। কেননা ‘পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক এবং অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু জমিদারদের অধীনে প্রজা।’৬৫
৬
উপসংহার : আধুনিক বাংলা হিন্দু ভদ্রলোকের সৃষ্টি। তারা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে হাত পেতে করুণা ভিক্ষা করে যাতে ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দুতে বাংলাকে বসাতে পারে। তাই ‘এই দৃষ্টিকোণ থেকে নব জাগরণই হল শুধু ভদ্রলোকের সংস্কৃতির প্রতীক নয়, সেই সঙ্গে একটি হিন্দু বাঙলার, যেখানে মুসলমানের ঠাঁই নাই।’৬৬ আমরা এ প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছি বঙ্গভঙ্গের কারনে হিন্দুদের মায়া কান্না পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদের আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদকে উস্কে দেয়া এবং বাংলা থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন বা আত্মপরিচয়হীন করে রাখা। ফলে বঙ্গভঙ্গের সময় যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, সে প্রতিক্রিয়া নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করল বঙ্গভঙ্গ রদের পর। এমনি এক অভাবনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল ‘১৯৩২ সালে যখন এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মুসলমানেরা নতুন আইনে সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে যাচ্ছে’৬৭ তখন। ১৯৩২ সালে ‘দি বেঙ্গল হিন্দু মেনিফেস্টো’তে স্পষ্টভাবে বলা হয় :
রাজনৈতিক যোগ্যতাকে কোনো জাতির বৃহত্তর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, আর রাজনৈতিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের. . . সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সক্ষম না হওয়ার আশংকা সত্যিকারেভাবে তাদের রাজনৈতিক অযোগ্যতা স্বীকার করে নেওয়ার শামিল, আর বর্তমান রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্ব করার দাবি করাটা অযৌক্তিক ও হাস্যকর।৬৮
এভাবেই ভদ্র লোকের আড়ালে বঙ্গকে বিভাজনের মধ্যে নিয়ে গেছেন কেউ কেউ। এই বিভাজনের প্রকৃত ইতিহাস অনুচ্চারিত থাকলে আজকে বিভাজনের যে রাজনীতি শুরু হয়েছে তা থেকে যেমন মুক্তি পাবার উপায় থাকবে না তেমনি নিজেদের অজানা ইতিহাসের কারণে নিজেরা আত্মঘাতী পথে হাঁটব চিরদিন। তাই ইতিহাসকে জানতে হলে ঐতিহাসিকের মানসিকতা ও ঘটনা আবিষ্কারের উৎস সম্পর্কে পূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।
তথ্যসূত্র:
১. আখতার হামিদ খান, ‘বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম সমাজ’, দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ অক্টোবর, ২০১৪, পৃ.৮
২. জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, কনস্ট্রাকশনস্ অব কমিউনালিজম, পৃ.২৩৫, উদ্বৃতি জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.২০০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩-২৫৪,
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪
৫. আনিসুজ্জামান, মুখবন্ধ, গোলাম মুস্তফা, বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল, সন্দেশ, ঢাকা, ২০০৫
৬. দৈনিক অমৃত বাজার, ২০ আগস্ট, ১৯৩২, উদ্ধৃতি জয়া চ্যাটার্জী, বাঙালা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.২৮
৭. এপেনডিক্স জি, রেজুলিউশন রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক বোর্ড ইন বেঙ্গল ডিউরিং দি ইয়ার ১৯২৩-২৪ আনটিল ১৯৩১-৩২, কোলকাতা, ১৯২৪-৩২, উদ্ধৃতি জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.২৮
৮. জয়া চ্যাটার্জী, বাঙালা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.২৮
৯. David Ludden ; ‘Spatial Inequity and National Territory: Remembering 1905 in Bengal and Asian’; Modern Asian Studies; Cambridge University Press; 2011, p.15
১০. Ibid, p.8
১১. David Ludden ; Ibid, p.5-6
১২. আখতার হামিদ খান প্রাগুক্ত, পৃ.৮
১৩. গোলাম মোস্তফা; বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল; সন্দেশ; ঢাকা; ২০০৫; পৃ.১৩
১৪. David Ludden; p.20
১৫. David Ludden ; Ibid, p.6
১৬. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ.১৩
১৭. David Ludden; Ibid,page-6
১৮. জওহরলাল নেহেরু, দি ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া (১৮৪৬), নিউ দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ.২৯৭
১৯. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, ভূমিকা
২০. জয়া চ্যাটার্জী; প্রাগুক্ত, পৃ.২৪
২১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬
২২. মি. এন.এন সরকারের স্মারকপত্র, জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমসেএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১(এইচ)/এ (জয়া২৬)
২৩. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ.৩০
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩
২৫. রোনাল্ড ইনডেন, ‘ওরিয়ান্টালিস্ট কনস্ট্রাকশনস্ অব ইন্ডিয়া’, মর্ডান এশিয়ান স্টাডিজ, খণ্ড ২০, ১৯৮৬. পৃ.৪০৩
২৬. আহমদ ছফা, ‘ফারাক্কা ষড়যন্ত্রের নানান মাত্রা’ নির্বচিত প্রবন্ধ; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ.৩২৬
২৭. আহমদ ছফা, ‘পলাশীর যুদ্ধের একটি দূরবর্তী প্রতিতুলনা’; প্রগুক্ত, পৃ.২৬৪
২৮. প্রগুক্ত, পৃ.২৬৬
২৯. Dr. T.V. Adivesh; ‘Promotion of Indigenous Industries And The Effect of Economic Swadeshi Bombay-Karnataka (1905-1911)’; International Interdisciplinary Research Journal, Volume-II, Issue-II, Mar-Apr 2012, p.190, www.oiirj.org
৩০. Ibid, p.191
৩১. David Ludden ; Ibid,p.18
৩২. এবনে গোলাম সামাদ; ‘ইতিহাসবিদ এ এফ সালাউদ্দীন আহমদ’; দৈনিক নয়াদিগন্ত; ১ নভেম্বর, ২০১৪; পৃ.৬
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘নেশন কী’, প্রবন্ধ সমগ্র, রবিশংকর মৈত্রী সঙ্কলন, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ.৮৪
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫
৩৬. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ.৩১
৩৭. আহমদ ছফা, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৯-২৭০
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭০
৩৯. জয়া চ্যাটার্জী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১*
৪০. Sayed Umar Hayet; Muslim Political ascendancy in Bengal: A Cast Study of the Roles Played by the Bebgal Provincial Muslim Ligue and the Krishak Praja Party(1906-41);Pakistan Jounal History and Culture. Vol. XXVIII. No.2(2007). P.112
৪১. Ibid, p.113
৪২. আবুল মনসুর আহমদ; আমার দেখা রাজনীতি পঞ্চাশ বছর; সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড; ঢাকা; ১৯৮৮; পৃ.৪৮-৪৯
৪৩. এ. কে. এম নাজির আহমদ, ‘উপমহাদেশের অতীত রাজনীতির খণ্ড চিত্র’, নির্মাণ, সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যা, http://www.nirmanmagazine.com/
৪৪. মোহাম্মদ গোলাম হাসেন; ‘হিন্দু মুসরমানদের আচার ব্যবহার ও দেশপ্রেম’; বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান; ১৩১৭(বঙ্গাব্দ); পৃ.১৮৮
৪৫. এবনে গোলাম সামাদ; প্রাগুক্ত, পৃ.৬
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৬
৪৭. তনিকা সরকার, বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪, পৃ:৩৯-৪০
৪৮. জয়া চ্যাটার্জী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১
৪৯. সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ভারতে সাম্যবদ, কোলকাতা , ১৯৩০, উদ্বৃতি, জয়া চ্যাটার্জি পৃ.৪১
৫০. ক্যাথারিন এইচ. প্রিয়র, ‘দি ব্রিটিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব হিন্দুইজম ই নর্থ ইন্ডিয়া, ১৭৮০-১৯০০’, ইউনিভার্সিটি অব ক্যাম্ব্রিজ, পিএইচডি ডিসারটেশন, ১৯৯০, জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.১৯৫
৫১. John R Mclane, Partition of Bengal 1905: A Political analysis.
৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ‘হিন্দু মুসলমান’; কালান্তর ; কলকাতা; ১৯৬২; পৃ.৩৩১
৫৩. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩
৫৪. জে. ইেচ. ব্রুমফিল্ড, এলিট কনফ্লিক্ট ইন পলুরাল সোসাইটি, পৃ. ৩১৭, জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.১৭৭
৫৫. শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্্র ইন বেঙ্গল, পৃ.২২৭, জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.১৭৮
৫৬. ফ্রান্সিস রবিনসন, ‘নেশন ফরমেশন: দি ব্রাস থিসিস এ্যান্ড মুসলিম সেপারিটজম’, জার্নাল অব কমপ্যারেটিভ এ্যান্ড কমনওয়েলথ পলিটিক্্র, খন্ড, ১৫.৩, নভেম্বও ১৯৭৭, পৃ.২১৫-২৩৪, জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.১৭৮
৫৭. বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; স্বরাজ ও খলিফত; ন্যাশানাল লাইব্রেরি ক্যালকাটা; ১৯২১; পৃ.১৯-২০
৫৮. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ.৪০
৫৯. মোহাম্মদ গোলাম হাসেন; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮০
৬০. পার্থ চ্যাটার্জী, কাস্ট, পলিটিক্স এ্যান্ড দি রাজ, বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৩৭, কোলকাতা, ১৯৯০, পৃ.১৮
৬১. সুপ্রকাশ রায়; গান্ধীবাদের স্বরূপ; কলকাতা ১৯৯০; পৃ.৬৫
৬২. আখতার হামিদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৮
৬৩. David Ludden ; Ibid,p.19
৬৪. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪
৬৫. মোহাম্মদ গোলাম হাসেন; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩
৬৬. জয়া চ্যাটার্জী; প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫-২০৬
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ:২০৬
৬৮. দি বেঙ্গল হিন্দু মেনিফেস্টো, ২৭ শে এপ্রিল ১৯৩২, (পুণঃপ্রকাশ) এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত) ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্ট্রার, ১ম খণ্ড, জানুয়ারি-জুন ১৯৩২, পৃ.৩২৩, উদ্বৃতি জয়া চ্যাটার্জী, পৃ.২০৭

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। লেখক, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।