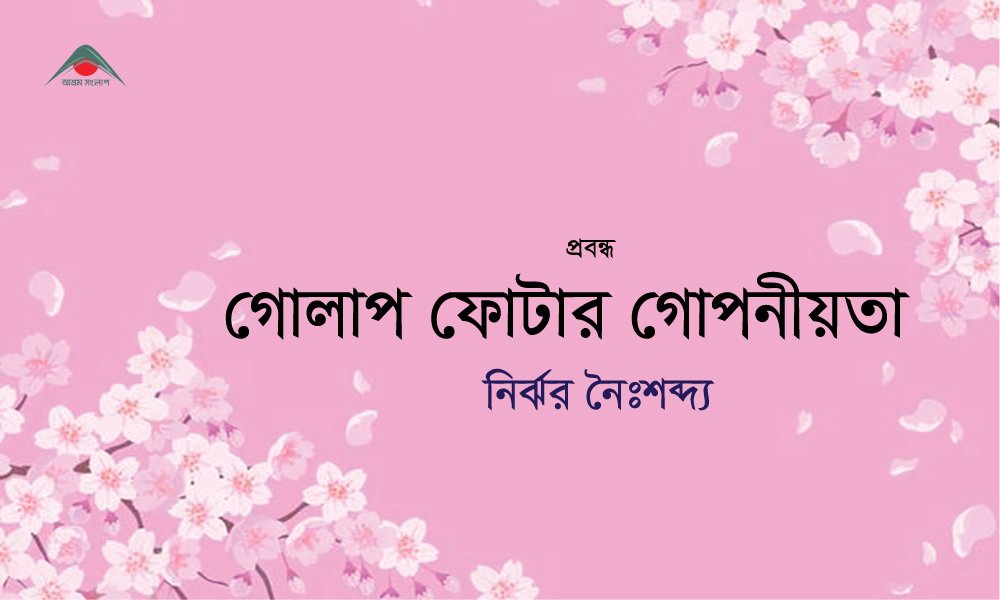মৃত্যু নিয়ে ভাবার আগেই মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। যদি ধরে নেয়া হয় মানুষ বিবর্তনের ফল, তাহলে কোটি কোটি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার আজকের রূপ পরিগ্রহ। নিজের নশ্বর দেহের মধ্যেই বারংবার পরিবর্তন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত মৃত্যুর শরীরে পরিণত হচ্ছে। জন্ম থেকেই মানুষের সকল কাজ পরিচালিত হচ্ছে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার জন্য। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে সে খুঁজে নিচ্ছে মায়ের দুগ্ধ। জন্ম যেমন এক অজানা উৎস থেকে পৃথিবী নামক গ্রহে আগমন করেছে, মৃত্যুও তেমন অন্ধকারের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। মৃত্যুই জীবনের বিকাশমানতাকে নিশ্চিত করেছে, যেন এক অদৃশ্য সারমেয় পৃথিবীর জীবনের গড্ডলিকা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে।
মৃত্যু না থাকলে মানুষের শিল্প সৌন্দর্য সাহিত্য দর্শন সমাধি ইমারত—কোনো কিছুরই দরকার হতো না।
মুরগি আগে না ডিম আগে—এ প্রশ্ন যেমন এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তেমন এটিও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, মৃত্যু আগে না জীবন আগে? মৃত্যু থেকেই জীবনের উন্মেষ, আবার মৃত্যুতেই জীবন বিলীন। পৃথিবীর জীবন প্রকাশের আগে সব মৃত ছিল, আবার জীবন থেকে সে মৃততে রূপান্তরিত হচ্ছে। মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোনো অর্থ থাকে না। মৃত্যু হলো সকল সৃজনশীলতার উৎস—জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। মৃত্যু না থাকলে মানুষের শিল্প সৌন্দর্য সাহিত্য দর্শন সমাধি ইমারত—কোনো কিছুরই দরকার হতো না। আবার এই মৃত্যুই তার পৃথিবীর জীবনের সব কিছু নিরর্থ করে দিয়ে যাবে। বাংলা আধুনিক কবিদের গোদা জীবনানন্দ দাশের কথায়—‘মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেছে নদীটির পারে।’
মৃত্যু যতই ভয়ংকর হোক মানুষ মৃত্যুর রোমান্টিক ভাবনাও কম ভালোবাসে না। তার প্রমাণও জীবনানন্দ দাশ, যার প্রায় সব কবিতা মৃত্যুময় জীবনের গান—‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’ ‘রূপসী বাংলা’—সব মৃত্যূত্তর জীবনের গান। যেখানে জীবন এসেছে মহাকালের ইশারালোক থেকে—ইতিহাসের মানুষ তার প্রধান প্রতিপাদ্য। কীটসের মতো বলতে হয়—‘এই দুঃখের গানই মানুষের মধুরতম উচ্চারণ।’ মৃত্যু থেকে জীবন কোথায় পৃথক, জীবন থেকে মৃত্যু কোথায় আলাদা—এই বিচার সহজ নয়। আবারও জীবনানন্দ দাশে আশ্রয় নিতে হয়—‘এ-রকম অনেক জন্ম-মৃত্যু দেখে গেলাম আমরা/ কিন্তু তবু আমরা অনেকবার মরে গিয়েছি—তবুও মরিনি/ আমরা আজো বেঁচে রয়েছি—তবু বেঁচে নেই।’ কোনো কিছু নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। যখন আমরা থাকি না, তখনো থাকি। এক অজানা লোক থেকে প্রাণের যে ধারা পৃথিবীতে শুরু হয়েছে আমরা দৃশ্যপটে না থাকলেও আমাদের মধ্য দিয়ে সেই ধারা চলতেই থাকে।
কেবল বাংলা সাহিত্য নয়—পৃথিবীর সব সাহিত্যই একটি মৃত্যুর গল্প। পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য গিলগামেশ থেকে শুরু করে বাংলার মধুসূদন পর্যন্ত একটি মৃত্যুর গল্প নানা ভঙ্গিতে নির্মাণ করেছেন। রাজা গিলগামেশের বন্ধু মহাপরাক্রমশালী এনকিদু একদিন প্রকৃতির ইচ্ছায় অসহায়ের মতো মারা গেলেন। গিলগামেশ মৃত্যুভয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেন, অমৃতের সন্ধানে তার শুরু হলো অভিযান। দেবতারা তাকে বলল, কোনোভাবেই তা হওয়ার নয়—মানুষ কখনো অমরত্বের সন্ধান পায় নি। দেবতারা যখন মানুষ সৃষ্টি করেন তখন তারা নিজেদের কাছে রেখে দেন জীবন ও পরমায়ু। জীবনে মৃত্যু হলো অবধারিত, কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। কিন্তু গিলগামেশ হাল ছাড়ার নয়। দুঃসাধ্য সব অভিযান চালিয়ে ব্যর্থতা ও সফলতার মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। দেবতারা খুশি হয়ে তাকে দিলেন অমৃত বর। বললেন, এ হলো তোমার কঠোর অধ্যবসায়ের ফল। মনোবল হারাও নি বলে মৃত্যু তোমার কাছে তুচ্ছ হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের মতো জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—আলাদা কোনো অর্থ নেই। তাই স্বর্গে যেতে তার বাহন লাগে নি।
আমি ভাবি, গিলগামেশের মতো একটি পরিণত উপাখ্যান কিভাবে পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য হতে পারে! হয়তো আরো অনেক কাহিনি মহাকাব্য লিখিত হয়ে থাকবে, কিন্তু আমরা কেবল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই বলতে পারি। প্রায় একই সময়ের সুমেরু অঞ্চলের আদাপা, তেলেপিনুস ও সিনুহের কাহিনিও কম রোমাঞ্চকর নয়—মৃত্যুজয়ের।
এই মৃত্যুকে আরেকজন ফাঁকি দিতে পেরেছিল, সে হলো গ্রিক পুরাণের করেন্থীয় রাজা সিসিফাস। আর এর জন্য তাকে দিতে হয়েছে মোটা মাশুল। মৃত্যুর দেবতা থানাটোস তার জান-কবজের জন্য গেলে সে তাকে মেরে শিকলে বন্দি করে রাখে। যে দুবছর থানাটোস বন্দি ছিল সেই দুই বছর পৃথিবীতে মৃত্যু ছিল না। মৃত্যু না থাকায় হাহাকার তৈরি হয়েছিল। বৃদ্ধ অসুস্থ, শয্যাশায়ী মানুষগুলো যাদের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুর দেবতা না থাকায় তারা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করছিল। এমনকি যুদ্ধ-আহতরা, দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন—কেউই মরতে পারছিল না। পৃথিবীতে মৃত্যু না থাকা যে এক ভয়াবহ অভিশাপ—এই দুই বছর মানুষ টের পেয়েছিল। এক বার নয়, দুই বার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছিল সিসিফাস। সেই অপরাধে তাকে দেয়া হয়েছিল কঠোর শাস্তি। আজও পাহাড়ে পাথর তুলছে সিসিফাস, পর্বতশীর্ষ স্পর্শের আগেই পাতালে পড়ে যাচ্ছে, একটু থামলেই নেমে আসছে দেবতাদের কঠোর চাবুক।
মিথ অফ সিসিফাস নিয়ে আলবেয়ার কামু এক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, মূলত অস্তিত্বের নিরর্থকতা উদ্ভ্রান্ততা প্রমাণ তার এই প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য। জীবন ও মৃত্যুর নিরর্থক অর্থ খুঁজে বেড়ানো। তাঁর বিখ্যাত আউটসাইডার উপন্যাসেও মৃত্যু ও মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পদ্ধতি প্রধান বিষয় করা হয়েছে। অপরাধ ও শাস্তি নিয়ে দস্তয়ভস্কির বৃহদায়তনের বই ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট-এর চেয়ে এই স্বল্পায়তনের বইটির গুরুত্ব কম নয়। দুটি উপন্যাসের বিষয় মৃত্যু। আউটসাইডারের নায়ক যখন বলেন—‘মানব-মানবীরা এমন এক পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করেছে যার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে আমার কাছে চিরদিনের জন্য।’ তখন পাঠক অস্তিত্বের এক সংকটের মুখোমুখী হয়। গ্রিক পুরাণে থানাটোস একাই মৃত্যুর দেবতা নয়, তাকে পরিচালনা করার জন্য রয়েছে পারসেফোন, তার স্ত্রী হেডাস। একইভাবে মায়া সভ্যতায় আজটেকদের মৃত্যুর দেবতা হলো মিকটল্যানটেকাটলি, সেও পাতালের রাজা। এই দেবতাকে খুশি করার জন্য আজটেকরা তার মন্দিরে জীবন্ত নরবলি দিত বলে মনে করা হয়। মানুষকে বলি দিয়ে হলেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। এসব যমদূত স্বাধীন নন। মৃত্যুর ফেরেশতার মতো আজ্ঞাবাহী।
একিলিস হেক্টরের পিতা বৃদ্ধ রাজাকে তুলে ধরে বললেন, ‘আমাদের দুঃখ আমাদের হৃদয়ের ভেতরে নীরবে থাকুক।’
মহাকাব্যের সব ঘটনার মধ্যেই রয়েছে কষ্টসাধ্য এক অভিযান, যুদ্ধ ও মৃত্যু, পরিশেষে মধুর সমাপন। অডিসিউসের অভিযান, ঈনিসের অভিযান—মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জীবনের পথে যাত্রা; কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুকে কে উপেক্ষা করতে পারে! পথে পথে যুদ্ধ, সমৃদ্ধ নগরপতন। অগণিত নারী-শিশুর কান্না, দাস ও যৌনদাসী হিসাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে হস্তান্তর। মহাপরাক্রমশালী বীররা একে অপরকে হত্যা করে নিজেদের বাহুর নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে—পৃথিবীর পথে ‘নিহত ভ্রাতার ভাই’। ট্রয়যুদ্ধে বীর একিলিস যখন প্যাট্রোক্লাসের হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে বীর হেক্টরকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন তার মা থেটিস কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ‘বাছাধন হেক্টর মারা গেলে তুমিও বেঁচে থাকবে না। হেক্টর মারা গেলে তুমিও মারা যাবে—এই হলো ভবিতব্য।’ যত অপরাজেয় বীরই হোক, নিহতের সঙ্গে হত্যাকারীর ভাগ্যও থাকে বাঁধা—সময় কাউকে ক্ষমা করে না। হেক্টরকে হত্যা করে একিলিস যখন রথে বেঁধে তার মৃতদেহ শিবিরে নিয়ে আসলেন তখন হেক্টরের বৃদ্ধ পিতা ট্রয় নগরীর রাজা প্রিয়াম পুত্রের মৃতদেহ ভিক্ষার জন্য হন্তা একিলিসের পা জড়িয়ে ধরলেন, হাতে চুমু খেলেন।
একিলিস : কে আপনি?
প্রিয়াম : আমি সেই হতভাগ্য, পৃথিবীতে কাউকে এর আগে এত কষ্ট সইতে হই নি। আমি সেই ব্যক্তির হাতেই চুমু খেয়েছি, যে আমার পুত্রকে হত্যা করেছে।
একিলিস : প্রিয়াম! আপনি কিভাবে এখানে এলেন?
প্রিয়াম : আমার ধারণা, আমি গ্রিকদের চেয়ে আমার দেশের পথঘাট বেশি চিনি।
একিলিস : আপনি সাহসী মানুষ। আমি তো চোখের পলকে আপনার মাথা কেটে ফেলতে পারতাম।
প্রিয়াম : তুমি কি মনে করো মৃত্যু ভয়ে আমি কি এখন ভীত? আমি চোখের সামানে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে মরে যেতে দেখেছি, তুমি তার মৃতদেহ রথের চাকায় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসেছ। তার মৃতদেহ আমায় ফেরত দাও। যথাযথ শেষকৃত্য তার প্রাপ্য, তুমিও সেটা জানো। তাকে ফেরত দাও।
একিলিস : সে আমার তুতো ভাইকে হত্যা করেছে।
প্রিয়াম : সে তো ভেবেছিল সেটি তুমিই। কত চাচাত ভাইকে তুমি হত্যা করেছ? কত পুত্র, কত পিতা, কত ভাই এবং কত স্বামীকে তুমি হত্যা করেছ? বলো, মহাবীর একিলিস তুমি কত মানুষকে হত্যা করেছ?
একিলিস হেক্টরের পিতা বৃদ্ধ রাজাকে তুলে ধরে বললেন, ‘আমাদের দুঃখ আমাদের হৃদয়ের ভেতরে নীরবে থাকুক।’ একিলিস হেক্টরের শব-সৎকার ও শোক প্রকাশের জন্য প্রিয়ামকে নয় দিন সময় দিয়েছিলেন। মাইকেলও মেঘনাদের জন্য সাত দিন বরাদ্দ রেখেছিলেন। ঝুঁকি নিতে চান নি, পাছে নিয়মভ্রষ্ট হয়!
যুদ্ধ সব কিছু শেষ করে দেয়, জীবিতকে মৃতে রূপান্তরিত করে। ট্রয় নগরী ধ্বংসের পরে রাজা প্রায়ামের স্ত্রী বীর হেক্টরের মা রানি হ্যেকুবা, হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকিকে অন্য সব বন্দির মতো জাহাজে ক্রীতদাসী হিসাবে নেয়া হয়েছে। হ্যেকুবা কেঁদে কেঁদে বলছেন—‘পৃথিবীতে আর কী দুঃখ আছে—যা আমাকে সইতে হয় নি। দেশ গেছে, সন্তান এবং স্বামীকেও হারিয়েছি। আমার সব গৌরব ভূলণ্ঠিত হয়েছে।’
এই মৃত্যু কেবল সবসময় প্রকৃতির নিজস্ব খেলায় সংঘটিত হয় নি, মানুষ নিজেও তার স্বগোত্রীয়দের মৃত্যুপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, ক্ষমতার লড়াই, লোভ, আধিপত্য-বিস্তার এই অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। মানুষ মানুষকে হত্যা না করার স্বাভাবিক সমবেদনা জেগে উঠলে, দেশ গোত্র ও ধর্মের পবিত্রতার দোহাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরু-পাণ্ডবের মহারণে অর্জুন যখন জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে ধনু চালাতে অস্বীকার করছেন তখন সময়ের দোহাই দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছেন। বলছেন ‘তুমি হত্যা করার কে, সময় তো সবাইকে হত্যা করে রেখেছে, তুমি যাদের দেখছ তারা সবাই মৃত মানুষ, তুমি নিমিত্ত মাত্র।’ রবীন্দ্রনাথ যদিও এটাকে হত্যাকারীর ছলনা হিসাবে দেখেছেন। ঠিক একইভাবে মিথ্যার দ্বারা হতোদ্যম করে নিজগুরু দ্রোণাচার্যের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন তার শিষ্যগণ। যিনি একদিন এই ধনুকৃতিতে পাণ্ডবের যশ প্রতিষ্ঠার জন্য নিষাদপুত্রের আঙুল কেটে নিয়েছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ সেই একই দাওয়াই দিয়েছিলেন : ‘মৃত্যু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তুমি কেবল একজন মৃত মানুষেরই মাথা কেটে নিচ্ছ। যত তাড়াতাড়ি কাটা যাবে ততই তাঁর মুক্তি।’
যুদ্ধে কৌরবদের সমূলে ধ্বংস করে বহুকষ্টে যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গিয়ে পৌঁছালেন, দেখলেন দুরাচার দুর্যোধন দুঃশাসন আগেই সেখানে বসে আছে। যুধিষ্ঠিরের রাগ আর তখন ধরে রাখা যায় নি—তাহলে এত যুদ্ধ সংগ্রাম করে লাভ কী হলো! তাই গীতায় জীবন ও মৃত্যুর আলাদা কোনো মানে নেই। মারো কাটো এই দুনিয়ায় কিছুই এসে যায় না, তাই ফলের প্রত্যাশা করো না, কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ হও!
একজনকে মারলে খুনি, শতজনকে মারলে নায়ক।
আরবীয় ধর্মেও ইহুদি-মুসলিম প্রতিপক্ষের মাথা কেটে নেয়ার জন্য করেছে লড়াই। যুদ্ধে মানুষহত্যাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে, যারা মারবে এবং মরবে উভয় মহাপ্রভুর খাতিরের লোক। অবশ্য যেসব ধর্মে মৃত্যুর অনুমোদন দেয়া হয় নি—তারাও ধর্মের নামে কম করে নি। কেউ যিশুর পবিত্র ক্রুশ ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কেউ মানুষহত্যার মধ্যে দেখেছে বুদ্ধের পুনরুত্থান। প্রভুর রাজ্য রক্ষার দায় ক্ষুদ্র মানুষ তার আরো ক্ষুদ্ধ স্কন্ধে তুলে নিতে চেয়েছে। প্রভুর রাজ্যে মৃত্যু একটি নৈমিত্তিক ঘটনা।
যুদ্ধের জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে, পবিত্রতা দান করতে অনেক পশুর জীবন দিতে হয়েছে বলি। নাম হয়েছে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, কোরবানি, বলি সেক্রিফাইস। জীবনকে নিরাপদ করতে জীবনহানির উৎসব রয়েছে ভুবনে ভুবনে। অনেক গুণীজনই বলেন, মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী মৃত্যু নিয়ে ভাবে না। তারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন! যার জীবন আছে তার মৃত্যুভাবনা আছে। তবু মৃত্যু এক গভীর ভয়, অসহ যন্ত্রণা, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে একা চলা নশ্বর পৃথিবীতে যেসব পরিচিত জন তার আনন্দ ও বেদনার কারণ ছিল, তারা যদিও একই পথের যাত্রী, তবু কেউ কারো সঙ্গে নেই। এমনকি গণহত্যা, গণকবরের বাসিন্দা, গণ-আত্মহত্যাকারীরাও মৃত্যুর একই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যায় না। প্রত্যেকের জন্য আসা ও যাওয়ার পথ আলাদা। আগমনের রাস্তাটি মানুষ টের পেলেও গমনের রাস্তা যার যার। যিশুকে ক্রুশকাঠে তার পিতাও ত্যাগ করে যান। পুত্রের আর্তনাদ ‘প্রভু আমায় একা ফেলে যেয়ো না।’ জানি না চিতায় সতী স্বামীর সাথে স্বর্গে যেতে পারে কি না!
তাই বলে ধর্ম মানুষহত্যার একমাত্র অনুমোদনকারী নয়। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই মানুষের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা, বৃহত্তরের শান্তিরক্ষার নামে ক্ষুদ্রতমের জীবন নেয়া তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। এসব হত্যাকাণ্ডের অনেকটাই ঘটে থাকে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতালিপ্সায়। আধুনিক সভ্যতার দাবিদার বিশ শতকের ক্ষমতালোভী স্বৈরাচারী শাসকরা যত মানুষ হত্যা করেছে, পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের সবকালের সম্মিলিত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি নয়। মধ্যযুগের অনেক সম্রাট কেবল হত্যা করেই ক্ষান্ত হতেন না, তাদের শবযাত্রাতেও গমন করতে হতো হাজার হাজার জীবিত দাসদাসী, সৈন্য ও আমাত্যদের। আজ যে পিরামিড আমরা দেখতে যাই, তার অভ্যন্তরে শুয়ে আছে রাজা ও তার শবানুগমনকারীরা। চেঙ্গিসখানের শবযাত্রায় যারা শরিক ছিল, যারা দেখেছিল, যারা তদারক করেছিল—তাদের সবার জীবনকেই তার সঙ্গী করা হয়েছিল। সব হত্যাকারীদের এক সংলাপ, ‘আমি যেখানে যাই সেখানে ঘাস গজায় না।’ হ্যামলেটও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে না পেরে অধীর হয়ে বলেছিলেন, ‘ঘাস গজাতে গজাতেই ঘোড়া মারা যাবে।’
মহাবীর আলেকজান্ডার মৃত্যুর সময় দুহাত খোলা বিছিয়ে রেখেছিলেন। এই পৃথিবী মৃত্যুকে সবার জন্য সমান করে দিয়েছে। পৃথিবী থেকে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে না। ভ্রাতৃ ও জ্ঞাতি-হত্যাকারীদের পরিণামে ভয় পেতেও দেখা গেছে। অশোক শত ভাই এবং পাঁচ শত স্ত্রীকে হত্যা করে মনোযন্ত্রণায় ছিলেন। পরবর্তী জীবনে অহিংস বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও প্রচার করে পাপ-ক্ষালনের চেষ্টা করেছিলেন। আওরঙ্গজেব মৃত্যুর আগে পুত্রের কাছে পত্র লিখে দোষ স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন—‘আমি যে পাপ করেছি না জানি পরকালে তার জন্য কত শাস্তি ভোগ করতে হয়।’ যদিও ‘অনেক যুগ চলে গেছে? ম’রে গেছে অনেক নৃপতি।’ তবু ‘কোন এক সম্রাটের সাথে/ মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে;/ যুদ্ধ-জয়ী-বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—পাশাপাশি—/ জিতিয়া রয়েছে আজ তাহাদের খুলির অট্টহাসি!’
কিন্তু এই মৃত্যু কোনো সরল বিষয় নয়। মৃতের যদিও সব খাতা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তবু জীবিতরা প্রায়ই মৃতদের নিয়ে রাজনীতি করে থাকে। বিশেষ করে রাজনৈতিক হত্যা ও গণহত্যার পরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলতে পারে সেই ধারা। এইসব ক্ষেত্রে হত্যার প্রাসঙ্গিকতা ও সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এখানে সংখ্যা এক পবিত্র বিষয়। চার্লি চ্যাপলিন মঁসিয়ে ভের্দুর জবানিতে বলছেন—‘একজনকে মারলে খুনি, শতজনকে মারলে নায়ক।’
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছিল। এই সংখ্যাটির কম বা বেশি কোনো ইহুদি আজ আর মেনে নিতে চাইবে না। কারণ আউশভিটসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড তাদের আজকের পরিচয় নিশ্চিত করেছে এবং আজকের ইহুদি রাষ্ট্রের কোনো অত্যাচার হতে পারে না তাদের উপর অত্যাচারের সমান। এমনকি তাদের বর্তমান অত্যাচারকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এই বুলিই যথেষ্ট—‘আমাদের উপর যে অন্যায় হয়েছে তার মর্ম আমরা জানি।’ বিশ শতকে মানুষের কল্যাণের নামে মাওজেদং ও স্টালিনের হত্যাকাণ্ড অতীতের সকল সংখ্যা অতিক্রম করলেও তাদের অনুসারীরা এটি মানতে রাজি নয়। ইয়াহিয়ার হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। হত্যাকাণ্ডের নিন্দা-জ্ঞাপনের চেয়ে সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক বেশি চলে। আবার সঠিক সংখ্যাটি তলিয়ে দেখতেও অনীহা। পাশাপাশি ওসমানিয়া তুরস্ক আর্মেনিয়ার উপরে গণহত্যা করেছে কিনা, বা কতটা করেছে—তা কেবল রাজনৈতিক মীমাংসার ব্যাপার। আর্মেনিয়া ছাড়াও তুরস্ককে যারা চাপে রাখতে চায় তাদের জন্য এই স্বীকারোক্তি জরুরি যে বর্তমান রাষ্ট্রটি অতীতে মানবজাতির উপরে এমন জঘন্যতম অপরাধ চাপিয়ে দিয়েছিল—যা বংশপরম্পরায় ক্ষমার অযোগ্য। যদিও ‘মৃতরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনো।’ যদিও ‘এশিরিয়া ধুলো আজ—ব্যাবিলন ছাই হয়ে আছে।’
ইংরেজ কোম্পানির অপশাসনে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলার তিন কোটি লোকের এক কোটি লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিল।
সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে মৃত্যুর পরিধি অনেক ব্যাপক। কবি যখন বলেন—‘ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?/ ওই ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।’ তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মৃত্যু মানব-অস্তিত্বের মধ্যে একটি ভয়ের সঞ্চার করে। এই ভয় তার মৃত্যু-চেতনার অংশ, জীবন-চেতনারও। একদিন সে থাকবে না—এর চেয়ে নিরাশার কথা আর কী হতে পারে! রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’ তখন এই অনিবার্য শূন্যতার ভয় মানবসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। জীবন উদ্যাপন ও মৃত্যুচিন্তা একই সঙ্গে চলতে থাকে। তাই প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে মৃত্যুচিন্তা উপেক্ষা করা মিথ্যাকে আশ্রয় করার নামান্তর। বরং মানবসত্তা যখন মৃত্যুকে চূড়ান্ত বিকাশ হিসাবে ধারণ করতে পারবে তখন তার জীবন সুষমা-পল্লবিত হয়ে উঠবে।
রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন দীর্ঘ মৃত্যুর মিছিল। নিজের পাঁচ সন্তানের তিন সন্তানই তার জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিল। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ। পুত্র ছিলেন নিঃসন্তান। বলা চলে একমাত্র দৌহিত্র—তারও মৃত্যু হয়েছিল বাইশ বছর বয়সে, জার্মানিতে কবির জীবদ্দশায়। চৌদ্দ ভাই-বোনের তেরো জনের মৃত্যুশোক তাকে সইতে হয়েছিল। শৈশবে মাতৃবিয়োগ, বিয়ের পরে প্রিয়তম বউদির আত্মহত্যা, বিয়ের দিনে ভগ্নিপতির পরলোক প্রাপ্তি—যেন এক মৃত্যু মিছিলে নেতৃত্ব দিতেই আধুনিককালে এক মহাকবির জন্ম। তিনিও যেন এক বেদব্যাস—নিজ বংশের ধ্বংসের কাহিনি লেখাই যেন তার ভবিতব্য। জীবনের শুরুতে কবি ভানুসিংহ ঠাকুরে ভর করে গেয়েছিলেন, ‘মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান।’ বুঝেছিলেন কানু বিনে গীত নাই।
নজরুলের চার পুত্রের তিনজনই মারা যায় তার জীবদ্দশায়। স্ত্রী-বিয়োগও হয়েছিল কবি বেঁচে থাকতে। বঙ্কিম যৌবনের প্রান্তে প্রথম স্ত্রী মোহিনীকে হারান, কন্যা উৎপলকুমারীকে মদ্যপ স্বামীর ষড়যন্ত্রে মৃত্যুবরণ করতে হয়—বাংলা সাহিত্যের তাবড় বড় লেখক খ্যাতি ও ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মানুষকেও দেখে নি মৃত্যু অসীম ক্ষমায়। এসব দেখে রবীন্দ্রনাথকে বলতেই হয়—‘মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোনো মানে নেই। আর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে না দেখলে অমৃতের সন্ধান মেলে না। এই জীবনমরণের খেলা দিয়েই জগৎ সত্য হয়ে উঠেছে।’
অনেক মহৎ সাহিত্যও নায়কের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিণতি টানছে, কিংবা কোনো মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখে কাহিনি এগিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে ট্র্যাজেডি নাটকের মূলত পরিণতি নায়কের শারীরিক অবসান। আগেই বলেছি, প্রাচীন—এমনকি আধুনিকালেও মৃত্যুই সাহিত্যের প্রধান অনুষঙ্গ। বাংলা কথাসাহিত্যের কিছু মৃত্যু আমরা এড়াতে পারি না। একটি মাত্র উদাহরণ যথেষ্ট হতে পারে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রতিষ্ঠা অবিতর্কিত। প্রথম উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন, একটি অজ্ঞাত মৃতের মাজারে লালসালুর আবরণে, মানুষের মনে মৃত্যুভয় জাগিয়ে দিয়ে। আরেক মৃত্যু জামিলা তার এই অন্ধকারের বেসাতি হুমকির সম্মুখীন করেছিল। দ্বিতীয় উপন্যাসে মাস্টার আরেফ আলীর মনোজগৎ ও কর্মপন্থা বন্দি হয়ে পড়েছিল একটি দেখে ফেলা হত্যাকাণ্ডে। আর তৃতীয় উপন্যাসেও মুহম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যা প্রধান অনুষঙ্গ। একটি মৃত্যুময় জগতের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের সক্রিয় সত্তার স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ওয়ালীউল্লাহ্’র গুরু আলবেয়ার কামু, জাঁ পল সাঁত্র—তারাও মৃত্যু নিয়ে কারবার করেছিলেন। অস্তিত্ব আসলে মৃত্যুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অস্তিত্বের সংকটমোচন মানেই মৃত্যুকে প্রলম্বিত করা। অবশ্য মৃত্যু নিয়ে সংকট আধুনিক দর্শনাক্রান্ত মানুষের যতটা প্রকট—কৃষিনির্ভর মানুষের ততটা নয়। জীবন ও মৃত্যুর উৎসকে তারা আলাদা করে দেখেন না। পল হ্যারিসনের অভিজ্ঞতা—‘নাইজেরিয়ার এক কৃষকপুত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অস্তিত্ববাদ পড়াতেন। ছুটিতে বাড়িতে গেলে তার বাবা জানতে চাইল—সেখানে কী পড়ানো হয়, তখন সে অস্তিত্বের অর্থহীনতা ও অ্যাবসার্ডিটির কথা বলল। ছাত্রটির পিতা স্যান্ডেলের ঘায়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলল, ‘এই সব নিয়ে ভাবার জন্য আমি তোকে সর্বস্বান্ত হয়ে খরচ জোগাচ্ছি না।’
মৃত্যুর চূড়ান্ত পরিণতি এক হলেও মৃত্যুর পথে পৌঁছানোর রাস্তা ভিন্ন। মৃত্যু নিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তের পদ্ধতিও আলাদা। স্থালকাল যত দূরবর্তী, মৃত্যু নিয়ে মৃত্যুর প্রতি প্রতিক্রিয়া তত নৈর্ব্যক্তিক। হিরোশিমা নাগাসাকির নরককুণ্ডে মানুষের শরীর মোমের মতো গলে পড়লেও আমাদের ততটা লাগে না, যতটা লাগে পাড়ায় জ্বরে কেউ মারা গেলে। তাছাড়া মৃত্যুটি কখন হচ্ছে সেটির উপরেও নির্ভর করে আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরন। স্বাভাবিক সময়ে কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে যে ধরনের প্রগাঢ় বেদনা প্রকাশ করা সম্ভব, মহামারি ও যুদ্ধাবস্থায় মারা গেলে তা সম্ভব নয়। যেমন বর্তমান মহামারিকালে মানুষের প্রত্যাশা থাকে—আজকের চেয়ে আগামীকালের সংখ্যাটি যেন কম হয়। যুদ্ধ ও মহামারিতে মানুষ কেবলই সংখ্যা। আলবেয়ার কামুর দ্য প্লেগ, জ্যাক লন্ডনের স্কার্লেট প্লেগ, হোসে সারামাগোর দ্য ব্লাইন্ডনেসসহ মহামারি নিয়ে লিখিত সব উপন্যাস তার প্রমাণ। দৃশ্যের বাইরেও মানবসৃষ্ট অদৃশ্য মহামারি ও গণহত্যার আলাদা রূপ রয়েছে। ড্রাগ কোম্পানিগুলোর অনেকে জেনেও মুনাফার জন্য দীর্ঘদিন বাজারে এমন সব ওষুধ সরবরাহ রাখে, সেই সব নীরব ঘাতক কেড়ে নেয় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। দুর্ভিক্ষের কারণেও গণমৃত্যু হয়ে থাকে। ইংরেজ কোম্পানির অপশাসনে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলার তিন কোটি লোকের এক কোটি লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিল। তাতে কোম্পানির খাজনা আদায় বেধে থাকে নি। মৃতদের কর আদায় করেছিল জীবিতদের নিকট হতে। এটিই হলো ইতিহাসের কুখ্যাত নাজাই কর।
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবী, মাধুরীলতা তৎকালীন সমাজের যৌতুকের বলি হয়েছিলেন।
মৃত্যু যেভাবেই হোক সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়েছে সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্যে। সাহিত্যের প্রসঙ্গ মৃত্যু হলেও পাঠকের বিষয় থাকে কতটুকু তা রসযোগ্য করে পরিবেশন করা গেছে। লেখকের কল্পনাশক্তি, গল্প বলার কৌশল, চরিত্রের বিকাশ ও সংবেদনশীলতা প্রধান হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজি সাহিত্যে মৃত্যু নিয়ে ভূরি-ভূরি বই লেখা হয়েছে। এমনকি হ্যারি পটারের মতো জনপ্রিয় বইয়ের বিষয়বস্তু মৃত্যু। কেন্টাবারি টেলস, মাদার অব ক্যাথার্ডাল, দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানসিন মেরিনার, হ্যামলেট, জুলিয়াস সিজার, ম্যাকবেথ—সবখানে মৃত্যুর জয়-জয়াকার। অ্যাডগার অ্যালান পো’র অধিকাংশ লেখা মৃত্যু নিয়ে। সম্প্রতি লেখা এ ধরনের উপন্যাসে সমাজ-গবেষণা, রাজনীতি ও জীববিদ্যা-গবেষণার প্রভাব দেখা যায়। মৃত্যুকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায়ও তুলে ধরা হচ্ছে, ডেথ অব অ্যা সেলসম্যান, ডিকেন্সের দ্য মিস্ট্রিস অব এডউইড ড্রুম, কাডিস ফর অ্যা চাইল্ড নট বর্ন—এ ধারার উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসেও মৃত্যুর অনুষঙ্গ কম নেই।
পথের পাঁচালীর দুর্গার মৃত্যু মাইলফলক হয়ে আছে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মৃত্যু সর্বদা একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে এসেছে। মহাভারতের মতো অতি বড় বীর, অনিবার্য যার প্রয়োজন সেও অবলীলায় ঝরে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্গা ও অপুর বেড়ে ওঠা, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দুর্গা ধীরে ধীরে পরিণতি পায়। আকস্মিক দুর্গা দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেলে কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসে। মৃত্যুকে বিভূতিভূষণ তার উপন্যাসে এক প্রতীকী মাত্রায় তুলে ধরেছেন,—‘দুর্গা আর চাহিল না। আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূর পারে কোনো পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা অজানা ডাক আসিয়া পৌঁছাইছে।’
দুর্গার মৃত্যুর অবব্যহিত পরে ‘নতুন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানা অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্য মনস্ক হইয়া পড়ে।’ পাঠক চোখে অশ্রু না এনে পারে না।
ইছামতী উপন্যাসে অত্যাচারী নীলচাষি শিপটন সাহেবের মৃত্যুদৃশ্যও আমাদের নাড়া দেয়। সুদূর ইংল্যান্ডের কোনো এক গ্রাম থেকে আসা। মৃত্যুকালে রক্ষিতা গয়া মেম আর রাম কানাই কবিরাজ মুচি বাগদিরা ছাড়া তেমন কেউ তার পাশে ছিল না। যখন সাহেবের কথা বন্ধ, শ্বাসকষ্ট—দেওয়ান হরকারী বলল, এ কষ্ট আর দেখা যায় না। মৃত্যুর চূড়ান্তপর্বে কষ্ট হয় কি না—মানুষের জানা সম্ভব নয়। বিভূতিভূষণ লিখলেন—
শিপটন সাহেবের কষ্ট হয় নি। কেউ জানত না সে তখন বহুদূর স্বদেশের ওয়েস্টমোরল্যান্ডের অ্যান্ডসি গ্রামের ওপরকার পার্বত্যপথ রাইনোজ পাস দিয়ে ওক আর এলম গাছের ছায়ায় ছায়ায় তার দশ বছর বয়সের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলেছিল খরগোশ শিকার করতে, কখনো বা পার্বত্য রদ এল্টার-ওয়াটারের বিশাল বুকে নৌকায় চড়ে বেড়াচ্ছিল, সঙ্গে ছিল তাদের গ্রেট ডেন কুকুরটা…
হয়তো মৃত্যুর আগে মানুষের অবচেতনে তার শৈশবের স্মৃতিই বেশি ভেসে ওঠে।
আসলে ‘মৃত্যুকে কে চিনিতে পারে, গরীয়সী মৃত্যু-মাতাকে? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মতো জীবনের পথে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে, কখনো বৃদ্ধের কাছে..।’
মানুষ নিজের মধ্যেও অনেকবার মরে যায়, তার দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। শারীরিক অস্তিত্ব বিলয়ের জন্য যদি দুঃখবোধের উদয় হয়। কিন্তু কোন সে শরীর, মৃত্যুর সময় আমরা কোন শরীরের কথা বলি। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, এমনকি বার্ধক্যেও মানুষ এক রূপ থেকে অন্য রূপে যায়।
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবী, মাধুরীলতা তৎকালীন সমাজের যৌতুকের বলি হয়েছিলেন। কবির নাম, ঐশ্বর্য, বড় ঘর—কোনোটাই তার মেয়েদের রক্ষা করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের মুক্তি ঘটেছিল। যেভাবে তার গল্পের চরিত্র হৈমন্তী, নিরুপমার করুণ পরিণতি ঘটেছিল। চন্দরা, বিন্দু, রাসমনীর ছেলেসহ অসংখ্য মৃত্যু তার ছোটগল্পে ছড়িয়ে রয়েছে। ‘ছুটি’ গল্পের কিশোর ফটিকের মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পাঠকের হৃদয়ে পাথরের মতো চেপে আছে। একটি গ্রামের কিশোর শহরে মামার বাড়িতে পড়াশোনার জন্য এসেছিল। শহরে তার মন টেকে নি, বাড়ি যাওয়ার জন্য মন অস্থির, মামা-মামিও তাকে বুঝতে চায় নি। অবহেলা অভিমানে সে জ্বর বাধিয়ে বসে, সেই জ্বরই তার কাল হলো। তার সেই হৃদয়-কাঁপানো সংলাপ—‘মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।’
রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যু একটা আলাদা চেতনা হিসাবে ধরা দিয়েছে। ছোটগল্পে মৃত্যুর নানা প্রতীকী ব্যবহার যেমন আছে তেমন কবিতার বিশালভুবন তাঁর মৃত্যু দিয়ে গড়া। মৃত্যুভীতি থেকে মুক্তি পেতেই হয়তো কবিগুরু, হয়তো জীবনানন্দ দাশও সাহিত্যে শ্রমের নিরলস তাজমহল নির্মাণ করে চলেছিলেন। ‘মরণকে মোর দোসর করে/ রেখে গেছ আমার ঘরে,/ আমি তারে বরণ ক’রে/ রাখব পরান-ময়।’ মরণ এই পার্থিব জগৎ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করতেন। তাঁর কথায়—‘জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরচিয় পেতে হবে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দি করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।’
সব ঘরেই মৃত্যু আছে, মৃত্যু ছাড়া প্রাণ নেই। একদিন এক বৃদ্ধ মা তার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে বুদ্ধের কাছে মাতম করে বললেন, ‘হে মহাস্থবির আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা দিন। বুদ্ধ বললেন, যাও, একটি বিল্বপত্র নিয়ে এসো—সেই বাড়ি থেকে, যে বাড়িতে কেউ মারা যায় নি।’
সক্রেটিস মনে করতেন মৃত্যুই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।
মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে ভয় পাওয়া বা দুঃখিত হবার অন্যতম কারণ হতে পারে , ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে কী ঘটবে সে আর জানতে পারবে না। সে দেখতে পারবে না নতুন পৃথিবীর নতুন আবিষ্কার, জানতে পারবে না তার পরিবারের কার ভবিষ্যৎ কেমন হবে। ব্যাপারটা আসলেই দুঃখজনক। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় : মনে করা মৃত্যুর পরে অনেক ভালো ভালো ব্যাপার ঘটবে তা যেমন সত্য; মৃত্যুর আগেও অনেক ভালো কিছু ঘটেছে—সেটাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বাহাত্তর বছর বয়সে সক্রেটিস তার মৃত্যুশয্যায় জ্ঞানচর্চা করে কাটিয়েছিলেন। ভোলেন নি অ্যাপোলের মন্দিরে একটি মোরগ দেয়ার কথা। সক্রেটিস মনে করতেন মৃত্যুই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। মৃত্যু ভালো না জীবন ভালো আমরা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারি না।
মৃত্যু বেঁচে থাকার একটি উপায়—মওলানা জালালউদ্দীন রুমির একটি গল্প দিয়ে শেষ করি। গল্পটি ‘পঞ্চতন্ত্রে’ও থাকতে পারে। এক আরবীয় বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কাফেলা প্রস্তুতির আগে তার প্রিয়জনের মনোবাসনা জানতে চাইলেন; এমনকি শেষ পর্যন্ত তার খাঁচায় বন্দি তোতাপাখিটিকেও জিজ্ঞাসা করলেন, সুদূর ভারত থেকে তার জন্য কিছু আনতে হবে কি-না। পাখি বলল, সওদাগর ভারতবর্ষের আকাশে তুমি অসংখ্য মুক্ত তোতাপাখি উড়তে দেখবে; পারো যদি তাদের কাছে জেনে এসো আমার মুক্তির উপায় কী।
বণিক সওদা শেষে ফেরার পথে একঝাঁক উড়ন্ত তোতাপাখি দেখে বলল, হে মুক্ত বিহঙ্গগণ, তোমাদের গোত্রের একটি পাখি আরবের এক সওদাগরের খাঁচায় বন্দি হয়ে আছে; সে তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তার মুক্তির উপায়। এই সংবাদটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে দলের সবচেয়ে প্রবীণ পাখিটি শোকাহত হয়ে পাখা-ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে মাটিতে পড়ে মরে গেল। ফিরে এসে এমন একটি হৃদয়বিদারক খবর সে তার পোষা পাখিকে জানাতে চাইল না; তবু নাছোড় পাখিটির অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারল না, সকল কাহিনি সবিস্তারে জানাল। পাখিটি এই ঘটনা শোনামাত্র শোকে ইহলীলা সাঙ্গ করল। শোকাহত বণিক পাখিটিকে মৃত ভেবে খাঁচার বাইরে ফেলে দিল। অমনি মৃত পাখিটি ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে বলল, সওদাগর, আসলে আমি মারা যাই নি, মরার ভান করে ছিলাম। আমার জ্ঞাতিরা তোমার মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছে, আসলে মুক্তি পেতে চাইলে জীবনে মৃতের মতো থাকতে হবে। এই হলো জীবন-মৃত্যুর গল্প।
জীবনানন্দ দাশের মতো আমরা বলতে পারি—‘কোথায় রয়েছে মৃত্যু? কোনদিকে? খুঁজি আমি তারে।’