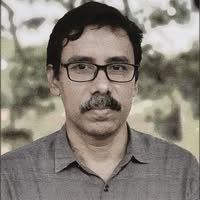শিল্পচর্চার সাথে সমালোচনার প্রসঙ্গটিও পিঠাপিঠি। শিল্পের বিভিন্ন শাখার যে চর্চা আমরা চারপাশে লক্ষ্য করি তার সমালোচনা যেমন থাকে তেমনি থাকে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য-মতামতও। তা আদৌ শিল্প কিনা এমন সংশয়ও কানে বাজে। এসব মতামত বোদ্ধা থেকে সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছ থেকেও আসে। যারা এমন মন্তব্য পোষণ করেন তাদের শিল্প সম্পর্কে নিশ্চয় কোনো পূর্ব ধারণা বা নিজস্ব উপলব্ধি রয়েছে বলা যায়। উপলব্ধির ভিন্নতা ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্যের অবতারনা করে বৈকি! প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, শিল্প বিচারের মাপকাঠিটা কী? এর কোনো সাধারণ সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ রয়েছে কিনা? এ প্রশ্নের প্রতিউত্তরে যেসব ধারণা আমরা পাব তার মাঝেও রয়েছে হাজার বেমিল। তাই বিভ্রান্তি বাড়া ছাড়া কম হবার নয়। এসবের প্রমাণ কিংবা উক্তির অবতারণা না করে বরং শিল্পসৃষ্টির মূলে প্রবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা যাক।
শিল্প যেহেতু মানুষের সৃজনশীল ক্রিয়া তাই এর অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মের দাস্যবৃত্তি করা শিল্পসৃষ্টি অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না। যারা সৃজনের উদ্দেশ্য ও কাঠামোবাদীতাকে বিরোধিতা করে নিজস্ব অভিব্যক্তিকে করণকৌশলের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শককে আগ্রহী করে তুলতে পারে তারাই হয়ে উঠে আদরনীয় এবং বরণীয়। এর সাথে শিল্প জনপ্রিয়তা ও অজনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ চলে আসে। অনেকেই জনপ্রিয়তাকে বলেন সস্তা (প্রকৃতার্থে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমর্থন) আর সংখ্যালঘু নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষিত বা এলিট অংশের সমর্থনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। বিতর্ক হতে পারে জনপ্রিয়তা কেন নয়? কিংবা শিল্প শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক গৌষ্ঠবাদের সেবা করবে কেন? এ উভয়বিধ বাস্তবতা আমাদের দেশে জাজ্বল্যমান।
শিল্পী বা শিল্প বিচারের দু’টি পক্ষ রয়েছে একটি দর্শক বা শ্রোতা অন্যটি শিল্পবোদ্ধা বা শিল্পী সম্প্রদায়। অন্য পক্ষটি আমাদের সমাজে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ যারা প্রকৃতার্থে লেখা ও আঁকা বোঝে না। এটি নির্মম হলেও সত্যি। বৈষম্যমূলক সমাজের বৃহৎ অংশ কেবল শ্রমদাস হিসেবে বাঁচতে বাধ্য হয়। তারা শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা থেকে বঞ্চিত। দর্শক বা পাঠকের যে অংশটি সেটিও খুব বড় অংশ নয়। সৃজনশীলদের চেয়ে কিছুটা বেশি। বর্তমানে এমন বাস্তবতা যে, সৃজনশীলের চেয়ে দর্শক আর পাঠক কমে যাচ্ছে বলে শোনা যায়। যাই হোক এই পাঠক বা দর্শকের মধ্যে রয়েছে নানা স্তর। সামাজিক জীবনে যেহেতু শ্রেণী পেশায় ভিন্নতা আছে তেমনি তার রুচিবোধ ও জীবনাচারেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন শ্রেণী বা পেশার লোক লেখক শিল্পীর কাজকে গ্রহণ করছে, প্রসংশা করছে সেটাও লক্ষ্যনীয়। শ্রেণী বিভাজিত সমাজে সার্বজনীনতা অসম্ভব। তাই কোনো একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের হয়ে পড়া দোষের বলে কিছু নেই বরং এটাই বাস্তবতা। অতএব বিপরীত শ্রেণী পেশার পক্ষ থেকে আসা সমালোচনাকে হজম করার মতো মানসিক ধৈর্য একজন লেখক শিল্পীর থাকতে হবে বৈকি! যারা সমালোচনায় বিভ্রান্ত হন তারা নিজ মত পথ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। বিপাকে পড়াও অস্বাভাবিক নয়।
২
শিল্পের নানা মত পথ বা ইজম আছে। প্রত্যেকটির পেছনে কারণ বা ব্যাখ্যাও আছে। যেমন- কেউ মনে করে শিল্প সমাজের দর্পন। যেমনটি ঘটছে, দেখছে; তারই প্রতিফলন ঘটে শিল্পে। কেউ মনে করে এটা স্রেফ বিনোদন ছাড়া কিছু নয়। কেউ বা একে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে দেখে। মনে করে বর্তমান ও অতীতের সমালোচনামূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি আদর্শিক সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন বপন করাই এর কাজ। কেউ বা একে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখে। কেউ আবার শুধু সৌন্দর্যবোধ বা আঙ্গিকের বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনা হিসেবে দেখে। অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্প কিংবা জীবনের জন্য শিল্প দ্বিবিধ পরিপ্রেক্ষিত থেকে শিল্পবিচারের চেষ্টা মূলত সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্বকে অলঙ্ঘনীয় করে তোলে। শ্রেণী সমন্বয়ের তত্ত্বও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যার অস্তিত্ব আমাদের লোকসংস্কৃতিতে প্রবল। এতসব দেখাদেখির দায়ভার নিয়ে শিল্প রচনা করতে বসা লেখক শিল্পীর জন্য সত্যিই কঠিন এবং দূরহ একটি ব্যাপার। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, তাহলে সমসাময়িক লেখক শিল্পীরা কিভাবে শুরু করবে তাদের সৃজনকর্ম? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাঝেই রয়েছে উদ্ভাবন বা সৃজনশীলতার পথ। লেখক শিল্পীকেই এই উত্তর তৈরি করে নিয়েই শুরু করতে হবে এবং নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। এর মধ্য দিয়েই শিল্পকলা পত্রপল্লবে পল্লবিত হবে, লেখক শিল্পীও হয়ে উঠবে দৃষ্টান্ত।
৩
লেখক শিল্পীর প্রত্যক্ষণ ও প্রকাশের মাঝে অধ্যবসায়ের বিষয় রয়েছে। একটি বিষয়কে নানাদিক থেকে দেখা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাকে আয়ত্ব করতে হয়। গতানুগতিকতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা একজন লেখক শিল্পী ধীরে ধীরে নিজেকে ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি করে নেয়। নিজেকে প্রকাশ করার নিজস্ব ভাষাশৈলী তৈরিতে সক্ষম হয়ে উঠে। তার সৃষ্টিতে শুধু বর্তমান নয় মূর্ত হয়ে ওঠে আগামীর প্রতি পক্ষপাত; যা তার স্বভাবজাত। লেখক শিল্পী এক্ষেত্রে একজন স্বপ্নদ্রষ্টাও বটে। সময় থেকে এগিয়ে থাকা একজন লেখক শিল্পীর চাহিদা ও প্রয়োজনবোধ দর্শক শ্রোতার চাহিদা ও প্রয়োজনবোধের মাঝে ফারাক তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যার দরুণ লেখক শিল্পী সমসাময়িক কালে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হতে পারে। একজন সৃজনশীল লেখক শিল্পী এসবের তোয়াক্কা না করেই শিল্প সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকে। স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। স্বীকৃতির পক্ষে জোরালো দাবীও থাকতে পারে কিন্তু লেখক শিল্পী তা নাও পেতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, স্বীকৃতি বিষয়টির সাথে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শিক অবস্থান জড়িত। লেখক শিল্পী কতটা রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সহমতের পক্ষে ছিলেন তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য। রাষ্ট্রেরও শ্রেণীচরিত্র রয়েছে। তার পছন্দ অপছন্দ রুচিবোধের বিষয়ও রয়েছে। তার সাথে লেখক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি সাংঘর্ষিক হলে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি কি তারা প্রত্যাশা করতে পারে? এক্ষেত্রে লেখক শিল্পীর মনোভাব দ্রোহী হতে বাধ্য।
এ প্রশ্নটি স্বাভাবিক যে তাহলে লেখক শিল্পীরা কি স্বীকৃতি প্রত্যাশা করবেন না? আবার এটিও প্রশ্ন যে, তারা কি স্বীকৃতির জন্যেই শিল্প রচনা করবেন? দুটো প্রশ্নের কোনটি লেখক শিল্পী গ্রহণ করবেন তার উপর তাদের মনোভাব ও অভিব্যক্তি বোঝা দর্শক শ্রোতার পক্ষে সহজ হবে। লেখক শিল্পী নিজেও সমাজের অংশ। তারও শ্রেণী অবস্থান আছে। এ অবস্থান অনুযায়ী তারও মতাদর্শিক অবস্থান বিচার্য। তার শিল্পচর্চা কোন না কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে খুশি করবে। তার গ্রহণযোগ্যতাও তাদের কাছে হওয়া স্বাভাবিক। ভিন্ন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় তার সমালোচনায় মুখর হবে এটাও স্বাভাবিক। তাই স্বীকৃতির প্রসঙ্গটিও সার্বজনীন নয়। কারো কাছে সমালোচিত কারো কাছে বরণীয় হওয়ার এ সত্যটি স্বীকার করে নিয়ে নিজ কাজে ব্যাপৃত হওয়া ছাড়া তাদের গত্যান্তর নেই বললেই চলে।
৪
বিষয় এবং শৈলী দুটোই লেখক শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির অনুসঙ্গ এবং মৌলিক। প্রচলিত শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত সতীর্থ এবং শিল্পবোদ্ধাদের সমালোচনা গতানুগতিক এবং সংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের সমালোচনায় বিচলিত হলে চলবে না। উদ্ভাবন বা সৃষ্টি সবসময় বিপ্লবাত্মক। প্রচলিত রীতি বিধ্বংসী। আবার পাশাপাশি এটিও মনে রাখতে হয় যে নতুনত্ব মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয় বরং অতীত ও বর্তমান অবস্থার গভীর পর্যবেক্ষণ এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার দায়িত্বশীল প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ। যার পেছনে লেখক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা আবশ্যক। প্রশ্ন আসতে পারে যৌক্তিক ব্যাখ্যায় তাহলে শিল্পসৃষ্টির মানদণ্ড কিনা? এ প্রশ্নেও ঐক্যমতে আসা সহজ নয়। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ মানুষকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে অবদমিত করে গতানুগতিক রীতি কিংবা সংস্কার দ্বারা বিষয়কে যাচাই করে তারপর গ্রহণ বা বর্জন করা। তা করতে কেউ ব্যর্থ বা বিরোধ করলে তাকে বর্জন করায় এ সমাজের রীতি। ফলে যুক্তির মাপকাঠিতে সবকিছু বিচার করাই যেন সভ্যতা; নয়তো অসভ্য বা অসামাজিক বলে নিন্দিত হন শিল্পী ও লেখক।
শিল্প কিংবা সৃজনশীল কাজেও যৌক্তিকতার মাপকাঠিতে কতগুলো পূর্ব ধারণা বা প্রকল্প কেন্দ্রিক কাঠামো রয়েছে। এই কাঠামো থেকে সৃষ্টিকে দেখার অভ্যাসে আমরা প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি বলা যায়। অতএব সৃজনশীলতা সবসময় চ্যালেজিং। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি যেখানে পরনির্ভশীল, সেখানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতাকে অস্বীকার করা কঠিনই বৈকি। পুরো কাঠামোটি যেখানে প্রভু রাষ্ট্রগুলোর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত; সেখানে তাকে অস্বীকার বা বিরোধিতার স্থান অপদস্থ কিংবা বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কি! ফলে দেবতার পূজা অর্চনার মাধ্যমে নিজের কিছু অর্জন ও সন্তুষ্টিই পরম পাওয়া। এরকম পরিবেশের ভেতরেই আমরা বেড়ে উঠেছি। দেখছি চারপাশে স্তুতি ও প্রভুদের সংস্কৃতির জয়জয়কার। আমাদের মানস রাজ্যে তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য। ধার করা ইজমের ঠেলায় আমাদের জনসাধারণ রয়েছে যোজন যোজন মাইল দূরে। শিল্প তাদের কাছে অবোধ্য। এটাকেও অনেকে এভাবে জায়েজ করতে শুনি যে, শিল্প সবাই বুঝে না। সবাই বুঝার জন্য লেখক শিল্পীরা লেখালেখি বা আঁকাআঁকি করে না। তাদের ভাষায় শিল্প এমন কিছু যা লেখক শিল্পী এবং সংখ্যালঘু কোন একটি গোষ্ঠী বুঝলেই হল। অর্থাৎ আত্মস্বীকৃত বৈষম্যবাধিতার সর্বোচ্চ নমুনা আর কি!
৫
আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ও শক্তির বিরোধিতা করে জাতীয় রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল চেতনার চর্চা কিংবা আন্দোলন গড়ে না উঠলে সৃজনশীল পাড়ায় নতুনত্ব বা অভিনবত্ব বলে কিছু সৃষ্টি করা সত্যিই কঠিন। আর সেটা না হওয়া অবধি সে লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার মতো মেরুদণ্ড শক্তপোক্ত লেখক শিল্পীদের, ব্যক্তিগত স্কুলিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ছাড়া আপাত কোনো রাস্তা আছে কিনা আমার জানা নেই। এটি আজকের সামাজিক বাস্তবতায় অপ্রত্যাশিত বলা যায়। আমরা ষাট-সত্তর দশকে যে রেডিক্যাল মধ্যবিত্ত পাই তা এখন নেই বললেই চলে। এখনকার মধ্যবিত্তরা করপোরেটের চাকর হওয়া কিংবা বিদেশে দাস্যবৃত্তি করতে উৎসাহী বেশি। ধন উপার্জন এখনকার মুখ্য নীতি এবং মধ্যবিত্তের ধ্যান-জ্ঞান ও তপস্যা।
প্রচলিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হয়ে উঠেছে মানুষের অভীষ্ট। শিল্পস্রষ্টারা টাকা উপার্জন করতে পারে না বলে তাদের দুচোখে দেখতে পারে না এখনকার পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র। মাস্তানী করে সম্পদ অর্জন করা একজন নিরক্ষর বর্বর খুনী মানুষও সৃজনশীলদের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও মান্য এই সমাজে। রাজনীতি তাকে রাজনীতিতে টানে। রাষ্ট্র তাকে রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে মানে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকে। তার সমস্ত পাপ মাপ হয়ে যায় এ ব্যবস্থায় টাকার কল্যাণে। এ অবস্থায় যে আধিপত্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ফল তা বুঝে কয়জন? নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েতের পতন প্রগতিশীল রাজনৈতিক চর্চায় ব্যাপক পতন ঘটিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাই রাজনীতি বিমুখ প্রজন্ম তৈরি হয়েছে ব্যাপকমাত্রায়। রাজনীতিই যে সমাজের ইঞ্জিন এটা না বুঝে যতই সৃষ্টিশীল চর্চা হোক না তা কোনো ফল বয়ে আনবে না। না ব্যক্তির জন্য, না সমাজের জন্য। ঔপনিবেশিক বাস্তবতার চরমতাকে অস্বীকার করে নতুন ভাবনা ও শৈলীর সৃষ্টি করা সত্যিই কঠিন বটে।
৬
তারপরও যারা লিখছেন আঁকছেন তারা স্বীকৃতি চান সমাজ ও রাষ্ট্রের। কারণ বলি আর নাই বলি স্বীকৃতি ছাড়া কীর্তির কি মহিমা থাকে? তাই স্বীকৃতি প্রত্যাশাও অমূলক বলি কি করে? স্বীকৃতির চেষ্টা তাই সৃজনশীলদের থাকতে হয়। নিজের সৃষ্টিকে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তাকে অন্যের কাছে গ্রহণীয় করে তোলাও তাই সৃষ্টির দ্বিতীয় কাজ বলা চলে। কে কিভাবে সেটা করবে তার নির্দিষ্ট কোন অবয়ব নেই, এটি ব্যক্তি লেখক বা শিল্পীর নিজস্বতার বিষয়। যদিও আমরা এ বিষয়েও গুঞ্জন শুনি যে, অমুক তেলবাজি করছে নিজের ব্যাপারে। ঢাকঢোল পিঠিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করে ফেলবে যেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সমালোচনা এক্ষেত্রেও সৃজনশীলদের ছাড়ে না আর কি! তারপরও প্রচারের ধরণটি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়িই হবে সেটাই স্বাভাবিক। কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে তিনি শিল্পচর্চা করছেন তা তার প্রপাগান্ডার ধরণ থেকে বুঝা সম্ভব।
৭
আরো একটি বিষয় উপেক্ষা করা চলে না, সেটা হল নিজ সতীর্থ বা একই প্লাটফর্মের লোকজন দ্বারা সমালোচিত বা উপেক্ষিত হওয়া। আমরা প্রায় দেখি, বা বলা চলে এটা একেবারে নির্ধারিত যে, আপনার সবচেয়ে কাছের সতীর্থও আপনার কাজকে সমর্থন করে না। অনেকক্ষেত্রে পিছনে বাজে কথা বলতেও আমরা দেখি। এসবকে ব্যক্তিগত জেলাস বা ইর্ষাপরায়নতা বলা চলে। যদি বিরোধিতা বা সমালোচনাটি গঠনমূলক হয় তাতে সতীর্থকে এগিয়ে যেতে সহায়তায় করা হয়; নয়তো বিরোধিতা কেবল হীনমন্যতার পরিচয় ছাড়া আর কি! সমাজে যেহেতু আত্মপ্রতিষ্ঠার অসুস্থ প্রতিযোগিতা রয়েছে সেখানে অন্যকে ডিঙ্গিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করাটা স্বাভাবিক। ফলে কেউ অন্যকে ভালো বা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে চাই না। বরং কেউ সত্যিকার ভালো বা শ্রেষ্ঠ হলে সবাই মিলে তাকে ডুবিয়ে দিতে পারলে বাঁচে আর কি!
এরকম আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বাস্তবতায় চাটুকার বা স্তুতিকাররা বাদে স্বকীয় ব্যক্তিত্বশীলরা অবহেলিত কিংবা নিন্দাবাদ বা অবজ্ঞার স্বীকার হবেন না; তা অপ্রত্যাশিত। তাই সমালোচনা বা সমালোচকের দৃষ্টিকোনটি কি? লেখক-শিল্পীদের বুঝে নিতে হয় সর্বাগ্রে।